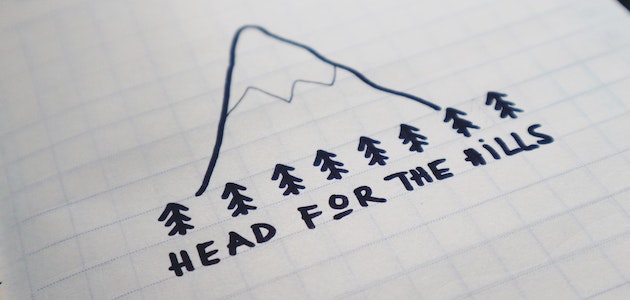‘রামায়ণ’-এর রামগাথার পরিবর্তন; আদি
কবির রচনা থেকে পরবর্তী কবিদের ‘রামচর্চা’র ইতিকথা
‘শ্রীরাম চন্দ্র কৃপালু ভজমন।
হরণ ভব ভয় দারুণম্।।’১
ষোড়শ শতাব্দীর খ্যাতনামা ব্যক্তি তুলসীদাস রচিত
‘রামস্তুতি’র বাংলা তর্জমা করলে দেখা যায়, দশরথাত্মজ রাম জন্ম-মৃত্যুর ভীষণ ভয়কে
হরণ করেন, অতত্রব তিনি মনকে সততভাবে রামবন্দনায় নিয়োজিত হতে বলেছেন।এহেন
ত্রিতাপহরণকারীর বর্ণনা প্রথম পাওয়া যায় সংস্কৃত ভাষায় রচিত বাল্মিকীর ‘রামায়ণ’-এ।
ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্তরাগে প্রজ্জ্বলিত রয়েছে ‘রামায়ণ’ তথা ‘রাম’-এর কৃতিত্ব,
তার ন্যায়পরায়ণতা সহ বিক্রমের কাহিনি। তবে ‘রামায়ণ’-এর আদি কবি রূপে বিশ্বসাহিত্যে
বরেণ্য হয়েছেন কবি বাল্মীকি। তাঁর
প্রায় সহস্রাধিক বছর পরে রচিত হয় রাজকবি কম্বন প্রণীত ‘রামাভতারম্’। যা আবার
‘কম্ব-রামায়ণ’ নামেও পরিচিত সাহিত্যের দরবারে। ভিন্ন সময়ে দুটি সাহিত্যিক নিদর্শন
রচিত হওয়ায় যুগগত প্রভেদের পাশাপাশি বিষয়বৈচিত্র্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়।
বাল্মীকি তাঁর কাব্যটিকে কাহিনিগত বিভাজন অনুসারে সাতটি পৃথক ভাগে বিভাজিত
করেছেন, যথা; বাল কাণ্ড, অযোধ্যা কাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, সুন্দর
কাণ্ড, যুদ্ধ কাণ্ড এবং উত্তর কাণ্ড। অন্যদিকে কম্বনের ‘রামায়ণ’ বাল কাণ্ড,
অযোধ্যা কাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, সুন্দর কাণ্ড ইত্যাদি ৬টি বিভাগে
বিভক্ত। আদি কবির রচনা অনুসারে অযোধ্যারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামের সঙ্গে
মিথিলাপতি জনকের কন্যা সীতার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ‘হরধনু ভঙ্গ’-এর মাধ্যমে। বিবাহের
পূর্বে উভয়ের সাক্ষাতের পরিচয় উল্লেখিত হয়নি কবির বর্ণনায়। অথচ ‘কম্ব রামায়ণ’-এ
কবি রাম-সীতার এই বিবাহটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রণয়ের জয়গাঁথা হিসাবে উপনীত করেছেন।
‘উজ্জ্বলনীলমণি’তেবর্ণিত ‘পূর্বরাগ’-এর উল্লেখ স্বরূপ
পাত্র-পাত্রীদ্বয়ের প্রাক্-বিবাহ জনিত সাক্ষাতের কথা বলা হয়েছে।বিশ্বামিত্র মুনির
অনুরোধে রাম যখন মিথিলায় যান সেই সময় সীতার সঙ্গে তাঁর সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ ঘটে। যা
কম্ব-রামায়ণে নতুন উপকাহিনির সঞ্চার করে। অবশ্য বাল্মিকীর সঙ্গে কম্বনের সময়গত
প্রভেদটিও এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। ‘রামাভতারম্’ রচনাকালে ‘রাম’ চরিত্রটি মহাকাব্যের
গণ্ডি পেরিয়ে জনমানসে দেবতার ‘অবতার’ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। নারায়ণের অবতাররূপী
অযোধ্যার শাসক সেই সময় মানুষের আরাধ্যে রূপান্তরিত হয়। সম্ভবত সেই কারণেই এহেন
কাহিনিগত রূপান্তর দেখা যায়। যার ফলে ‘সীতাহরণ’ এর ক্ষেত্রে ঘটনাক্রমের পরিবর্তন দেখা যায়। কবির
সমসাময়িক কালে যেহেতু রাম নারায়ণ রূপে মানুষের কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে
ফলে তার স্ত্রী
সীতাও, লক্ষ্মী দেবীর অবতার রূপে আরাধ্য হয়ে ওঠে।
তাই রাক্ষস কর্তৃক দেবী
সীতার অপহরণ
অথবা তার অঙ্গস্পর্শ সম্ভব নয়; ফলত ‘কম্ব-রামায়ণে’ রাবণ কর্তৃক পর্ণশালা সহ সীতাহরণের
বিবরণ পাওয়া যায়। আবার আদি
কবি ‘জটায়ু’কে রামের অনুগত হিসেবে চিত্রিত করলেও কম্বন রামানুজরূপে
‘জটায়ু’কে দেখিয়েছেন। এছাড়া অশোক বনে বন্দীনী সীতার মন-পরিবর্তনের জন্য রাক্ষসরাজ
‘মায়া-জনক’ও নির্মাণ করেন।। আদি কবির বর্ণনায় এই হেন কোনো
ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়
না। বাল্মীকবির
কলমে দশরথ পুত্র রাম পুরুষোত্তম
হিসেবে চিত্রিত হলেও
তামিল ভাষায় রচিত ‘কম্ব রামায়ণে’ দেবতা রূপে প্রতিবিম্বিত হয়েছে রাম।
প্রাগানুধিকযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একটি জনপ্রিয়তম
শাখা অনুবাদ সাহিত্য।
যার সূত্রে রচিত
হয় বাংলা রামায়ণ তথা কবি
কৃত্তিবাস বিরচিত 'শ্রীরাম পাঁচালী'।
তুর্কি-বিজয় পরবর্তী সময়কালে অনুবাদ সাহিত্যের জন্ম হয়।
নানান সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য অনূদিত হয় রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত
সহ নানাম পৌরাণিক রচনা।
বাল্মীকি রামায়ণ রচিত
হয়েছিল সমগ্র ভারতবাসীর জন্য তবে কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচিত হয়েছিল বাঙালির জন্য। ফলত কাহিনি ক্রমের পাশাপাশি রাম চরিত্রের পরিবর্তনও
দেখাযায়।পূর্বে
সংস্কৃত সাহিত্য বা রামায়ণ মহাভারত পাঠ করার জন্য কথকঠাকুরের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু
সর্বসাধারণের জন্য রচিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবি লোক-শিক্ষার্থে কাব্য রচনা প্রসঙ্গে
মন্তব্য করেছেন,
“মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পন্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী।।
বাপ মায়ের আশীর্বাদ গুরুর কল্যাণ।
বাল্মিকী প্রসাদে রচে রামায়ণ গান।।
সাত কান্ডের কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে হইল কৃত্তিবাস
পণ্ডিত।।'২
অর্থাৎ
সাধারণ জনমানসে রামকথা
প্রচারিত করার জন্য তিনি গ্রন্থটি রচনায় অগ্রসর হয়েছেন বলে
সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন।
এছাড়া সমকালীন পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে মানুষের পরিত্রাণের একটি পথও নির্দেশ করতে
চেয়েছিলেন কৃত্তিবাস;
“মরা
মরা বলিতে আইলো রাম নাম।
পাইলে সকল
পাপে দস্যু পরিত্রাণ।।
তুলা রাশি
কেমন অগ্নি ভস্ম হয়।
একবার রাম
নামে সর্ব পাপ ক্ষয়।।”৩
কম্বনের রামায়ণের ন্যায় কৃত্তিবাসী রামায়ণেও বিষ্ণুর অবতার
হিসেবে রাম চিত্রিত হয়েছে। যদিও অনুবাদের পরিবর্তে কবির স্বকীয় ভাবনার প্রগাঢ়তা সমগ্র কাব্য জুড়ে লক্ষ্য করা যায়। মূল
রামায়ণ থেকে কাহিনি গ্রহণ করলেও বাঙালি জাতির ভাবনাকে মর্যাদা দান করতেই
কৃত্তিবাস বাংলা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রতিবিম্বিত করেন রাম চরিত্রের মাধ্যমে।
তাই সংস্কৃতের
‘পুরুষোত্তম’
রাম বাঙালির কাছে ‘দেবতা’ রামে পরিণত হয়। আদি কবির রামায়ণে
দেখা যায় রচয়িতা সমস্ত
ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর কাব্য রচনা করেছেন। অথচ কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসারে রাম জন্মের ষাট হাজার
বছর আগেই বাল্মিকী রামায়ণ রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়,
“রাম
জন্ম পূর্বে ষাটি সহস্র বৎসর।
অনাগত পুরাণ
ছিল মুনিবর।।”৪
তাছাড়া বাংলার রামায়ণে বাংলার লোকসাহিত্যের নিজস্ব ছন্দ স্বরূপ
পাঁচালীর প্রয়োগ দেখা যায়। আসলে কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভক্তিরস এবং
হাস্যরসের মেলবন্ধন ঘটেছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভক্তি রসের প্রাবল্য দেখা যায়
শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে। বঙ্গবাসী যেন রাম ও কৃষ্ণের নানান পৌরাণিক কাহিনির মাধুর্যে মোহিত হয়ে কালযাপন করত। পরে রাজা গণেশ এবং তাঁর পুত্রের
শাসনকালে বিজাতীয় শাসকের আগ্রাসন এবং ধর্মান্তরিতকরণের বিষয়টিও লক্ষ্যণীয়। তাই সকল
হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষকে একত্রিত করার একটি প্রয়াসও দেখা যায়। যার ফলে দেশীয় পাঁচালী ছন্দে রামকথা জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাঙালির নীতিকথা ও ধর্মীয়
মূল্যবোধের পরিচয়
স্বরূপ ‘অহল্যার
শাপমুক্তি’
কিংবা ‘লক্ষণের গণ্ডিদান’ প্রসঙ্গের কথা বলাই যায়। সংস্কৃত
রামায়ণে অলংকার এবং উপমার গাম্ভীর্য দেখা যায়। তবে কৃত্তিবাসী রচনায় বাংলার চিরায়ত
ঘরানার পরিচয় মেলে; ‘কলার বাগুড়ি’ এবং ‘কুমোরের চাক’ ইত্যাদি প্রসঙ্গের সংযোজন তার
স্বপক্ষেই যুক্তি দেয়। বাংলা ছন্দ রীতির বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে যখন কবি রামের
পদাপর্ণের কথা বলেন-
‘শ্রীরাম আইল দেশে পড়ে গেল সাড়া।
ঝা গুড়গুড় বাদ্য বাজে নাচে চণ্ডাল পাড়া।।”৫
অথবা,
‘ডাল ভাঙ্গে হনুমান শব্দ মড়মড়ি।
আতঙ্কে রাক্ষস সব উঠে দড়বড়ি।।”৬
এক্ষেত্রে
উভয় পঙ্ক্তিতে অনুপ্রাস এবং ধন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কাহিনি
বর্ণনা প্রসঙ্গেও কবির স্বকীয় ভঙ্গিমা প্রকাশিত হয়েছে। গ্রিক তাত্ত্বিক
অ্যারিস্টটল গুরু প্লেটোর বিরোধিতা করে সাহিত্য বা কাব্যকে অনুকরণের পরিবর্তে
‘পূরণকারক সত্য’ রূপে নির্দেশিত করেছিলেন। তাঁর মতানুসারে মানব জীবনে যে কোনো
বিষয়ে আয়ত্ত করার প্রথম এবং প্রধান মাধ্যম হল অনুকরণ, যা তাঁর মতানুসারে
‘মাইমেসিস’ নামে অভিহিত। ফলত কবি বা সাহিত্যিক বাস্তবিক জীবনে ঘটে যাওয়া কিংবা
অতীতে ঘটে কোনো ঘটনার থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হন। এক্ষেত্রে
ঘটনাবলীর মধ্যে থাকা ঈষৎ ফাঁক-ফোঁকর অথবা তথ্যের পরিপূরণ করেন কবিরা তাঁদের
অর্ন্তদৃষ্টির মাধ্যমে। ফলত ইতিহাসের তথ্যের পরিবর্তের কাব্যের সত্য ‘পরিপূরক’
রূপে প্রতিভাত হয়। তাই হয়তো কৃত্তিবাসী রামকথা অনূদিত গ্রন্থের পরিবর্তে স্বতন্ত্র
কাব্য হিসাবেই সমাদৃত হয়েছে। কবি-প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর মতে, “বলা বাহুল্য,
কৃত্তিবাস বাল্মীকির বাংলা অনুবাদক শুধু নন, দেব দানব রাক্ষসেরা শুদ্ধু মধ্যযুগীয়
গৃহস্থ বাঙালি চরিত্রে পরিণত হয়েছেন, গ্রন্থটির প্রাকৃতিক এবং মানসিক আবহওয়া
একান্তই বাংলার। এ-কাব্যে বাঙালির মনের মতো হতেও পারে, এমনকি বাংলা সাহিত্যে
পুরাণের পুনর্জন্মের প্রথম উদাহরণ বলেও গণ্য হতে পারে, কিন্তু এর আত্মার সঙ্গে
বাল্মীকির আত্মার প্রভেদ রবীন্দ্রনাথের ‘কচ ও দেবযানী’র সঙ্গে মহাভারতের
দেবযানী-উপাখ্যানের প্রভেদের মতোই, মাপে ঠিক ততটা না-হলে জাতে তা-ই।’’৭
সংযোজনের
পাশাপাশি বেশ কিছু বিয়োজনও লক্ষ করা যায়। আদিকবি কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে বর্ষা এবং শরৎ ঋতুর প্রসঙ্গ বিবৃত করেছেন। আসলে
সীতাহরণ, বালিবধ এবং ভাবী যুদ্ধের বার্তাবাহী ক্রমালাপের মধ্যে একটু দিক
পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ছিল; ‘বনবাসের দুঃখ, সীতা-হারানোর দুঃখ, বালীবধের উত্তেজনা
ও অবসাদ—সমস্ত শেষ হয়েছে, সামনে পড়ে আছে মহাযুদ্ধের বীভৎসতা; দুই ব্যস্ততার
মাঝখানে একটু শান্তি, সৌন্দর্য-সম্ভোগের বিশুদ্ধ একটু আনন্দ। এই বিরতির প্রয়োজন
ছিল সকলেরই—কাব্যের, কবির এবং পাঠকের, আর সবচেয়ে বেশি রামের।’’৮
সেক্ষেত্রে ‘নরোত্তম রাম’-এর বিষয়টিও স্মরণযোগ্য। কৃত্তিবাসের বর্ণনায় রামের মধ্যে
দৈবিক সত্তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাই এহেন বিরতিজনিত বিষয়টিকে বিধৃত করার
পরিবর্তে বিয়োজনকেই নির্বাচন করেছেন কবি।
তারপর
‘ময়মনসিংহ গীতিকা’-র কবি রূপে দ্বিজ বংশীদাস সুতা চন্দ্রাবতীর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাগাধুনিকালে তাঁর কলমেই
‘রামায়ণ’-এর নতুন বিবরণ পাওয়া যায়। বস্তুত রামায়ণের মূল কাহিনির পাশাপাশি নারীর দৃষ্টিতে
‘সীতায়ন’-এর পরিচিতি মেলে। যদিও অসম্পূর্ণভাবে গ্রন্থটি পাওয়া যায়। সেখানে সীতার
জন্ম, রামের জন্ম এবং সীতার বনবাসের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়।
ভূমিজা সীতার জন্মবৃত্তান্তটিও অভিনব ভঙ্গিমায় তুলে
ধরেছেন চন্দ্রাবতী। স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে কবি জানান সতা নামক এক ধীবর রমণী কৌটের
মধ্যে রাখা ডিম্বটি ভেদ করে এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যার জন্ম হয়। ধীবর বধূর
নামানুসারে সেই কন্যা সীতা নামে পরিচিত হয়।মঙ্গলকাব্য ধারা অন্যতম উল্লেখযোগ্য
বৈশিষ্ট্য রূপে সমাদৃত বারামাস্যারও পরিচয় মেলে এক্ষেত্রে। বনবাসে থাকাকালীন নানা
সময়ের সাপেক্ষে বয়ে চলা নানান সুখদুঃখের ইতিকথা সীতার জবানীতে উল্লেখিত হয়েছে।
মূলত স্বপ্ন-দর্শনের মাধ্যমেই ঘটনাপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়েছে;
“মাঘ মাসেতে আমি গো দেখিনু স্বপন।
রণে মরে ইন্দ্রজিত গো রাবণ নন্দন।।
স্বপন সফল হইল গো লঙ্কা ছারকার।
সাগরের কূলে শুনি গো রাক্ষসের হাহাকার।
ফাল্গুন মাসেতে আমি গো দেখিনু স্বপনে।
সবংশে মরিল রাবণ গো শ্রীরামের বাণে।
স্বপন সফল হইল গো দুঃখের দিন যায়।
বানর কটক শুনি গো রামগুণ গায়।।
চৈত্র মাসেতে সীতার গো দুঃখ হইল দূর।
পোহাইল দুঃখের নিশি গো আইল সুখ ভোর।।
অন্ধেতে পাইল যেমন গো নয়নের মণি।
তেমতি দুঃখিনী সীতা গো পাইল রঘুমণি।।
সীতার বারোমাসী কথা গো দুঃখের ভারতী।
বারোমাসের দুঃখের কথা গো ভনে চন্দ্রাবতী।।’’৯
এছাড়াও
‘কুকুয়া’ নামক কৈকেয়ী কন্যার সংযোজনও লক্ষ করা যায় চন্দ্রাবতীর লেখনীতে। একজন
নারীর দুঃখ-যাতনা জনিত দুর্বিপাকের ক্ষেত্রে যে অন্য নারীর ভূমিকা অগ্রগণ্য সেটি
এক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। কুকুয়ার অনুরোধে সীতা তালপাতায় মন্দোদরীপতি রাবণের
চিত্রাঙ্কন করেন। অসাবধানবত সেটি নিজের কাছে রেখে নিদ্রাগত হন সীতা। সেই সুযোগে
কুকুয়া রামের কাছে ভাতৃবধূর চরিত্রগত স্খালন তুলে ধরেন। ফলশ্রুতিতে গভীর বনে
নির্বাসিত হন জানকী। কবির ব্যক্তি-জীবনের ছায়ায় প্রতিফলিত হয়েছে এক্ষেত্রে।
রামায়ণের রাম ও সীতার প্রণয়ের অপূর্ণতা যেন চন্দ্রাবতী ও জয়ানন্দের প্রণয়ের
অসম্পূর্ণতাকেই নির্দেশ করে। পরমারাধ্য রামের দৈবি প্রভাব যেন এক্ষেত্রে খণ্ডিত
হয়েছে। চিরায়ত পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে এক নারীর কথালাপ বিধৃত হয়েছে কাব্য
সমগ্রে। কবি নবনীতা দেবসেন এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন; ‘বিবৃতিকার রূপে সীতা এবং
চন্দ্রাবতীর প্রভেদ এই যে, কাহিনির চরিত্র, অপরজন বহিরাগত। দুটি স্বতন্ত্র ভূমিকা
ও দৃষ্টিকোণ ছাড়াও, তাঁদের জগত-সম্পর্কিত নীতিও পৃথক। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মূল
আদর্শের যোগ্য প্রতিনিধি সীতা, কিন্তু চন্দ্রাবতী একজন বিদ্রোহী নারী।”১০
ফলত নারায়ণরূপীর রামের শৌর্য-বীর্যের ক্ষীণ প্রভাব ‘চন্দ্রাবতী রামায়ণে’র অন্যতম
উল্লেখযোগ্য দিক।
এছাড়াও
ষোড়শ শতকে রচিত অদ্ভুত আচার্যের ‘রামায়ণে’ বাল্মিকীকে ভগবান বিষ্ণুর রাম রূপ
প্রদর্শনের কথাও পাওয়া যায়। আবার রামানন্দ ঘোষের ‘নূতন রামায়ণ’ গ্রন্থে বুদ্ধরূপে
প্রদর্শিত হয়েছে ‘রাম’ চরিত্রটি। আবার রঘুনন্দন বিরোচিত ‘রাম রসায়ন’ গ্রন্থে
পরাক্রমী রামের পরিবর্তে প্রেমিক রামের পরিচয় পাওয়া যায়। সীতার বিরহ অংশে বৈষ্ণবীয়
বিরহজাত ঘটনার পরিচয় মেলে। তবে বাংলা তথা বাঙালির রাম-ভাবনায়
‘নীলাম্বুজশ্যামকোমলাঙ্গ’ রাম পরিণত হয়েছে ‘নবদূর্বাদল শ্যামের’ গাত্রবর্ণে। এছাড়া
বাঙালি জাতিগত দৈহিক লক্ষণও প্রত্যক্ষ করা যায় এক্ষেত্রে।

পরবর্তী সময়ে উত্তর এবং উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন ভাষা, যেমন- অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দি
ইত্যাদির পূর্বে দক্ষিণ ভারতের
তিনটি প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণ রচিত হয়। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে প্রথম প্রাদেশিক ভাষার রামকথা কর্ণাটক ভাষায়
‘পম্পা
রামায়ণ’ হিসাবে রচিত হয়। তেলেগু ভাষার রাম কথার প্রকাশ লক্ষ্য
করা যায় তিক্কনের
‘নির্বাচনত্তোর রামায়ণ’ গ্রন্থে। অসমীয়া
ভাষায় মাধব কন্দলি এবং শংকরদেবের রামায়ণের
কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। আবার
ওড়িয়া ভাষায় রামকথা পুরাণ এবং কাব্য দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে রচিত হয়।
সংস্কৃত রামায়ণ অবলম্বনে
মহাকবি সারলা দাস, বলরাম দাস, কৃপাসিন্ধু দাস প্রমুখ রামায়ণ রচনায় অগ্রসর
হন। পরবর্তীতে কৃষ্ণচন্দ্র রাজেন্দ্র কৃষ্ণচরণ পট্টনায়ক
প্রমূখ কবি সাহিত্যিকদের কলমে রামায়ণের অমর কাহিনি।
ভারতীয় আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট সহ জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য
অঙ্গস্বরূপ রামায়ণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অবশ্যই প্রসঙ্গে বাল্মিকী রামায়ণের
ব্রহ্মা কর্তৃক বাল্মীকির আশীর্বাদ দানের প্রসঙ্গটিও উল্লেখযোগ্য
“যাবত
স্থস্যান্তি গিরয়ঃ
সরিতঃচ মহীতলে।
তাবৎ
রামায়ণ কথা লোকেষু প্রাচরিষ্যতি।।”১১
অর্থাৎ পৃথিবীতে
পাহাড়-পর্বত সহ নদ-নদী যতদিন থাকবে ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে রামায়ণের কাহিনি, লোকমুখে প্রচারিত অপসারিত হবে।
হরপ্রসাদ
শাস্ত্রী রামায়ণকে ভারতীয় যুব সমাজের চরিত্র গঠনের অন্যতম সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত
করেছিলেন। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় স্বতন্ত্রভাবে রচিত রাম গাথা
তার স্বপক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। রামায়ণের এহেন বিশেষত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুর অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, 'রামায়ণের
প্রথম বিশেষত্লেছেন্ তা ঘরের কথা কে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখায়ইছে। পিতা-পুত্র-ভ্রাতায়-ভ্রাতায়-স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতির সম্বন্ধ,
রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে তা অতি সহজে মহাকাব্যের
উপযুক্ত হইয়াছে। দেশ-জয়, শত্রুবিনাশ, দুই প্রবল বিরোধী পক্ষের প্রচন্ড আঘাত-সংঘাত এই সমস্ত ব্যাপারে সাধারণত মহাকাব্যের মধ্যে
আন্দোলন ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করে নাই, সে যুদ্ধ ঘটনা রামসীতার দাম্পত্য-প্রীতকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ্যমাত্র; পিতার প্রতি
পুত্রের বশ্যত, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতি-পত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও রাজার প্রতি রাজার
কর্তব্য কত দূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইতেছে। এইরূপ ব্যক্তি-বিশেষের প্রধানত ঘরে সম্পর্ক গুলি কোন
দেশের মহাকাব্যে এমন ভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলে গণ্য হয়
নাই।”১২
ফলত ‘নরোচন্দ্র’রাম পুরুষোত্তম রাম চরিত্রটি যুগে
যুগে সময়ের কালপ্রভা অনুসারে বিষ্ণু অবতার বা দৈবি-শক্তির আধারে পরিণত হয়েছে। সেই সূত্রেই সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে বিধৃত হয়েছে রাম বৃত্তান্ত। যার মাধ্যমে আদি কবির রচনা থেকে উত্তর কালের কবিদের রচনায় রাম
চর্চার এক প্রবাহমান ধারার পরিচয় পাওয়া মেলে।
তথ্যসূত্র;
1. https://hindi.webdunia.com/ram-navmi-special/ram-stuti-117040100037_1.html
2. বেণীমাধব
শীল(সম্পা), ‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ’, কলকাতা, অক্ষয় লাইব্রেরি, পৃ ২৯
3. তদেব,
পৃ ৩৫
4. তদেব,
পৃ ৩৮
5. তদেব,
পৃ ৬৭
6. তদেব,
৩৩৮
7. বুদ্ধদেব
বসু, ‘শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ সঙ্কলন’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃ ১০
8. তদেব,
পৃ ১২
9. হিমেল
বরকত(সম্পা), ‘চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ও প্রাসঙ্গিক পাঠ’, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ
৩৮
10. হিমেল
বরকত(সম্পা), ‘চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ও প্রাসঙ্গিক পাঠ’, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ
১২২
11. ড.
প্রদ্যোত বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস’, কলকাতা, নিউ আদ্যাশক্তি
প্রিণ্টার্স, পৃ ৩৬
12. রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুর, ‘প্রাচীন সাহিত্য’, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃ ৯