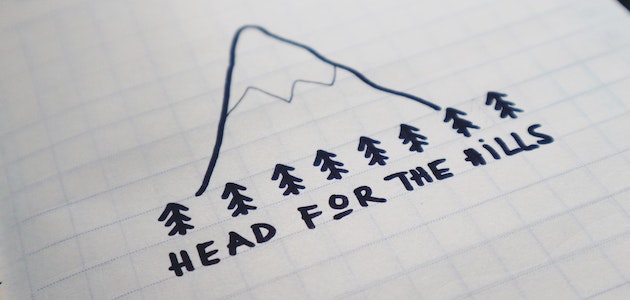সূত্র হনুমান

(নামকরণ যা ইঙ্গিত দিচ্ছে তাই, হ্যাঁ পাঠক এখানে
আমি হনুমান চরিত্রকে সবিস্তারে বিশ্লেষণ করতে নয়, যত রকম সূত্র যত রকম রেফারেন্স সারাজীবনের
পাঠে হনুমান বিষয়ে পেয়েছি, তার ইশারাগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে চাই। স্বল্পপরিসরের মধ্যে
সে সব তত্ত্ব ও তথ্য একত্রে সন্নিবেশিত করে তুলে ধরতে এখনও পর্যন্ত স্বীয় অল্পপাঠে
কোন বই বা প্রবন্ধে দেখিনি। এবং তাই এই লেখায় এক এক জায়গায় হনুমানের এক এক রকম ইন্টারপ্রিটেশন
আসবে। পাঠক বিভ্রান্ত হবেন না। হনুমান আধ্যাত্মিক পীঠস্থান ভারত জাতির শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মচর্য
ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা। তাঁর মাহাত্ম্য ইনফিনিট - তাই তাকে বিশ্লেষণ করতে বসলে অসংখ্য অ্যাঙ্গেল তো আসবেই। সেভাবে হনুমান কখনো
হবেন sun god, কখনো হবেন cloud, কখনো হবেন monsoon wind, কখনো post-conscious, কখনো
ইতিহাস, কখনো ধর্ম কখনো চালু অর্থে এক experienced কাউন্সিলার - কখনো child-hero। শুধু একটা aspect নিয়েই
(ধরা যাক দূত ও সীতার counsellor হিসাবে হনুমান) এক একটা ১০ পাতার প্রবন্ধ হয়ে যেতে
পারে। সেই সব ইঙ্গিতগুলো জড়ো করে আরো সবিস্তার বিশ্লেষণ করে পূর্ণাঙ্গ হনুমান চরিত
মানস হয়তো আরো স্থিতিশীল কেউ লিখবেন। আসলে হনুমানের মহিমার কোন তল পাওয়া আমার পক্ষে
সম্ভব নয়।)
হনুমান
অঞ্জনার গর্ভজাত পবনের সন্তান - সুমেরু পর্বতের রাজা কেশরীর ক্ষেত্রজ পুত্র। একদা অঞ্জনা
পর্বতে বেড়াচ্ছিলেন - তখন বায়ু তাকে দেখেন ও বায়ুবেগে অঞ্জনার বস্ত্র মোচন করে অঞ্জনার
সঙ্গে মিলিত হন। তাদের পুত্র হনুমান। এ অবধি ঠিক আছে। কিন্তু এমন ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের
উদাহরণ রামায়ণ মহাকাব্যে আর নেই। হ্যাঁ, পঞ্চপাণ্ডব মহাভারতে দেবতার ঔরসে জন্মেছেন।
আরো অনেকেই মহাভারতে দেবতার ঔরসে মানবীর গর্ভে জন্মলাভ করেছেন। কিন্তু রামায়ণে দেবতার
ঔরসে মানবীর গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্রের উদাহরণ একমাত্র হনুমান! তবে বালী সুগ্রীবের পিতা
ঋক্ষরজার বাল(চুল)ও গ্রীবায় ইন্দ্র ও সূর্যের বীর্য পড়ে জন্মেছিলেন বালী ও সুগ্রীব।
আবার অক্ষম দশরথ পুত্রার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়েছিলেন তেজস্বী ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গকে
দিয়ে। এগুলি সামান্য ইঙ্গিত দেয় ক্ষেত্রজ জন্মের বিষয়ে। কিন্তু মহাভারতে ব্যাস যেভাবে
কুরু রাজবধুদের সঙ্গে সঙ্গম করেছেন... সেখানে, গোটা মহাভারত জুড়ে এ ব্যবস্থা যতটা খোলামেলা-তার
তুলনায় রামায়ণে এত রাখঢাক দেখে বোঝা যায় যে আসলে মহাভারতের সমাজ অনেক প্রাচীন, অনেক
আনঅ্যাডালটারেটেড ও তার আদিম মাতৃতান্ত্রিক সত্ত্বা নিয়ে বিরাজমান। এ প্রসঙ্গ এখন সুবিদিত।
তবে বলার বিষয় এই যে স্পষ্ট করে, কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় না করে রামায়ণে দেবতার ঔরসে ক্ষেত্রজ
পুত্রের একমাত্র উদাহরণ হনুমান।
হনুমানের
প্রসবের পরে অঞ্জনা ফল আহরণের জন্য গভীর বনে প্রবেশ করেন। তখন বালক মাতৃবিরহে ক্ষুধায়
কাতর হয়ে রোদন করতে লাগল। তখন সূর্যোদয় কাল। জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ সুর্যকে দেখে
বালক ফলভ্রমে তাকে গ্রহণ করার জন্য এক লম্ফ দিল। এই তরুণ বীর দ্বিতীয় তরুণ সুর্যের
ন্যায় অন্তরীক্ষে যেতে লাগলেন। নভোমণ্ডলের মধ্যপথ দিয়ে গরুড় ও মনেরও অপেক্ষা বেশি বেগে
বাধিত হতে লাগলো হনুমান! তুষারশীতল বায়ু তাকে সূর্যের দহনশীল উত্তাপ হতে রক্ষা করতে
করতে তার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, সুর্যদেব তাকে অজ্ঞান শিশু বোধ করে দগ্ধ করলেন না। এদিকে
যেদিন বালক সূর্য ধরবার জন্য ধাবিত হয়, সেদিন সূর্যগ্রহণের দিন। রাহু সূর্যগ্রহণের
উপক্রম করছেন। এই বালক সূর্যের রথোপরি রাহুকেই আক্রমণ করে বসলে রাহু সভয়ে সরে পড়লো।
পরে ইন্দ্রালয়ে গিয়ে সরোষে ইন্দ্রকে বললো- তুমি আমার ক্ষুধাশান্তির জন্য চন্দ্রসুর্যকে
দিয়ে আবার তা অন্যকে দান করেছ কেন?
রাহুর
কথা শুনে ইন্দ্র ঐরাবতে আরোহণ করে রাহুকে সঙ্গে নিয়ে যেখানে সূর্য হনুমানের সঙ্গে অবস্থিত
সেখানে গেলেন। তাদের দেখে বালক নতুন ফললাভের
আশায় লাফ দিলে রাহু পালাল। বালক ভীষণ মূর্তি ধরে ঐরাবতকে গ্রহণ করতে ধাবিত হলো।
তখন
ইন্দ্র নিতান্ত ক্রুদ্ধ না হয়ে তার উপর বজ্রপ্রহার করলে ঐ বীর তৎক্ষনাৎ পর্বতোপরি পতিত
হলো। ফলে তার বামভাগের হনুদেশ ভগ্ন হলো। বায়ু ইন্দ্রের উপর কুপিত হয়ে স্বীয় গতি রোধ
পূর্বক পুত্রকে নিয়ে গিরিগুহায় প্রবেশ করলেন। বায়ু নিরোধে সকলে যেন উদরীরোগগ্রস্ত হয়ে
ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলো। তখন ব্রহ্মা সকলকে নিয়ে বায়ুকে প্রসন্ন করবার জন্য তার অবস্থান
স্থলে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মার করস্পর্শ পাওয়া মাত্র শিশু পুনর্জীবন লাভ করলো।
পুত্রকে
জীবিত দেখে বায়ু আনন্দে পুনরায় জগতে বিচরণ করতে লাগলেন। ব্রহ্মা দেবগণকে বললেন- এই
বালকের দ্বারা তোমাদের কোনও গুরুতর কার্য সাধিত হবে, অতএব তোমরা বায়ুর তুষ্টির নিমিত্ত
বালককে বর প্রদান কর।
তখন
ইন্দ্র বললেন- যেহেতু আমার বজ্রে এ শিশুর হনুভঙ্গ হয়েছে অতএব এর নাম হবে কপিবীর হনুমান।
অতঃপর আমার বজ্রে এর মৃত্যু হবে না।
সূর্য
বললেন- আমার তেজের শততম অংশ দান করলাম। এর শাস্ত্রাধ্যয়নের শক্তি যখন জন্মাবে তখন একে
শাস্ত্রদান করবো।
বরুণ
বললেন- আমার বরে অযুত শতবৎসরেও এর মৃত্যু হবে না এবং আমার পাশাস্ত্র ও জলেও এর কোন
আশঙ্কা নেই।
যম
বললেন- এ আমার দন্ডের অবধ্য হবে, আরোগী হবে ও যুদ্ধে কদাচ বিষণ্ণ হবে না।
কুবেরের
গদা ও বিশ্বকর্মা নির্মিত দিব্যাস্ত্রেরও অবধ্য হবে এ সন্তান। ব্রহ্মা তাকে দীর্ঘায়ু,
ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মশাপে মুক্ত থাকার বর দিলেন।
বরলাভে
বলীয়ান হনুমান তখন ঋষিগণের উপর অত্যাচার শুরু করলেন। তখন ভৃগু ও অঙ্গিরার বংশীয় ঋষিরা
হনুমানকে এই অভিশাপ দিলেন যে অতঃপর কেউ তাকে স্মরণ করিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত নিজ বল সম্পর্কে
হনুমান দীর্ঘকাল অজ্ঞান থাকবেন।
এই
অভিশাপে হনুমানের বল ও তেজ খর্ব হলো ও তিনি শান্তভাবে আশ্রমে বিচরণ করতে লাগলেন।
এই
কারণেই বালী সুগ্রীবের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে হনুমান যেহেতু নিজের বল জানতেন না তাই
তিনি সুগ্রীবের মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা হিসেবেই থাকেন, যুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকেন। সমুদ্রলঙ্ঘনকালে
জাম্ববান হনুমানকে তার অতীতের বলবীর্যের কথা স্মরণ করালে হনুমান আত্মজ্ঞান লাভ করে
সমুদ্র লঙ্ঘনে সমর্থ হন।
রামায়ণ,
হে পাঠক আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে একটি nature myth। রামায়ণ কৃষি
ও কৃষি সংক্রান্ত সংস্কৃতির প্রতীক। যে রামায়ণ গান লব কুশ রামকে শোনাচ্ছেন তার অর্থ
দ্বিমাত্রিক, উদ্দেশ্যও দ্বিমাত্রিক। প্রাথমিকে তা কৃষি, জ্যোতিষ ও আবহ বিজ্ঞানের পুরাকথা,
দ্বিতীয় অর্থে রামের কীর্তিগাথা। প্রাথমিক উদ্দেশ্যে রামের কাছে লব কুশকে তার সন্তানরূপে
ও তার রাজসিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকাররূপে প্রতিষ্ঠা, প্রমাণ করা ও দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে
সেই সূত্রে এক মহাকাব্য রচনা।
এবং
এই nature myth এর, “রামায়ণের উৎস কৃষি”র আলোকে আমরা আবিষ্কার করবো হনুমান হলেন বায়ুর
একটি বিশেষ রূপ- তিনি মৌসুমি বায়ু- monsoon personified!!
হনুমান
চরিতের বক্তা অগস্ত্য অর্থাৎ অগস্ত্য নক্ষত্রে শরৎকাল। শ্রোতা রাম অর্থে বর্ষাকাল।
যে উত্তর-পূর্বমূখী বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ সমুদ্র থেকে রাশি রাশি মেঘ টেনে এনে উত্তরে হিমালয়ে
এসে গতিশক্তি হারিয়ে ফেলে সেই বায়ুপ্রবাহই রামায়ণে পবনপুত্র হনুমান।
এই
বায়ু পর্বতের গা বেয়ে উর্দ্ধমুখী হয়। সেই প্রবাহে মেঘ উর্দ্ধে উঠে হিমবাহের শৈত্যপ্রবাহে
কুয়াশা ও তুষারে পরিণত হয়ে পতিত হয়। আবহমণ্ডলে শীতলতা বাড়ে। সূর্যও নিরক্ষরেখার কাছাকাছি।
উষ্ণতা তাই কম। তাই সূর্যকে বলা হয়েছে শিশুসূর্য। এবং এই সূর্যের প্রতি রাহুও সূর্যগ্রহণ
কারণে ধাবিত। এই সূর্য তাপহীন তাই উর্দ্ধমুখী মেঘের ও বায়ুর উপর তার তাপ প্রযোজ্য নয়।
যেমন সূর্যদেব হনুমাণকে দগ্ধ করেন না। কিন্তু শৈত্যপ্রবাহ মেঘকে গতিহীন করে ও তুষারে
বজ্রবৎ পরিণত করে। তাহাই হনুমানের উপর বজ্রপ্রহার।
উত্তর
পূর্বমুখী বায়ু বাম দিক থেকে ভারতে ঢোকে ও তার প্রবাহশক্তি নষ্ট হয়ে প্রায় স্তব্ধ হয়ে
যায়। ইহাই হনুমানের বাম হনু ভঙ্গ ও ইহাই বায়ুর গুহামধ্যে অবস্থান।
হিমালয়ে
গতিশক্তি স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পর হিমালয়ের গর্ভে দক্ষিণমুখী বায়ুপ্রবাহ শুরু হয়। ইহাই
ব্রহ্মার স্পর্শে হনুমানের পুনর্জন্মলাভ।
শারদকালের
শুরুতে হিমালয়ে যে তুষার ঝড় হয় তাকেই বরলাভে বলীয়ান হনুমানের ঋষিদের উপর অত্যাচার বলা
হয়েছে। এই প্রচন্ডতার বিনাশ হয় শিখরে ও ঘন বৃক্ষরাজিতে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে। তাই ভৃগু
ও অঙ্গিরার (অঙ্গার বা ঋকবেদে বর্ণিত আদিপুরুষবৎ অঙ্গিরসগণ) অভিশাপ।
বরলাভের
প্রসঙ্গটি এবার আলোচিত হোক। হনুমানের নবজন্ম অর্থাৎ শরৎকালীন দক্ষিণাধিমুখী বায়ুপ্রবাহ
মেঘে মেঘে ঘর্ষণে অর্থাৎ বজ্রাঘাতে ব্যাহত হয় না। ইহাই ইন্দ্রের বর।
সূর্যের
বরে তেজের শততম অংশ ও পরবর্তীকালে শাস্ত্রাজ্ঞান। দক্ষিণাভিমুখী বায়ুর মন্দগতি ও ধীরে
ধীরে তেজ/গতিশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকা। শাস্ত্রজ্ঞান প্রসঙ্গ হনুমান as a sun-god যেখানে
আলোচনা করবো সেখানে বলবো।
বরুণের
বর অর্থে চিরন্তন এই মৌসুমী বায়ু চক্র অর্থাৎ অমর। যম দন্ড অর্থে শাস্তি বা বাধা প্রদান
করা। কেউই এই মৌসুমী প্রবাহকে বাধাদান করতে সক্ষম নয়।
যখন
ভূখন্ডে প্রচণ্ড শীত তখন দক্ষিণাভিমুখী বায়ুপ্রবাহ পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পরিত্যাগ করে
সমুদ্রে প্রবেশ করে। বসন্তেই তাই জাম্ববানের কথায় নিজেকে স্মরণ করে প্রবল পরাক্রান্ত
বিক্ষুব্ধ বায়ুরূপে হনুমানের সাগরপার করে লঙ্কা গমন।
এ
প্রসঙ্গে তাই আর একটি বিষয়ে আলোকপাত করে আমরা বহুমাত্রিক হনুমান interpretation এর
অন্য অ্যাঙ্গেলে চলে যাব। যেহেতু গ্রীষ্মকালে রক্তসূর্য যত তপ্ত আগুনবৎ রশ্মি বর্ষণ
করবে বর্ষাকালে তত মৌসুমীবায়ু জলীয় বাষ্প সহ ভূখন্ডে প্রবেশ করবে, উত্তরাভিমুখী এই
বায়ুও তাই রক্তবর্ণ। পরাক্রমের যেমন জ্ঞানেরও তেমন বর্ণ আলোকময় তেজোদীপ্ত রক্তাভ। তাই
হনুমানকে লাল সিঁদুরলিপ্ত করার চল চলে আসছে।
জ্যাকবির
মতে রামায়ণ ঋকবেদে বর্ণিত প্রাচীন একটি মিথের পরিবর্ধিত রূপ। ঋকবেদে সীতাদেবীর উল্লেখ
আছে ও তিনি ইন্দ্র/পর্জন্যের স্ত্রী। যাইহোক, একদা বৃত্ত নামের অসুর দেবতাদের গোধন
হরণ করেন। ইন্দ্র পবনদেব ও মেঘেদের সঙ্গে নিয়ে সরমা নামক দেবকুকুরীর সহায়তায় রসনদী
অতিক্রম করে বৃত্তকে বধকরে গোধন পুনরুদ্ধার করেন। এই সরমা হলেন বিভীষণ পত্নী যিনি সীতার
সখী হিসেবে অশোক বনে ছিলেন ও রামের মায়ামুন্ড দেখে শোকাতুরা সীতাকে মোহ থেকে রক্ষা
করেছিলেন। আর দেখার বিষয় রসনদী বা সাগর ইন্দ্র পার হচ্ছেন পবনদেব ও মেঘেদের সহায়তায়
যারাই কিনা যথাক্রমে হনুমান ও বানর সেনা।
বস্তুতঃ
সংকালিয়া সহ বহু ইতিহাসবিদ ও রামায়ণের উপর পাণ্ডিত্যময় গ্রন্থস্রষ্টাদের মতে হনুমান
প্রকৃত পক্ষে মেঘরাশি বা cloud এর প্রতীক। রামের সঙ্গে হনুমান তেমনই একাত্ম যেমন মেঘের
সঙ্গে বজ্রের সম্পর্ক! অবিচ্ছেদ্য। একে অন্যকে বিনা অস্তিত্বহীন আর একজন থাকলে অন্যজনও
অবশ্যই আছেন। একমাত্র মেঘের পুঞ্জ যে রাহু ব্যাতীত সূর্যকে সাময়িক সময়ের জন্য হলেও
গ্রাস করতে পারে। ঠিক যেমন হনুমান শিশুবয়সে সূর্য খেতে গিয়েছিলেন। আবার পৃথিবীর প্রান্তর
থেকে মুগ্ধবিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকাও। সূর্য আর মেঘ যেন ধানের রৌদ্রছায়ার মতোই লুকোচুরি
খেলছে। তারা মিত্র, তারা পরস্পরের পরিপূরক, বিজ্ঞান অনূযায়ীও, সূর্যের তেজ আছে, তাই
মেঘের সৃষ্টি। সূর্য মেঘের হেতু, সূর্য মেঘ ভগবান ও ভক্ত। রামায়ণে হনুমান বৈশিষ্ট্য
বর্ণনায় বারবার আমাদের সূর্যের রেফারেন্সে ফিরে যেতে হবে। আপাতত চলুক।
আবার
এও ভাবুন যে হনুমান ঠিক তখনই সূর্য খেতে যাচ্ছেন যখন কিনা সত্যিই সূর্যগ্রহণের ক্ষণ।
একইসময় রাহুও সূর্য খেতে যাচ্ছেন। আসলে রামায়ণ আর্য সভ্যতার গৌরবমদে মত্ত এক সেলফ অ্যাকেল্মড
শুচিবায়ুগ্রস্তা। সে শুধু পলিটিক্যাল বা সামজিক স্তরেই নয়, মনের বিষয়েও চরম শুচিবায়ুগ্রস্ত।
যা কিছু জ্যোতির্ময়, conscious, যা কিছু দিন, আলো ও সূর্য সংক্রান্ত সেখানে সব কিছুই
পবিত্র। আর অপবিত্র রাহু... সূর্যগ্রাসী, unconscious অন্ধকার ও রাহুর উপাসকসম অনার্য
রাক্ষসদের অশুচিতার বিপরীতে এক অবস্থান হনুমানকে দিয়ে সুর্য গ্রাস করানো। আর্য জাতি
সম্মত এক parallel পবিত্র সূর্যখাদক তৈরি ও অনুমোদন। যার মাধ্যমে সেই অশুভ অন্ধকার, অপবিত্র unconscious থেকে নিস্কৃতি পাওয়ানোর এক অল্টারনেট নিজপক্ষীয়
ফোর্স পাওয়া যায়। তাই হলেন হনুমান - তাই তিনি মেঘপুঞ্জ - তাই তিনি ইন্দ্র/রাম/পর্জন্যের
শ্রেষ্ঠতম follower। তিনি আর্যসম্মত সূর্যখাদক।
এবার
আমরা একটা সস্তার দুপয়সার গাল গল্পে চলে যাব। এ লেখায় সেখানে যাওয়ার দরকার পড়েছে।
অঞ্জনীকুমার
খন্না জন্মেছিলেন শিয়ালদার এক পাড়ার কেশরীকুমারের তৃতীয় পুত্র রূপে। একেবারে শৈশবে
নাকি সাপকেও মানুষ নির্দ্ধিদায় হাতের মুঠোয় ধরে কারণ সাপ কি বিষম বস্তু তা সে জানে
না। তার কাছে গোটা পৃথিবীটাই নতুন। খিদে পেলে সূর্যকে দেখে তারও হয়তো আপেলের কথা মনে
হতো । বিরাট জলন্ত গোলা আর স্নিগ্ধ চন্দ্রিমা অপার বিস্ময় জাগিয়েছে সভ্যতার আদিমপর্বের
শিশুঋষি থেকে শিয়ালদার ল্যাংটো ছেলে সবারই মনে সমানভাবেই জাগিয়েছে।
সেই
অঞ্জনীকুমারের তখন ছোট্ট বয়েস। পাড়ার পাশের বাড়ি ডাকাত পড়েছিল। অঞ্জনী তিনতলার ন্যাড়া
বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল কিচ্ছুটি না জেনে। জানার তার বয়সও নয়। হাত টবে লেগে অ্যাক্সিডেন্টালি
পড়েছিল ডাকাতদলের মাতব্বরের মাথায়। বলাই বাহুল্য তারা ডাকাতির মাল ইত্যাদি ফেলে চম্পট
দেয়।
তখন
থেকে অঞ্জনী পাড়ার দি ব্রেভেস্ট বয়। অঞ্জনী পাড়ার সেলিব্রিটি বালক। তার সাহস, তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের
প্রশংসা শুনে শুনে বড় হতে থাকে অঞ্জনী ও যেকোন বড় সমস্যায় “আমাদের অঞ্জনী আছে” গোছের
আত্মবিশ্বাসে পাড়া মজে থাকে মৌতাতে।
এদিকে
বড় হয়ে অঞ্জনী হয় ভীরু কবি গোছের। কোন “রামজন্মে” হাতে টব লেগে পড়ে গিয়েছিল পড়বি তো
পড় ডাকাতের মাথায়- আর সেই টবের ফুলের গন্ধ শুঁকে শুঁকে বড় হওয়া অঞ্জনীর ভালো লাগে না
তাকে নিয়ে এই সাহসীর মিথ। তার মন্দও লাগে না, লোকগুলো অন্য নজরে দেখে, সম্মান করে,
মুশকিল আসান ভাবে- মন্দ লাগে না। এভাবেই চলছিল।
তারপর
একদিন সত্যিই পাড়ায় আবার বড় ডাকাত পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ডাকাতি চালিয়ে যখন তারা রাস্তায়
নেমেছে কবি সন্মেলন করে ফিরছে ফিনফিনে পাঞ্জাবীর অঞ্জনী। একেবারে মুখোমুখি। অঞ্জনীর
কানে সেই ছোট্টবেলা থেকে শুনে আসা বিপদভঞ্জন অরিত্রসূদন স্তোত্র বাজতে লাগলো। গোটা
পাড়া তখন দেখছে তাদের হিরো আর ডাকাত দল রাস্তায় মুখোমুখি।
ছেলেবেলায়
যা ছিল নেহাত অ্যাক্সিডেন্ট এবং তারই সুবাদে
পাওয়া বিশেষণগুলোর প্রতি সুবিচার করেছিল অঞ্জনী। ডাকাতদের বাধা দিতে গিয়ে তিনবার
ছুরিকাহত হয়ে মারা গিয়েছিল হাসপাতালে। মারা যাওয়ার সময় এ শান্তি তার ছিল যে ... যা
ছিল সমাপতন- যা ছিল মিথ - যা ছিল অলীক - তাকে সত্য করে দিয়ে গেল সে। বীর হয়ে প্রমাণ
করে গেল তার বীরত্বগাথা গাঁজা গল্প ছিল না - তার বীরত্ব মিথ সমাপতন নয়। সে মানবের হৃদয়ের
আবেগের সাগরের পাড়ে সহস্র যোজন হনুমানের আকার নিয়ে পেরিয়েছিল সেই আবেগ মিথ সমুদ্র।
তবে তার নামে পাড়ায় বসেছিল শহীদবেদী, তবে তার নামে পাড়ার রাস্তার নামকরণ হয়েছিল। ভীতু
রুগ্ন আঁতেল কবি হয়েছিল বীর personified- অমর!
গল্প
আমার আসে না। কিন্তু এরকমই হনুমানের আধুনিক গল্প। আরে ছোটবেলায় সবাই সূর্য খেতে যায়।
ছোট বেলায় সবাই অনন্ত সম্ভাবনার আধার। বড় হয়ে হাজার ভয় লজ্জা বাসনা লোভ লক্ষ বাধা নিষেধ
অবদমন অতিক্রম করে যে সেল্ফ অ্যাকচুয়ালাইজ করে যে আমি মর্গের ইঁদুর নই - আমরা সবাই
ঐরাবত তখনই শুধু মেন্টাল স্টেটের বদল ঘটে কবি প্রাবন্ধিক বাগ্মী অথচ ভীতু রুগ্ন হনুমান
থেকে সহস্রযোজন আকৃতি ও সমুদ্র লঙ্ঘন ক্ষমতাবান হয় যে কোন মানুষ। যে কেউ। তখন তাকে
অমর পূজনীয় বলা হয়।
বস্তুতঃ
হনুমান child-hero, শিশুরা সবথেকে বেশি ভালোবাসে হনুমান চরিত্র। তার মধ্যেই নিজের
identification খোঁজে শিশুরা। শিশুদের কল্পনাশক্তি, অপার বিস্ময় ও পবিত্র মন যতদূর
যেতে পারে ততই অদ্ভূত বিস্ময়কর ভক্ত হনুমানের কীর্তিকলাপ। A child is smaller than
small, bigger than Big. A child is younger than young and older than old. A
child is beginning/unconscious and a child is the end/post-conscious। একটি বস্তু
যত ছোট তার শক্তি ততই বেশি। তাই পরমাণুর মধ্যেও হাইড্রোজেন যেহেতু ক্ষুদ্রতম ও হাল্কাতম
পরমাণু ( মাত্র একটি প্রোটন , কোন নিউট্রনও নেই) তাই হাইড্রোজেন বোমাই পরমাণু বোমার
মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী। তাই হনুমান অন্যান্য বানরদের মতোই চপল শিশুসুলভ আবার মহাপ্রাজ্ঞ
অপেক্ষাও জ্ঞানী, স্থিতধী। হনুমান জন্মেই অমর! আর হনুমান পর্বত তুলে আনেন, হনুমান লঙ্কায়
আগুন লাগান, হনুমান উড়তে পারেন- আর কি চাই এক শিশুর! বলতে গেলে তো বলতে হয় বাল্মীকির
যাবতীয় অলৌকিক হনুমানে attached, হনুমানের মধ্য দিয়েই তার যাবতীয় অলৌকিক কল্পনার শিশুত্ব
বেরিয়ে এসেছে- কে জানে ঋষি বাল্মীকির কাছে কে বেশি মনের আপন- তপস্বী বাল্মিকীর হয়তো
রাম কিন্তু সাধারণ মানুষ বাল্মীকির হয়তো হনুমান লব কুশ ! তার তাই জনসাধারণের মধ্যেও
রামের মূর্তি মন্দির বা সাধনা যত না তার থেকে হাজার গুণ বেশি পপুলারিটি হনুমানের! এ
বিষয়ে স্বতন্ত্র গবেষণা করে দেখা যেতে পারে কিন্তু!
ইয়ুঙেই
মহাকাব্য বিশ্লেষণের মনস্তত্ব আটকে থাকা উচিত নয় কিন্তু হনুমানের সাগর পাড় হওয়ার পিছনের
মনস্তত্ব ও পুরাকথা ইয়ুং এর rebirth তত্ত্বে যেভাবে পরিস্ফুট হয়েছে, তার উল্লেখ না
করলেই নয়।
সূর্য
প্রতিদিন ওঠে পূর্বদিকে, অস্ত যায় পশ্চিমে। পরের দিন কিন্তু পশ্চিম থেকে সে ওঠে না!
ওঠে আবার পূর্ব দিক থেকেই।
Horizon
থেকে সূর্য জন্ম নেয়, Horizon এই মারা যায়। আসে আদিম মানবের ভয়ের অন্ধকার রাত। সেই
আন্ধার তার কাছে ম্যাডেনিং- যেন মাতৃগর্ভের আঁধার! সূর্যও গোটা রাত তাই সমুদ্রের পশ্চিম
পার থেকে পূর্বের দিকে সমুদ্রের জলের মধ্য দিয়ে বা mother womb এর মধ্য দিয়ে যাত্রা
করে পূর্ব দিকে নতুন ভাবে জন্মগ্রহণ করে, তার Rebirth হয়। মাতৃগর্ভের সঙ্গে জলের তুলনা
বাসমুদ্রের তুলনা উপনিষদেও আছে। বাস্তবেও অ্যামোনোটিক ফ্লুয়িডেই ভ্রুণ ভাসে ও কিছু
কিছু suckও করে ম্যাচিওর হলে। এমনকি সৃষ্টির আদিতে সব জীবই জলচর ছিল- তা থেকে উভচর,
সরীসৃপ থেকে মেরুদন্ডী স্তন্যপায়ী ইভলিউসন হতে হতে মানুষের ভ্রূণের সৃষ্টি- মাতৃগর্ভে
এই পুরো প্রসেসটিই চলে।
নোয়ার
যে নৌকো তাও এই মিথের অঙ্গ। চারদিকে অনন্ত জলে মাতৃগর্ভের মধ্যেই যেন সৃষ্টির বীজ নিয়ে
লালন করে নোয়া। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এইধরণের Rebirth মিথে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গমনকারী
জীব/Sun-God নানা বাধার সম্মুখীন হয়- শেষে মাছ বা রাক্ষসীর পেট চিরে পূর্বপারে পদার্পন
করে। সে slipped out করে গর্ভ থেকে, সমুদ্র থেকে আবার পূর্ব horizon এ নতুন reborn
সূর্যরূপে।
হনুমানের
সাগর পার হওয়ার প্রাথমিক অবস্থা হল Threshold ও মানসিক adolescence অতিক্রম করে
unconscious থেকে pre-conscious হয়ে ego formation দিকে যাত্রারম্ভ । অসংখ্য রূপকথা
ও মিথে হিরো এ ভাবেই তার নিজের লক্ষ্যের দিকে যাত্রা শুরু করে যা কিনা প্রকৃত পক্ষে
নিজের আত্মানুসন্ধান ও নিজের self বা আত্মনকে উপলব্ধি করার মাধ্যমেই (ড্রাগন মেরে রাজকন্যা
ও অর্ধেক রাজত্ব) তা পরিপূর্ণতা লাভ করে।
তো
সাগরপার হওয়ার জন্য লাফ দেওয়ার সময় প্রায় সন্ধ্যাকাল। শুরু হয়ে গেছে হনুমানের
night journey through sea। অর্থাৎ হনুমানের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে
transformation of self প্রক্রিয়া যা দুই বিপরীতের মিলন ঘটাবে - পুরুষ অপেক্ষা করে
আছে তার বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির জন্য - হনুমান সাগরপার হচ্ছেন সীতা / Great Mother এর খোঁজে।
আর যাবতীয় বিপরীত শক্তির মিলনের প্রতীক হিসেবে প্রথমেই উড়তে সক্ষম বায়ু বা মেঘকে বাধা
যে দেয়, যে তার শক্তি নাশ করে সেই পর্বত(মৈনাক)হনুমানের সঙ্গে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হয়ে
তার ক্লান্তি দূর করতে এসেছেন। এরপর সাগরপার করতে গিয়ে দুইজন রাক্ষসী হনুমানের পুনর্জন্মলাভ
বা অমরত্ব ও সীতা/মহীয়সী মাতার সঙ্গে মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছেন। একটি পজিটিভ ও
একটি নেগেটিভ ফোর্স।
দেবতা
গন্ধর্ব ও মহর্ষিগণ পবননন্দনের বুদ্ধি বীর্য ও শক্তি পরীক্ষার জন্য “নাগমাতা” সুরসাকে
রাক্ষসীবেশে হনুমানের পথরোধ করতে আদেশ দেন। এখানে লক্ষণীয় “নাগমাতা” কথাটি। প্রকৃতপক্ষে
রাবণ শব্দের একটি অর্থ serpent(নাগ) এবং রাক্ষস সেই যে যক্ষ বা রক্ষা করছে জলকে। বৈদিক
মিথ অনুসারে তাহলে অর্থ দাঁড়ায় যে জলকে বাধা দিচ্ছে বা obstruct করছে। রাবণ নাগের মতো
চারিদিকে জলদ্বারা আষ্টেপিষ্টে সীতাকে লঙ্কায় বন্দিনী করে রেখেছে। হনুমান সরসার বিরাট
মূখ্যব্যাদানের মধ্যে প্রবেশ করেই বেরিয়ে এসে তার দাবী ও শর্ত মানেন অর্থাৎ রাক্ষসদের
মাতৃশক্তিকে অথবা যদি Rebirth তত্ত্বে সাগরপার প্রসেসের ভিত্তিতে ধরি তবে নিজের
anima সত্ত্বাকে অ্যাকনলেজ করলেন হনুমান। নাগমাতা তাকে আশীর্বাদ করে রাম সীতার মিলন
কামনা করেন।
এরপর
হনুমান Mother of the Rahus-সিংহিকা নাম্নী এক কামরূপী ছায়াগ্রাহী রাক্ষসীর মুখবিবরে
প্রবেশ করে তার মর্মস্থান ভেদ করে বেরিয়ে এসে তাকে হত্যা করেন। এখানে দুটি বিষয় প্রণিধান
যোগ্য- এক, যে এই রাক্ষসী হনুমানের সমুদ্রে পরা ছায়াকে গ্রহণ করে হনুমানকে আটক করেন
আর দুই তিনি jung এর মতে রাহুদের জননী। বুঝতে কোন অসুবিধাই হয় না যে jung তত্ত্বে ইহা
shadow আর ফ্রয়েডে প্রায় id! Shadow হলো animal instinct and personal
unconscious. একই সঙ্গে black cold shadowy aspect of Ego. Self-actualization এর পথে,
wholesome personality develop করার প্রক্রিয়ায় এই animal nature বা shadow কেও স্বীকৃতি
দিতে হয়। Evil কে আগে অ্যাকনলেজ করে, তার ক্ষতিসাধন ক্ষমতাকে চিনে বুঝে নিয়ে তাকে অতিক্রম
করার মাধ্যমেই আত্মজ্ঞানলাভ সম্ভব। সাধক যখন কুন্ডলিনী জাগরণের প্রথম পর্যায়ে আসেন
তখন তিনি গুরুর হাত ধরে সাঁতার শিখতে জলে নামছেন আর তাই এই পর্যায়ের animal হল জলদানব
মকর, যে negative force এর হাত থেকে বাঁচতে শিখতে হবে। নাহলে আত্মজ্ঞান লাভের পথে আর
এগোনো যাবে না। হনুমান তা করেছেন। সঙ্গে পুরুষের শুভ animaর নির্দেশ মেনে তার প্রাপ্য
তাকে দান করে হনুমান শেষবধি পৌঁছাচ্ছেন সেই লঙ্কা The Golden City তে যাও একটি মাতৃপ্রতীক
এবং সন্ধানে রত হচ্ছেন তার ও জাতির মহীয়সী জননী সীতামাতার।
এবং
দেখুন এই দুই বাধাই আসলে কিন্তু মাতৃশক্তি...নাগেদের মাতা আর রাহুদের মাতা। সুতরাং
Sun God Myth এ rebirth তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য মাতৃগর্ভে পুনঃপ্রবেশ (রাক্ষসীদের
দেহ গহ্বরে প্রবেশ/ night journey through sea )
ও বেরিয়ে আসা ( সূর্যের পূর্বপারে slip out করা ) এখানে তাই এত প্রাসঙ্গিক।
এই
সমুদ্র যাত্রা হনুমানকে Fleshy Rebirth নয়, অযোনিজ আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম বা রেজারেকশন
দেয়। হনুমান হয়ে ওঠেন অমর। “It is the longing to attain rebirth through the
return to the mother’s womb, that is to say, to become immortal as the sun “(jung).
এভাবে হনুমান মাতা সীতার সঙ্গে মিলিত হবার বাসনায় সাগরপার প্রতীকে হয়ে ওঠেন
Sun-hero, অবশ্য পাঠক মনে করুন সূর্যের বালক হনুমানকে দেওয়া সেই বরের কথা যে শাস্ত্রজ্ঞান
দেবেন।
এই
অমিতবল বীর যখন ব্যকরণ পাঠ করেন সেইসময় ইনি সূর্যের সম্মুখীন হইয়া হস্তে গ্রন্থ ধারণ
পূর্বক গ্রন্থার্থ জানিবার উদ্দেশ্যে উদয়গিরি থেকে অস্তাচল পর্যন্ত গমনাগমন করিতেন।
ইনি সূত্র বৃত্তি অর্থপদ মহাভাষ্য ও সংগ্রহে অতিমাত্র ব্যুৎপন্ন। এমনকি বেদার্থ নির্ণয়
ও সর্বশাস্ত্র পারদর্শীতায় সুরুগুরুকেও যেন অতিক্রম করেছেন!
এখানেই
instinct এর বিপ্রতীপে ভারতবর্ষ ও তার চতুর্থ লক্ষ্য মোক্ষ! শুধু night journey
for rebirth নয়। বই হাতে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করতে করতেও হনুমান পূর্ব থেকে পশ্চিমের
horizon এ সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে গমন করেছেন। এখান থেকেই আমরা হনুমানের
post-conscious এর দিকে নজর রাখতে শুরু করবো। হনুমান সুতরাং consciouslyও totally
attached with sun। তিনি সূর্যপুত্র সুগ্রীবেরই পক্ষ নিয়েছেন বালী সুগ্রীব দ্বন্দ্বে। এমনকি
অন্য যে সূর্যপুত্র কর্ণ-তাকেও পেটিকায় ( মাতৃগর্ভের প্রতীক box ) চাপিয়ে জলেই ভাসিয়ে
দিয়েছিলেন অবিবাহিতা কুন্তী। কর্ণও আরেক মহান Sun-Hero। সব মিলিয়ে তাহলে
একদিক থেকে হনুমান Monsoon-Cloud আবার অন্যদিকে Sun personified। এবং এদের দ্বৈতসত্ত্বা
নিয়ে আগেই বলেছি সিঁদুর প্রসঙ্গে। সূর্য আছে, তার গ্রীষ্ম তেজ আছে-তাই মৌসুমী বায়ু
মেঘ আছে। পাঠক চলুন হনুমান চরিত্রের বিবিধ interpretation এর মধ্যে integrity আস্তে
শুরু করে দিয়েছে। আমরা সঠিক কিনা জানিনা তবে অন্তত একটি অভিমুখে চলেছি।
সুন্দরকাণ্ডই
রামায়ণে সবথেকে সুন্দর, সর্বাপেক্ষা কবিত্বময় কাণ্ড। বাল্মিকি প্রতিভা তার সর্বশ্রেষ্ঠ
কবিত্বের উদাহরণ দিয়েছেন হনুমানের ন্যারেটিভে। হনুমানের চোখ দিয়ে দেখা ও হনুমানের বর্ণনাতেই
তাই যথার্থ ভাবে এই কান্ডের নাম রেখেছেন পরবর্তী কবিরা। প্রসঙ্গত সর্বশাস্ত্রবিশারদই
এখন বীরও, তিনি এখন self কে অ্যাকচুয়ালাইজ করা complete man। তার ন্যারেটিভ
রামায়ণে ন্যারেটিভের মধ্যে বয়ে চলা আরেক ন্যারেটিভ এবং তাই ই সুন্দরতম এই কাণ্ডের প্রধান
বৈশিষ্ট্য। সুন্দরকাণ্ডে অন্তত হনুমানও আদিকবিসম।
এই
কাণ্ডে আমরা হনুমানকে আবিষ্কার করবো একজন পোড় খাওয়া প্রফেশনাল কাউন্সিলার রূপে। এই
সেই সময় যখন আর দুইমাস মাত্র বাকি যা সীতা রাবণের থেকে চেয়ে নিয়েছেন তাকে উদ্ধার করার
উদ্দেশ্য রাম আসবেন এই আশায়। সীতার কাছে নিয়মিত রাবণ আসছেন, হম্বিতম্বি করছেন আর প্রত্যাখ্যাত
হয়ে চলে যাচ্ছেন। সীতা উদর পা দ্বারা আর স্তন করযুগল দ্বারা আচ্ছাদন করে প্রবল ইনসিকিউরিটিতে
অ্যাংজাইটিতে আতঙ্কিত মানুষ যেমন গুটিয়ে যায় ও প্রবল শীত অনুভব করে সে মত আতঙ্কিত হয়ে
আছেন। “তিনি সন্দেহাত্মক স্মৃতির ন্যায়, পতিত সমৃদ্ধির ন্যায়, স্খলিত শ্রদ্ধার ন্যায়,
নিষ্কাম আশার ন্যায়, কলুষিত বুদ্ধির ন্যায় এবং অমূলক অপবাদে কলঙ্কিত কীর্তির ন্যায়
যারপরনাই শোচনীয় হইয়াছেন”। কোন কবিত্ব নয়, প্রতিটি বিশেষণ যথার্থভাবে সীতার অবস্থা
ও ভাগ্যকে মূর্তভাবে ব্যাক্ত করছে। আরও কবিত্ব উপমাময় অংশও পেশ হলো। “ঐ রাজবন্দিনী
অবসন্ন কীর্তির ন্যায়, অনাদৃত শ্রদ্ধার ন্যায়, ক্ষীণ বুদ্ধির ন্যায়, উপহত আশার ন্যায়,
বিমানিত আজ্ঞার ন্যায়, বিঘ্নবিনষ্ট পুজার ন্যায়, ম্লান কমলিনীর ন্যায়,...দূষিত বেদির
ন্যায়, ও প্রশান্ত অগ্নিশিখার ন্যায় একান্ত শোচনীয় হইয়া আছেন...তাহাকে দেখিলে বোধহয়
যেন তিনি একটি নদী, উহা প্রবাহ প্রতিরোধনিবন্ধন অন্যত্র অপনীত ও শুষ্ক হইইয়াছে।...তাঁহার
মনে নিরন্তর নানারূপ আতঙ্ক উপস্থিত হইতেছে”। বারংবার আত্মহত্যা করার চিন্তা তার মাথায়
ঘুরপাক খাচ্ছে। তিনি নিতান্তই আতঙ্কিত ও নিউরোটিক রোগলক্ষণাক্রান্ত হয়েছেন। নিজের পাতিব্রাত্য
তিনি কোনভাবেই খোয়াতে পারবেন না। “শচী যেমন ইন্দ্রের, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের, রোহিণী
যেমন চন্দ্রের, লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের, সুকন্যা যেমন চ্যবনের, সাবিত্রী যেমন সত্যবানের,
শ্রীমতি যেমন কপিলের এবং দয়মণ্ডী যেমন নলের”... তিনিও তেমনই একমাত্র রামের এবং রাবণ
গমন মানে সীতার self, আত্মসত্ত্বারই যেন মৃত্যু- সতীত্ব খোয়া যাওয়া সীতার কাছে নিজের
আত্মা খোয়া যাওয়া। আবার তিনি একটুকুও পর্যন্ত জানেন না যে, তিনি যে লঙ্কায় বন্দিনী
তা রামের অবগত আছে কিনা। তার কাছে কোন আশাও নেই ভবিষ্যতের জন্য। তাই “জানকী যেন উন্মত্তা,
শোকভরে যেন উদ্ভ্রান্তা”। রাবণকে বরণ করে নেওয়ার বদলে তিনি প্রাণত্যাগ করবেন। “আমি
বিষপান বা শাণিত কৃপাণ দ্বারা আত্মহত্যা করিব...”।
তো
এই হল সীতার অবস্থা। পাগলিনী উদ্ভ্রান্তা অবস্থায় ভয়ে আতঙ্কে অ্যাংজাইটিতে এক সম্পূর্ণ মনোরোগী
অবস্থা। সেই অবস্থা থেকে হনুমান তার বিচক্ষণতা, বাকপটুত্ব ও ভরসা আশ্বাস দিয়ে সীতার
মনের এই স্টেটকে ধীরে ধীরে বদলাচ্ছেন-বলা ভাল কাউন্সিলিং করছেন সীতার।
হনুমান
বুঝলেন শুধু সীতার সংবাদ রামকে গিয়ে দিলেই তার দূত হিসাবে দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না। “যদি ইঁহাকে
প্রবোধ দিয়া না যাই,…এই রাজকুমারী পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন”। সুতরাং সীতার
সহিত রাক্ষসীদের অমনোযোগে কথোপকথন করতে হবে এবং তা করতে হবে সংস্কৃতে নয় কারণ তাহলে
সীতা হনুমানকে রাবণের বা রাক্ষসদের ছদ্মবেশ বলে ভাবতে পারেন। কথা বলতে হবে
“মানুষীভাষা”য় অর্থাৎ সাধারণ মানুষের প্রাকৃত ভাষায়। এ থেকে বোঝা
যায় বহুরকমের ভাষা হনুমানও জানতেন আবার জানকীও জানতেন!
তো
সীতা সর্বদা স্মরণ করছেন রামকে। তাই শান্ত ও মধুরভাবে রামের কীর্তি বন্দনা করলেন
হনুমান। কারণ যে সীতা এখন মনোরোগার মতো সদাসংশয়ী, তার আস্থা বিশ্বাস আগে স্থাপন
করাতে হবে। ঠিক যেভাবে একটি কাউন্সিলিং সেশন শুরু করেন একজন অভিজ্ঞ সেন্সেটিভ কাউন্সিলার।এতক্ষণে হনুমান
কিন্তু নিশ্চিত যে ইনিই সীতামা। কিন্তু তৎক্ষণাৎই কিন্তু তিনি রামের সংবাদ ও নিজের
পরিচয় সীতাকে দিলেন না কারণ ভঙ্গুর সংশয়ী মনের সীতা’র পক্ষে হঠাৎই এত উত্তেজনার চাপ
নেওয়া সম্ভব নয়। হনুমানের রামবন্দনায় সীতা তাকে দেখতে পেলে হনুমান গাছ থেকে আরো নীচে নেমে
এসে বরং সীতারই পরিচয় অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও বাকপটুত্বের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন এবং
বললেন যদি আপনি সীতা হন তো প্রত্যুত্তর করুন। just সীতাকে মোল্ড করা-সীতাকে ধাতস্থ হতে দেওয়া,
তাকে শান্তভাবে রামের সংবাদ দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করছেন হনুমান।
সীতা
নিজের পরিচয় দিলে হনুমানও আপন পরিচয় দিয়ে ও রামলক্ষণের কুশলসংবাদ দিতে দুপা নেমে সীতার
নিকটস্থ হতেই আবার শুরু হলো বিকারগ্রস্তা সীতার প্যানিক। এতকিছুর পরেও আবার তার মনে
হতে শুরু করলো রাবণই মায়াবলে রূপান্তরগ্রহণপূর্বক তার কাছে আগমন করেছে। এত ভয় পেলেন
যে হনুমানের দিকে তাকাতে পর্যন্ত না পেরে চোখ বুজলেন এবং বলতে লাগলেন যে জনস্থানে যেভাবে
রাবণ স্বীয়রূপ বর্জন ও সাধুর বেশ ধারণ করে তার সঙ্গে ছলনা করেছিলেন আবারও সেই খেলা
খেলতে এসেছেন। আবার ভাবছেন এ স্বপ্ন। “অদৃষ্টদোষে স্বপ্নও আমার শুভদ্বেষী শত্রু হইয়াছে”।
নিজেই নিজেকে উন্মাদজ বিকারগ্রস্তা, উন্মাদবৎ মোহের শিকার ও হ্যালুশিনেসন দেখছেন এসব
বলছেন জানকী।
হনুমান
এবারও অতিমধুরভাষণে রামগুণকীর্তন করে জানালেন যে তিনি রাবণ নন। তখন রাম-লক্ষণের
অঙ্গে যা যা অভিজ্ঞান চিহ্ন আছে তার বর্ণনা চাইলেন সীতা। রাম বানর মিত্রতার কাহিনীও
জানতে চাইলেন। হনুমান প্রথমে রাম পরে লক্ষণের দেহ বৈশিষ্ট্যবর্ণনা করলেন এবং বালী-সুগ্রীব
বৈরিতা, রামের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ, রাম-সুগ্রীব মৈত্রী, বালি বধ, সম্পাতির মুখে
পাওয়া সীতার সংবাদ, সাগরপার যাবতীয় বিবরণ পেশ করলেন আর নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে তার পিতৃপরিচয়
বিস্তারিত দিলেন। “আমি কপিবর কেশরীর পুত্র। কেশরী মাল্যবান নামে এক উৎকৃষ্ট পর্বতে
বাস করতেন। পরে তথা হইতে গোকর্ণ পর্বতে প্রস্থান করেন। তিনি তথায় পবিত্র সমুদ্রতীরে
দেবর্ষিগণের আদেশে শাম্বসাদন নামে এক অসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। আমি এই কেশরীর ক্ষেত্রজাত
ও বায়ুর ঔরস পুত্র”।
এবং
এরপর রামদূত হিসাবে মোক্ষম প্রমাণ রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় সীতাকে দেখানো। এবার আর্কিওলজির
দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি দেখা যাক যেমন দেখেছেন সংকালিয়া তার “রামায়ণ-myth or
Reality?” নামক পুস্তকে। শকুন্তলা ও রামায়ণে এই ওনারের ( রাজার ) নামাঙ্কিত আংটির কথা
পাওয়া যায়। কিন্তু ২৫০০ খ্রী.পূ. থেকে খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দী অবধি ভারতে প্রচলিত
সব আংটি ছিল একেবারে সাধারণ ধরণের, তামা ব্রোঞ্জ বা টেরাকোটার সিম্পল তারে বানানো।
একমাত্র হরপ্পায় এমন আংটির সন্ধান পাওয়া গেছে যেখানে flat broad space আছে যাতে নামকরণ
খোদাই করা সম্ভব। নামাঙ্কিত আংটির প্রচলন করে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ইন্দো-গ্রীকেরা যার
সময়কাল কোশাম্বীর মতে খ্রী.র্পূ. দ্বিতীয় শতকের শেষভাগ থেকে খ্রী.র্পূ. প্রথম শতকের
শুরুতে। সুতরাং রামায়ণ ও কালিদাসের সময়কাল নির্ণয়ে এই নামাঙ্কিত আংটি ও তার ইতিহাস
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
যাই
হোক প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলি যে, সীতা এবার নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হলেন। কেন রাম এখনো নিশ্চেষ্ট
ইত্যাদি পরিতাপের মধ্যেও বললেন- “আমি যতক্ষণ তাঁহার সংবাদ পাইব, জানিও, তাবৎকাল আমার
জীবন”। উপবাসে কৃশা ধূলিমলিনা জানকীর এই সুইসাইডাল টেন্ডেন্সির দিকে বারবার দৃষ্টি
ফেরাতে হচ্ছে হে পাঠক একথাই বুঝিয়ে বলতে যে হনুমানের মধ্যে এই সময়ে কি নিপুণ কাউন্সেলিং
গুণ ও মনস্তত্ব বিষয়ে জ্ঞান ও কমন সেন্স আমরা আবিষ্কার করছি। হনুমান জানালেন রাম এখনও
জানেন না যে সীতা লঙ্কায় বন্দিনী। এবং রাম আমিষ মদ্য ত্যাগ করে শাস্ত্রবিহিত বন্য ফলমূলে
দিনাতিপাত করছেন। এবং রাম নিয়মিত সীতাকে স্মরণ করে বিরহে আকুল।
এবার
এক সতীত্ব বাধ্য হয়ে হারাতে বসা পতিব্রতা নারীর সাইকোলজি অসীম নৈপুণ্যে ধরেছেন আদিকবি।
সীতা বললেন- “দূত! তোমার কথা বিষ মিশ্রিত অমৃত; রাম অনন্যমনে আছেন এই বাক্য অমৃত আর
তিনি নিতান্ত শোকাকুল, এই কথা বিষ”। তার আবার সেই আত্মহত্যা, বিষ এইসব উপমাই মনে পড়ছে।
“দ্যাখ, যাবৎ না এই সংবৎসর পুর্ণ হইতেছে, ততদিন আমি প্রাণধারণ করিব। এটি দশম মাস,
সুতরাং বর্ষশেষের আর দুই মাস কাল অবশিষ্ট আছে”। পরে আমরা জানকীর মুখ থেকে আর একমাস
কাল বাকি আছে একথা শুনবো। এ থেকে আন্দাজ করা যায় হনুমান একমাস কাল যাবৎ লঙ্কায় ছিলেন।
এরপর
হনুমান সীতাকে পিঠে নিয়ে সাগর “সন্তরণ” করে রামের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। রাম ছাড়া
অন্য পুরুষের দেহ স্পর্শ করবো না, সীতার এই বাক্যে মোহিত হয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। দেখা যাচ্ছে
যে সীতা হনুমানের সঙ্গে যদি চলে আসতেন তবে রামায়ণ রাম নয় হনুমানের বীরগাথা বলেই চিহ্নিত
হতো। সীতা তা বুঝেছিলেন। আমরা দেখছি রামায়ণ হনুমান ছাড়া চলে না। মহাভারত যে কাউকে বাদ
দিয়ে এমনকি যুধিষ্ঠির ভীষ্ম অধিক কি কৃষ্ণ বাদ দিয়েও চলতে পারে, রামায়ণে রামকে আধুনিক
সিনেমায় অন্ত্যজ ভীতু অভিরাম বানিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু হনুমানকে ছাড়া রামায়ণ চলে না-
তাও তার ১০০% নয়, হনুমানের পূর্ণ ক্ষমতার ভগ্নাংশ প্রকাশিত রামায়ণে, তবু তাকে ছাড়া
যে চলে না এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে।
জানকীও
হনুমানকে তার চূড়ামণি খুলে দিলেন। এরপর এই কাউন্সিলিং সেশন শেষ হওয়ার মুখে। যে আশা,
যে নতুন করে ভবিষ্যতে বিশ্বাস, আত্মসম্মান ও ক্যাথারিসিস করে মানসিক শান্তি পেয়েছেন
সীতা তা এই বিচ্ছেদের সময় তার বারংবার হনুমানকে পিছু ডাকায় স্পষ্ট।এতটুকু আশার আলো
দেখেছেন তিনি, তা আর হারাতে যেন চান না। তার দৃঢ় বিশ্বাস রামের কাছে ফিরে গিয়ে আবার
হনুমানই আসবেন তাকে উদ্ধার করতে!! হনুমানকে আবার পিছু ডেকে কান্না চাপা গলায় আবার রামকে
তার সংবাদ দিয়ে দ্রুত তাকে উদ্ধার করতে বলেছেন। আবার সীতা হনুমানকে প্রস্থানে উদ্যত
দেখিয়া বারংবার দেখিতে লাগিলেন। তাকে লঙ্কায় একদিন থেকে যেতে বললেন। “বলিতে কি,তোমাকে
দেখিলে এই মন্দভাগিনীর শোক ক্ষণকালের জন্য উপশম হইতে পারে”।
হনুমান
প্রবোধও যথাসাধ্য দিয়ে গেছেন সীতাকে, বিশ্বাস ও মন জয়ের পর যথাসম্ভব আশা জাগিয়ে তুলেছেন
বৈদেহীর মনে। বলেছেন একটি মিথ্যে কথা। বলেছেন সুগ্রীববাহিনীতে তিনি নিতান্ত নিকৃষ্ট
বানর, তার থেকে অনেক বলশালী বানর আছেন যারা অনায়াসে সাগ পার করবেন। হ্যাঁ, হনুমান মিথ্যা
প্রবোধ দিয়েছেন। অসহায় পাগলিনীর তা দরকার ছিল।
এরপর
হনুমান ফিরে যেতেই পারতেন সমুদ্রের উত্তরপাড়ে। কিংবা একমাত্র রামায়ণের মেরুদন্ড হনুমান
বলেই তিনি শত্রুদের বল বীর্য সম্যক জানতে ও তাদের কয়েকটাকে মেরে শত্রুর মধ্যে ভয় উৎপাদন
করার নিমিত্ত একে একে বধ করলেন কিঙ্করগণ, জাম্ববালী, পঞ্চসেনাপতি, মন্দ্রিকুমারগণ,
মহোদর ও রাবণ পুত্র অক্ষকে। এখানে point to noted যে প্রথমে রাবণের পক্ষে যুদ্ধে করতে
আসছে কিঙ্কররা আর হনুমানও এখান থেকেই এরপর নিজেকে চিহ্নিত করেছে রামকিঙ্কর ও রামের
ভৃত্যরূপে ও তার মুখে নিরবিচ্ছিন্ন রাম নাম জপ চলছে। এখান থেকে রাম ও সীতাকে পেয়ে
complete transformed self হনুমান এখন ভক্তপরাকাষ্ঠা, ভৃত্য বা বৃত্ত যে এখন থেকে রামকে
কেন্দ্র করে চার যুগ আবর্তিত হতে থাকবে। বা পাতি কথায় হনুমান রামের চাকরে পরিণত। দাসে
পরিণত। যার উদাহরণ ও দুই মহাকাব্যে আর নেই। হ্যাঁ, মহাভারতে ভীষ্ম অর্থদাস, বিদুর শুদ্রগর্ভজাত,
তবুও তাদের সেল্ফ আইডেন্টিটি তারা হারায়নি। রামের ইনফ্লুয়েন্সেও অন্য কেউ রামায়ণে একেবারে
চাকরে পরিণত হয়নি। হনুমান হয়েছে। হয়েছে রামের ক্রীতদাস, হয়েছে ভক্ত ভৃত্য
personified। এমত দাসের উদাহরণ অন্য দ্বিতীয়টি কোন মহাকাব্যেই নেই।
আবার
আরেক আশ্চর্য যে, হনুমান যখন এমত রাবণের ত্রাসে পরিণত হয়েছেন - তাকে অবধ্য অজেয় কৃতান্ত
মনে হচ্ছে -তখনও রাবণের পররাষ্ট্রনীতি বা মিত্র রাষ্ট্রের বর্তমান হালহকিকত বিষয়ে জ্ঞানের
যে চরম অভাব তাতে বিস্মিত হতে হয়। রাবণ এর পূর্বে বালী, সুগ্রীব, জাম্ববান এমনকি
নীল বা কিঞ্চিৎকর দ্বিবিধের নামও শুনেছেন-কিন্তু এমন গতিশক্তিময় ও ইচ্ছাক্রমে দীর্ঘ
আকার ধারণকারী হনুমানের নামই তিনি শোনেননি, এবং এও সন্দেহ হয়, তার মিত্ররাষ্ট্র কিস্কিন্ধ্যায়
যে রাজ্যপাট পরিবর্তিত এবং তার মিত্র বালীর মৃত্যু এবং সুগ্রীব-রাম সন্ধি ও গোটা রাজ্যটি
তার শত্রুতে পরিণত হয়েছে এখবরও যেন জানা নেই রাবণের। অন্তত হনুমান
যেভাবে খবরটি রাবণকে শোনাচ্ছেন। আর ভাবুন, কি থেকে কি তে পরিণত হয়েছেন হনুমান
রামকাজে নেমে। নামই কেউ কখনো শোনা যায়নি থেকে সাগরপার করা লঙ্কায় আগুন লাগানো ব্রহ্মাস্ত্রের অবধ্য বীর! এমন
transformation of self এর দ্বিতীয় কোন উদাহরণও কি পুরাকথা দিতে পারে?
হনুমানকে
রাবণ মৃত্যুদন্ড দিলে বিভীষণ একটি ভালো খেলা খেলেছিলেন যাকে অবশ্য বাচ্চাদের ললিপপ
দিয়ে ভোলানো মনে হতে পারে, কিন্তু হনুমান তখনই চিনে নিয়েছিলেন এই বিভীষণকে। রাবণকে
বিভীষণ বলেছিলেন-“এই বানর বিনষ্ট হইলে তাহাদিগকে(রাম ও বানরসেনা) গিয়া যুদ্ধে উদ্যত
করিয়া দেয় এরূপ আর কাহাকেও দেখি না। এক্ষণে রাক্ষসগণ বীরত্ব প্রদর্শনে উদগ্রীব হইয়া
আছে। আপনি যুদ্ধের ব্যাঘাত দিয়া তাহাদিগকে ক্ষুদ্ধ করিবেন না”। এই ব্যাজস্তুতির
মর্মার্থ ধরে নিয়েছিলেন বলে বিভীষণ যখন রামের কাছে আশ্রয় বা বলা চলে লঙ্কায় সিংহাসনের
লোভে মীরজাফর হয়ে আসেন তখন বিভীষণের পক্ষে কথা বলতে হনুমান দ্বিধা করেননি। একটু বলি
বিষয়টি।
রাক্ষস
বিভীষণ রামের কাছে আশ্রয় নিতে সমুদ্রের উত্তরভাগে এলেন। বিভীষণ বিষয়ক মন্ত্রণায় সকল
বানরযূথপতি এমনকি জাম্ববান ও মৈন্দও বিভীষণকে রাবণের চর, ছিদ্রান্বেষী, মিত্ররূপী শত্রু
ইত্যাদি বললেন- হনুমান যে যুক্তি দিলেন তা এক কথায় চরমতম যুক্তিবিদ্যা ও পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদদের
মতো বুদ্ধিমত্তাময়। তিনি বললেন বিভীষণকে দলে না নিলে সে ছিদ্রান্বেষী কিনা তা কিভাবে
প্রমাণ সম্ভব? আর চর এসে এরকম প্রত্যক্ষ পরিচয়
দিয়ে কথা বলে না। আর বিভীষণ যথার্থ দেশ কালেই এসেছেন। দুরাত্মা ও তার সিংহাসন লাভের
অন্তরায় অভদ্র ব্যাবহারকারী রাবণের বিনাশ ও
মহাত্মা ও শত্রুর শত্রু রামের সঙ্গে মিত্রতার এইই যথার্থ সময়। এবং এখন আগে থেকে
বিভীষণকে পরীক্ষা করতে গেলে যদি তার সৎ উদ্দেশ্য থাকে তবে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন ও ব্যথা
পাবেন। এবং বিভীষণের expression এ কোথাও কোন অসংগতি নেই, আন্তরিকভাব তিনি প্রচ্ছন্ন
করতে চাইলে তা প্রকাশ পেতই। এবং শেষে বললেন, রাম “তোমার যুদ্ধ চেষ্টা, রাবণের বৃথা
বলগর্ব, বালীবধ ও সুগ্রীবের অভিষেক(ঠিক যেমন বিভীষণ চান জ্ঞাতিবধ ও রাজ্য)এই সমস্ত
আলোচনা করিয়া রাজ্যকামনায় বুদ্ধিপূর্বকই এই স্থানে আসিয়াছেন”। মোদ্দা কথা এত নিশ্চিত
যে হনুমান তার কারণ সেই প্রথমবার লঙ্কার রাজপ্রাসাদে রাবণের সঙ্গে সাক্ষাতে বিভীষণের
মন তিনি পড়ে নিয়েছেন।
এখানে
একটা Greatest joke of Ramayan না উল্লেখ করে পারছিনা যে সুগ্রীব তখন বলেছিলেন- যে
ব্যক্তি বিপদ উপস্থিত দেখেও ভ্রাতাকে ত্যাগ করে, সে দোষী হোক বা নির্দোষ, তাকে গ্রহণ
করা উচিত নয়!
রাম
বেশ মজা পেয়েছিলেন একথায়। বলেছিলেন- ভরতের মতো ভাই সবার হয় না আর বিভীষণ তার শরণার্থী।
দোষস্পৃষ্ট হলেও এমনকি শত্রু হলেও শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া সাধুর ধর্ম।
এরপর
হনুমানের লেজে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল ও লঙ্কায় আগুন ধরিয়ে দিলেন হনুমান। ব্যাপারটা অত
সহজও নয়, অত তরল গালগল্পও নয়, টিপ্পনী প্রবাদ প্রবচন টাইপ নিত্যাভ্যাসযুক্ত কথার কথাও
নয়। আমরা আগেই বলেছি- হনুমান কে? না হনুমান Wind God। বায়ু স্বরূপ
এবং আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় যে হনুমান হাতে মশাল নিয়ে লঙ্কায় অগ্নিসংযোগ করছেন না বা
that kinda। হনুমান লেজে খেলিয়ে আগুন ধরাচ্ছেন। লঙ্কা বা অতল সমুদ্রের/Unconscious এর
মধ্যে ভেসে থাকা iceberg/ preconscious রাক্ষস বা
Evil side id এর লঙ্কায় হনুমান consciousness এর harbinger। হনুমান প্রমিথিউসের
মতো মৃত্যুপুরীতে শীতল জমাট তুষারময় কঠিন ধাঁধাঁ unconscious এর যুগান্তকালীন অন্ধকার
devil এর ঘন বনে আগুন নিয়ে, consciousnessকে নিয়ে, সততা ভক্তি দেবত্বকে নিয়ে উপস্থিত
হলেন। হনুমান লঙ্কায় আগুন প্রথম নিয়ে এলেন প্রমিথিউসের মতো তাকে পবিত্র করতে। এবং আগুন
যাতে দাবানলে পরিণত হয় তা হল বায়ুর মাধ্যমে, অক্সিজেনের সংস্পর্শে জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ
দ্বিগুণ! আর হনুমানও তাই বায়ুর প্রতীকে রাবণের রাজসভা থেকে নিমিষে গোটা লঙ্কায় আগুন
ছড়িয়ে দেন বায়ুর মতো দ্রুততায়! এর যদি অন্যকোন উদাহরণ পাওয়া যায় তবে তা অবশ্যই মহাভারতের
খাণ্ডবদহন। সেখানেও আগুন আর জলের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল যাকে অত্যন্ত বিদগ্ধভাবে আলোচনা
করেছেন বুদ্ধদেব বসু। সেখানে অগ্নির অনুরোধে বরুণ অর্জুনকে গান্ডীব ধনু, কপিধ্বজ রথ
ও কৃষ্ণকে সুদর্শণ চক্র gift করেছিলেন। আর
ইন্দ্র তার মেঘ বজ্র সহযোগে চাইছিলেন সেই দাবানলকে নিভিয়ে দিতে। এখানে হনুমান কিন্তু
রাম/ইন্দ্র/পর্জন্যের স্ত্রীকে রক্ষা করে অর্থাৎ ইন্দ্র/রাম এর প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা
দেখিয়ে পবন ও অগ্নির যৌথ সক্ষমতায় শীতল সোনার মতো ক্ষয়হীন ধাতব অচলায়তনকে অর্থাৎ
unconscious এ, যার উপর কখনো চেতনের আলো পড়েনি, যে চিরকালীন অনাবিষ্কৃত অনাঘ্রাত সেই
গহিন সব পাপে ইন্সটিঙ্কটে যৌনাবেগ ও অবদমিত কামে ফেললেন প্রথম চেতনের আলো। লঙ্কা ও
রাবণের যাবতীয় অবদমিত কাম ও কামলালসার উপর প্রথম psychoanalyst এর আলো ফেললেন হনুমান।
পবন ও সূর্য পারসনিফায়েড হনুমান। হনুমান দি কাউন্সিলার।
অনেকেই
যে প্রসঙ্গগুলো আলোচনা করেছেন সেগুলো পুনরুক্তি করে লেখা অনর্থক বাড়াতে ইচ্ছা নেই।
তবে সেগুলো আবার একেবারেই এড়িয়ে গেলে মনে হতে
পারে তা লেখকের চোখ এড়িয়ে গেছে অথবা অদীক্ষিত পাঠক পূর্ণ ধারণা পাবেন না হনুমান চরিতের।
তাই উল্লেখ্য যে হনুমান যখন লঙ্কায় সীতার সন্ধানে প্রাসাদ থেকে প্রাসাদ ঘুরে বেড়াচ্ছেন
তখন রাবণের শয়নকক্ষে অসংলগ্ন ও মদ্যপানোত্তর ঘুমন্ত স্খলিতবাসনা অসংখ্য কামিনীকে দেখে
ভাবলেন, হয়তো তার ধর্মনাশ হচ্ছে। তারপর যা তিনি ভাবলেন তা হল রাজযোগের ভাষ্য। যে হনুমানের
দেখায় এযাবৎ সর্বাপেক্ষা সুন্দরী নারী তারা, তার রাবণের এতগুলি অসঙ্কুচিত ঘুমন্ত স্ত্রীকে
দেখেও কিছুমাত্র চিত্তবিকার হল না। “মনই পাপ-পুণ্যে ইন্দ্রিয়কে প্রবর্তিত করিয়া থাকে”।
এবং যেহেতু তার মন অটল তাই ভোগ্যবস্তু তার
নিরোধ করা ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে মনকে ভোগ্যবস্তুতে সংযুক্ত হতে দেয়নি।
এখানেই হনুমানের জিতেন্দ্রিয়ত্ব আরো একবার প্রমাণিত। এবং হনুমান সিদ্ধান্তে এলেন যে “বৈদেহী যখন নারী তখন তাঁকে নারীর মধ্যেই
খুঁজতে হবে, মৃগের মধ্যে নয়”।
এরপর রাম হনুমান প্রথম সাক্ষাৎ। ঋষ্যমূক পর্বত। সুগ্রীব সেই দিব্যকান্তি
ধনুর্ধরদ্বয়কে দেখে স্বভাবমতো বালীরচর ভেবে ভীত। দূত হনুমান ভিক্ষুরূপ ধারণ করে রামের
আগমন উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন ও ইঙ্গিতে সুগ্রীববার্তা দান করলেন। রাম হনুমানকে দেখে
মুগ্ধ হয়ে সেই প্রথম সাক্ষাতেই লক্ষণকে বলেছিলেন, ঋক যজু ও সামবদে যার প্রবেশ নেই,
তিনি এরূপ বক্তব্য বলতে পারেন না। ইনি ব্যকরণে মহাপণ্ডিত হবেন নিশ্চয়ই, এতবাক্য বললেন,
একটিও অপশব্দ ব্যবহার করলেন না। এবং বক্তব্য বলার সময় মুখের অভিব্যক্তিতেও কোন বিকার
পরিলক্ষিত হল না। তার কথা brief to the point and simple। তার উচ্চারণ
নিখুঁত এবং বক্ষ, কর্ণ, তালু হইতে মধ্যমস্বরে সুস্পষ্ট নিঃসৃত হল। যেখানে যে শব্দ যে
শব্দের আগে বসবে তা সবই তিনি মেপে মেপে প্রয়োগ
করেছেন এবং পূর্ণজ্ঞানসহ প্রয়োগ করেছেন। - তাহলে দেখা যাচ্ছে রাম একেবারেই love at
first sight with হনুমান...! কিন্তু হনুমান, ভক্ত ও ব্রহ্মচর্যের চিরকালীন ভারতীয় আদর্শ
হনুমান কিন্তু ধীরে ধীরে রামদাস হয়েছেন।
আসলে অবতারবাদ তো একটি পলিটিক্স। সেই মান্ধাতার আমলেই রামের পূর্বপুরুষ
“মান্ধাতা” বৌদ্ধসন্ন্যাসীকে হত্যা করেন ধর্মনাশের দোষে! আসলে অবতার যেমন রাম, কৃষ্ণ...
এদের ভক্তরা sexless formless অখন্ডমণ্ডলাকার
ব্রহ্মকে কোন মনুষ্যআধারে প্রভু, সখা অথবা শত্রুরূপে পেতে চায়। তার সঙ্গে গল্প করতে
চায়, তাকে সেবা করতে চায়, তার সঙ্গে চায় অবতারের চরণে নিজের যাবতীয় কাম, প্রেম ও অন্যান্য
যা যা লিবিডোনাল ইন্সটিংক্টচুয়াল ইম্পালস তাকে সমর্পণ করে দিতে। flow off করিয়ে নিজেকে
মুক্ত করে ফুরফুরে করে ভক্তের অখণ্ড আনন্দ আস্বাদন করতে। আর এই প্রসেসে
কোথাও তবে লুকিয়ে থাকে অবতারের প্রতি পুরুষভক্তের-রামের প্রতি হনুমানের, কৃষ্ণের প্রতি
সুদামা বৃহন্নলার প্রতি সমকামী টেন্ডেন্সি। অথবা একে বলা যায় “ সমপ্রেম ”।
এ প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে ‘রামায়ণে সমকামিতা’ নামক লেখায় বলেছি, এখানে তা
পুরোটা বলা সম্ভব নয়, দরকারও নেই, কিন্তু রামের influenceএ রামকে কেন্দ্র করে যে বৃত্ত
তাতে যত ভৃত্য সকলেই কঠোরভাবে ব্রহ্মচারী। শুধু জিতেন্দ্রিয় হনুমানই নন; লক্ষণ, নিজের
রাজ্যে স্ত্রীর সঙ্গেই থাকা ভরত-শত্রুঘ্ন,এমনকি কামুক যে কামুক সুগ্রীব যার বৌদিকামনা
কিস্কিন্ধ্যার রাজ্যপাট উল্টে দিলো সেও তারা রুমা সঙ্গ ত্যাগ করে রামকাজে নিয়োজিত।
যে বানরগণকে রামায়ণে অসংখ্যবার চপলমতি কামুক গুলিবল পেটুক ইত্যাদি বলা হয়েছে সেইসব
সাধারণ বানরেরাও রামের call of duty তে সব ত্যাগ করে ব্রহ্মচারী কৃচ্ছসাধনারত ও কঠোর
পরিশ্রমে যুদ্ধে রত। তাই যাহা রাম হ্যায় উহা কাম নেহি। সীতার সঙ্গে কনজুগাল লাইফে যে
চরম ব্রহ্মচর্যব্রতে নিয়োজিত রাম, সেই principle রাম তার প্রতিটি ভক্তে প্রযোজ্য করেছেন।
যাবতীয় ইন্দ্রিয় কাম ত্যাগ করে, নারীসঙ্গ ত্যাগ করে শুধু রামে নিয়োজিত হবে, তবে রামের
মধ্যেই ভক্ত তার যৌনতাকে fixation করে ফেলবে, নিজের লিবিডো attached করে ফেলবে পুরুষভক্ত
রামে -এবং তবে সে তো সমকামীই প্রতিপন্ন হয় সাধারণ চোখে। আসলে কাকে ভক্তি করছি তা বড়
কথা নয়, ভক্তি এই emotionটাই আসল অবতার। ভক্ত, কেবল ভক্তের আত্মসমর্পণই তাকে তার, একান্তভাবে
তার অবতার বানিয়েছে। রাম অবতার হনুমান ভক্ত বলে তাই। ভক্ত যদি মরে, তবে দূর্গানাম কেউ
লবে না। যেই হও সুপুরুষ হয়ে ভক্তের অবতারপুরুষ হও হে!!
এবং হনুমান কে অসংখ্য লোকরামায়ণে কখনও রামের পুত্র, কখনো ভ্রাতা কখনও বন্ধু
এমত অসংখ্যরূপে পাওয়া যায়। রামের অন্ডকোষ ছিন্ন হয়ে নারী তা ভক্ষণ করে হনুমান জন্মায়
অর্থাৎ হনুমান লিটারালি রামের পুত্র এমত গল্পও শোনা যায় সুকুমার সেনের বয়ানে। তবে হনুমান
রামের আত্মজ অর্থে হনুমান রামের দেহেরই অংশ। প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
হনুমানের ব্রহ্মচর্য আসলে রামের সহিত সমকামে সংযুক্ত তাই তার নারী বা অন্য ভোগ্য লাগে
না এবং সবচেয়ে বড় কথা এই চরম মানসিক শাস্তি বা সমস্যা আসলে ভক্তের মনে আনন্দই উৎপাদন
করে। সে তো সেলফ হিপনোটিক, নিজেই নিজের চেতনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মিথ্যা বিশ্বাস
তার যত কষ্ট পায় মেসোকিস্ট ততই আনন্দ পেতে থাকে, যেহেতু সে কাম নামক পৃথিবীর মুখ্যতম
পাপ থেকে মুক্তি পায় অবতারে কামকে প্রবাহিত করে, তাই তার মনে কোন সংশয় নেই অবদমন নেই,
টারময়েল নেই- তা নিশ্চিত ও শান্ত। এই চরম নিউরোটিক দশাই তবে ভক্তের ভগবান লাভ বলে বর্ণিত
হোক।তবে হনুমান ব্রহ্মচারী ছিলেন কিনা এ প্রশ্ন দীনেশচন্দ্র সেন পড়ার বহু আগেই আমার
মাথায় এসেছে।
রাম অযোধ্যা থেকে তিন যোজন দূরে ভরদ্বাজ আশ্রমে উপবিষ্ট আছেন। সেখান থেকে
তিনি ভরতের মতিগতি বোঝার জন্য (আদৌ ভরত রাজ্য রামকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছুক কিনা) ও রামের
আগমনের সংবাদ ভরতকে জানানোর জন্য হনুমানকে দূত হিসাবে প্রেরণ করলেন। ভরত রামের অযোধ্যায়
come back news শুনে অতিমাত্রায় আনন্দিত হয়ে
হনুমানকে একলক্ষ গো, একশ গ্রাম ও ষোলোটি সালংকারা sexy কন্যা উপহার দিতে চেয়েছিলেন।
তাই প্রশ্ন আসে হনুমানের বিখ্যাত আজন্ম ব্রহ্মচর্য বিষয়ে ... যখন ভরত to be or not
to be হনুমানের সঙ্গে পূর্বপরিচিত। আবার হনুমানের
বীর্যপান করে কুমীরের পেটে জন্ম পাতালপুরীর রক্ষক হনুমানের পুত্র মকরধ্বজ বা অহিরাবণ
মহিরাবণ কাহিনী মূল রামায়ণে নেই। তাহলে শুধু সাধারণ যৌনতাই নয়, হনুমানে পশুকামের কলঙ্কও
এসে লাগে যে!!
আরো কিছু তথ্য শেয়ার করা যাক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী স্টাইলে, যেখানে সবাই
মানুষ আর কি! মিথের মিস্টিকের যাবতীয় fantasy ছাড়িয়ে যুক্তিময় ব্যাখা খুঁজতে। দিতে
হয়, দেখাতে হয় এই অ্যাঙ্গেলগুলো, তাই বাধ্য হয়ে দেওয়া।
যেমন তো প্রথমেই হনুমানের কোন গদা ছিলনা। রামের নির্দেশ ছিল বানররা স্বচিহ্ন
ব্যতীত মনুষ্যমূর্তি ধারণ করবেন না। অস্ত্র সহযোগে যুদ্ধ করবেন রাম, লক্ষণ, বিভীষণ
ও তার চার অমাত্য নিয়ে সাতজন মানুষ। বানররা তাই বৃক্ষ প্রস্তরখন্ড মুষ্টি ও নখরদন্ত
সহযোগেই গোটা রামায়ণে যুদ্ধ করেছেন। কোন বানরই গদা ব্যবহার করেননি। হনুমানও নন। এটা
চালু মিথ মাত্র।
দুই, ইন্দ্রজিতের ভীষণ যুদ্ধে রাম লক্ষণ মুর্চ্ছিত আর বানরসেনা ছিন্নভিন্ন।
বিভীষণ কোনমতে মন্ত্রণাদাতা জাম্ববানকে পেলে জাম্ববান রাম লক্ষণের কুশল জানার বদলে
আগে জানতে চাইলেন পবনপুত্র জীবিত আছেন কিনা। কারণ হনুমান জীবিত থাকলে সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট
হলেও জীবিত আর বিনষ্ট হলে সকলে জীবিত থাকলেও useless। জাম্ববানের
পরামর্শেই হনুমান ওষধি আনতে কৈলাসস্থ ওষধি পর্বতে গেলেন এবং ওষধি চিনতে না পেরে পুরো
পর্বতশৃঙ্গ উৎপাটন করে নিয়ে এলেন। এখন প্রশ্ন পুরো একটা পর্বত তুলে আনা তো সম্ভব নয়!!
হ্যাঁ, তবে একমাথা খড় নিয়ে (পর্বতপ্রমাণ খড়) কোনো চাষীবৌ এর ঘরে ফেরার দৃশ্য দেখা যায়।
সম্ভবত ওষধি গাছগাছড়ার স্তূপ হনুমান চিনতে না পেরে উপড়ে নিয়ে আসেন, যা মহাকাব্যীয় রূপক
হয়ে দাঁড়ায়। নাহলে দুবার প্রয়োজনে একই পর্বত তো আনা সম্ভব নয়!
সংকালিয়ার মতে লঙ্কা বর্তমান শ্রীলঙ্কা নয় এবং হনুমানও লাফিয়ে উড়ে গোটা
সাগর পার করেননি। কারণ যদি ভারতের দক্ষিণভাগ থেকে শ্রীলঙ্কা অবধি সেতু নির্মিত হয়,
তবে বর্তমান অত্যাধুনিক প্রযুক্তির নিরিখেও তা হবে দীর্ঘতম সেতু! এবং অন্যান্য অনেক
তথ্য সন্নিবেশিত করে সংকালিয়া বলতে চেয়েছেন প্রকৃতপক্ষে মহানদীর দুইপাড় ছিল রাম ও রাবণের
লঙ্কার অবস্থান এবং তা মূলতঃ আদিবাসী গোন্ডদের মিথ যা রামায়ণের মূল ক্লু। এর কারণ হিসেবে
তিনি দেখান কোথাও রামের নর্মদা পার হওয়ার কথা নেই বা শালবৃক্ষ যা দিয়ে সেতু নির্মিত
হচ্ছে তা তত পরিমাণে দক্ষিণ ভারতের ওই অংশে জন্মায় না। বা বিভীষণ ক্ষণমধ্যে সমুদ্রের
উত্তরপাড়ে এসে উপস্থিত হলেন লঙ্কাত্যাগ করে রামের আশ্রয়ে যেতে অথবা মারীচ সমুদ্রে গিয়ে
পতিত হল রামনিক্ষিপ্ত বানের প্রভাবে ইত্যাদি। মহানদীর যে স্থানের কথা সংকালিয়া বলছেন
তার একপাড়ে “লক্কা” যেখানে গোন্ডরা রাবণবংশী বা রাবণের পুজো করে আর অপর পাড়ে শবররা
থাকে যারা শবরীর জাতিভুক্ত বা রামভক্ত বলে মনে করা হয়। এবং মহাকাব্যীয় অতিকথনে যা শতযোজন
বিস্তৃত সমুদ্র তা সংকালিয়ার মতে শতহস্ত (যোজনের এক অর্থ নাকি হাতও বোঝায়) এবং হনুমান
তা সাঁতরেই পার হয়েছিলেন। রামায়ণে “লঙ্ঘন” শব্দটি রয়েছে তার থেকেও স্বষ্টতরভাবে আছে
“সন্তরণ” শব্দটি। হনুমান সাঁতরে বা হয়তো নৌকা বেয়েই পার হন সাগরই যদি বা ধরে নেওয়া
হয় সংকালিয়াকে উপেক্ষা করেও। এমনকি শারীরিক প্রতিবন্ধীরাও যখন ইংলিশ চ্যানেল পার হন
তখন হনুমানের সাগরপার মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় হয়তো এইরূপ পায়।
নিশ্চয়াত্মিকা স্থির বুদ্ধি, সর্ববিদ্যা ও বেদজ্ঞান, শাস্ত্র ও ব্যকরণজ্ঞান,
অনন্ত common sense ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ইত্যাদি একবীরের যা যা চারিত্রিক গুণ থাকলে
সে জিতেন্দ্রিয় আজন্ম ব্রহ্মচারী হতে পারে তার সবই হনুমানে- এই চরিত্রে বুদ্ধিজীবি
ও বীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই- দুইই পরিপূরকরূপে হনুমানের চরিত্রে বিদ্যমান। অন্যান্য
বানর যারা হনুমানের মুখে সীতার সংবাদ পেয়েই কিক্সিন্ধ্যার অশোকবন(শোকরহিত বন/disneyland) বা সুরম্য মধুবন
তছনছ করে মধু ফল মদ খেয়ে ফেললো বা এমনকি রাজকুমার অঙ্গদ ও এত অস্থিরমতি যে তিনি সীতার
সংবাদ না পেয়ে বিফল হয়ে ফেরার চেয়ে আত্মহত্যা করা শ্রেয় মনে করছেন অথবা সাগরতীরেই নতুন
বানররাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছেন তখন তার বিপ্রতীপে হনুমান ও তার বুদ্ধিবিদ্যাই তাকে
আলাদা করে দিয়েছে। বাল্মীকি অবশ্য তার হনুমানকে নিয়ে বেশি অলৌকিক বীরত্ব খুব একটা করেননি
কিন্তু কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস কিছুই বাকী রাখেননি। তবুও হনুমান বিদ্বান কূটনীতিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ
সুবক্তা শাস্ত্রজ্ঞ স্থিতপ্রজ্ঞ বুদ্ধিবলেই শ্রেষ্ঠ হয়ে ব্রহ্মচারীভক্ত হিসাবে মনে
যেন প্রতিষ্ঠা পান এই প্রার্থনা করি, তার বল ও অলৌকিক কান্ডকারখানা দিয়ে যেন নন। হনুমানের
কাছে ভক্তি ইন্দ্রিয়জয় ও বিদ্যাবুদ্ধি প্রার্থনা করি, সংকটমোচন অলৌকিক মিরাকেলে মুশকিল
আসান ইচ্ছা করি না। হনুমানকে আদর্শ রেখে একটা জাতি যেন ব্রহ্মচর্য ও ভক্তির ক্ষমতায়
বিশ্বাস রাখে।
আধ্যাত্মিক এক অতি চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যা পাচ্ছি হনুমান চরিতের এবং সমগ্র
রামায়ণ নিয়েই। যদিও প্রতিটি পদক্ষেপ ধরে ধরে রামায়ণকে আধ্যাত্মিক প্রতীকের মোড়কে বর্ণনা
করা বোধহয় ঋষি বাল্মীকিরও উদ্দেশ্য ছিল না কিন্তু কিছুদূর অবধি এগোনো যায়। আর এই বিষয়ে
যেহেতু তাত্ত্বিক জ্ঞান কাজে লাগে না, উপলব্ধি ও wisdom নিজেই নিজের spirituality জানিয়ে
দিয়ে যায় তাই শুধু শোনা ও পড়া ব্যাখ্যাকে উপস্থাপিত করতে পারি মাত্র। তার সত্যাসত্য
বিচার করা লেখকের সাধ্যাতীত।
সন্ন্যাসীর সাধনমার্গে কুলকুণ্ডলিনী সাধনার স্তরে স্তরে রামায়ণের আধ্যাত্মিক
প্রতীকায়নের সন্ধান পাওয়া যায়। দশরথ হলেন দশ ইন্দ্রিয় ও অযোধ্যা হল দেহ / মূলাধার। তাঁর তিন স্ত্রী তিন গুণের প্রতীক। দেহান্তে আত্মা
মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার নিয়ে বেরিয়ে যায়। এরাই হলেন রাম ( মন ), লক্ষণ ( চিত্ত
বা consciousness ), শত্রুঘ্ন ( বুদ্ধি বা intellect ) আর ভরত ( অহংকার বা ego )। মন
আর চিত্ত সবসময় পরস্পর সংযুক্ত । চিত্ত মনের ছায়াস্বরূপ। সীতা আদ্যাশক্তি স্বরূপিনী।
রাবণ হলেন রব= রুলার + অন্য = other. অর্থাৎ এই মুহূর্তে সহস্রদলে অবস্থান করছেন শুভ
শক্তি নন বরং অন্য শক্তি বা অশুভ শক্তি / matter not spirit। এই সহস্রদল বা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আবাস
ত্রিকুটিতে এখন অবস্থিত লঙ্কা, সোনার মায়া লঙ্কা । অসুরদের আক্রমণে দেবতাদের স্বর্গ
রাজ্য হারানো ও বিষ্ণুর শরণাপন্ন হওয়ার মাধ্যমে যে মিথের টেণ্ডেন্সি নিজেকে বার বার
পুনরাবৃত্ত করেছে। হনুমান হলেন হনন + মান = যিনি নিজের ego বা pride কে হত্যা করে হয়েছেন
বিনম্র ও নিরহঙ্কারী। যাইহোক বিস্তারিত আধ্যাত্মিক প্রতীকায়ন অন্য লেখায় আলোচনা করে
আমরা এখানে শুধু হনুমানের আলোচনা করব।
Spiritual journey তে সাধকের পরম প্রয়োজন এই নম্রতা যার মাধ্যমেই সে গুরুকৃপা
লাভ করে তার ইষ্টলাভ করবে। আমিকে বশ করা হনুমানই তাই প্রথম সীতা দর্শন পেয়েছেন। নম্রতা
অহিংসা সব থেকে শক্তিশালী অস্ত্র আমাদের ভারতীয় চিন্তায় দর্শন ও ধর্ম জগতে যদিও তাকে
আপাতভাবে দুর্বল মনে হয়। আত্মসচেতন বিনম্র aspirant তাই সফলতা লাভ করবেই। তিনিই ত্রিকুটি
বা লঙ্কায় প্রবেশের ক্ষমতা রাখেন। হনুমান তার সাগর যাত্রায় প্রথমে সুরসার মুখোমুখি
হন যায় অর্থ সুমিষ্ট রস। আবার নাগমাতাটিকে সুমিষ্ট বিষ ও ভাবা যায়। হনুমান দেহকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র
করে (নিজেকে ছোট ও নম্র রেখে) সেই বাধা অতিক্রম করলেন এবং সৎ শব্দনাদের (সীতা) অভিজ্ঞতা
করলেন (কান থেকে বেরিয়ে এলেন)।
পরবর্তী বাধা সিংহিকা বা অঙ্গারিকা বা ছায়াধরা যিনি আবার রাহুদের জননী।
এই হিংসা, delusion ও বিশ্বাস ঘাতকতার প্রতীক প্রাণীটিকেও হনুমান তার ক্ষুদ্রতাবোধ
দিয়েই ধ্বংস করলেন।
এরপর লঙ্কায় প্রবেশ করে হনুমান রাবণের সাতমহলা প্রাসাদ দেখলেন যা কিনা অনেক
রূপকথাতেও শোনা যায় যার প্রকৃত অর্থ সাত চক্র । সেখানে মন্দোদরীকে (মন = mind + দউ
= two + দরী = split ) দেখে হনুমানের সীতা বলে বোধ হয়েছিল। হনুমানের মন মায়ায় দ্বিধা
বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এমনভাবেই যে তিনি ভাবছিলেন রাবণের স্ত্রীদের এভাবে লুকিয়ে দেখে
তার পাপ হচ্ছে কিনা!! মায়ার ফাঁদে পড়ে হনুমানের মতো জ্ঞানী ব্রহ্মচর্য পরাকাষ্ঠারও
এমন দশা হয়।
হনুমান সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে অশোকবন বা শোক রহিত বন বা redeemer of
sorrows নামক সকল তপস্বীর পরম ঈপ্সিত স্থানে গিয়েই আদ্যাশক্তির দেখা পেলেন। সীতা যে
বৃক্ষটির নীচে বসেছিলেন সেটি শিংশপা বা শিশু গাছ বা সংশয় doubt যা তার মনে এখন সবথেকে
বেশি আর সেই গাছেরই উপর চেপে বসলেন হনুমান। শুধুমাত্র চরমপর্যায়ের আমিত্ব নাশক সাধকই
এই বৃক্ষ জয় করতে পারে। যে যে রাক্ষসীরা সীতার প্রহরায় ছিল তারা সকলেই আধ্যাত্মিক উন্নতির
চরম লক্ষ্যে পৌছোনোর পথে এক এক জন বাধা। শঙ্কাকর্ণা ( rousing suspicions), একজটা
( single minded ) , হরিজটা নামক ক্যাট্স আই যুক্ত নীলবর্ণা রাক্ষসী (
cowardliness ), দুর্মুখী যিনি রাবণকে উস্কেছিলেন শূর্পনখার অপমানের বদলা নিতে তিনি
দুর্গন্ধের প্রতীক। ধান্যমালিনী রাবণের স্ত্রী ( অতিকায়ের জননী ) তিনি অতিভোজনের প্রতীক।
এদের সবাইকে জয় করেই হনুমান বা ভক্তকে রাম কাজে মনোনিবেশ করতে হয়।
ত্রিজটার স্বপ্ন অতিমাত্রায় সাইকোলজিক্যালি ইন্টারেস্টিঙ এক বর্ণনা যেখানে
রাক্ষসী রামকে রাবণের বিরুদ্ধে জিততে দেখছেন। ত্রিজটা বিভীষণের কন্যা ও তিনি বরাবর
সীতাকে বাস্তবিক বিপদ থেকে ও এমনকি মানসিকভাবেও রক্ষা পেতে সাহায্য করেছেন। ত্রিকুটি
বা spiritual principle of triadic movement কে প্রতীকায়িত করেন তিনি। দেহমধ্যে গঙ্গা
যমুনা সরস্বতী স্রোত বা কাল পুরুষ, আদ্যা ও অক্ষর পুরুষ যারা ত্রিকুটিতে এসে মিলিত
হয়েছে ও সেই স্রোত নিম্নে নেমে মায়া ও ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে তৈরি হয় নিরঞ্জন বা ত্রিজটা
। এই তিন সত্ত্ব তম ও রজোগুণের প্রতীকায়ন। ত্রিজটার স্বপ্ন রামের ত্রিকুটি বা লঙ্কা
জয়ের harbinger.
এখানেই সুন্দরকাণ্ড শেষ হয় না , হনুমানের পরীক্ষাও না। অক্ষয়কুমার বা
indestructible prince তার রথে ঘোর নাদ করতে করতে হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন।
এই শব্দ হল কালের সেই নেতিবাচক শব্দ যা বামদিকে শ্রুত হয় ও যার প্রভাবে শুধু আধ্যাত্মিক
উন্নতিই স্তব্ধ হয়ে যায় না বরং সাধককে খেয়ে ফেলে কামনা, রাগ, লোভ ও ডিলিউশান। তাকে
হত্যা করে হনুমান সম্মুখীন হন জাম্বুমালীর ( যিনি চোখ দিয়ে hypnotize করেন ) এবং তার
পাঁচ সেনাপতিকে... বিরুপাক্ষ, যুপাক্ষ, দুর্ধর্ষ, প্রঘাস, ভাসকর্ণ হত্যা করলেন যারা
matter এর পঞ্চ উপাদান। ত্রিকুটিতে তিন শক্তি প্রবাহ কাল, আদ্যা ও অক্ষরপুরুষ আরো দুই
শক্তি মায়া ও ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে matter কে দেহাত্মবোধকে ধ্বংস করলেন।
এরপর মেঘনাদ যিনি নিজেই মেঘ personified কিন্তু নেতিবাচক মেঘ / অনাকাঙ্খিত
মেঘ তার সঙ্গে monsoon wind ও মেঘের প্রতীক হনুমানের লড়াই হল। হনুমান তাই ক্ষণিকের
জন্য হলেও ধরা দিলেন। ব্রহ্মাস্ত্রও তার বিনম্রতার
সামনে অকেজো হয়ে গেল, তার স্থায়ী কোন ক্ষতি করল না। যেটুকু যা মলিনতা হনুমানের মনে
লেগেছিল তা পুড়ে সাধককে আবার স্থিতধী করল লেজের আগুন। এভাবে হনুমানও একবার fire
ordeal দিলেন সীতা ছাড়া রামায়ণে। প্রমাণিত হয়ে গেল তিনিই ভক্তশ্রেষ্ঠ। এমনকি সীতার
কাছ থেকে তিনি রামকে দেখানোর জন্য গহনাও পেলেন যাকেই ভক্তের কৃপালাভ ভেবে নেওয়া যায়
যা থেকে নিরহঙ্কারী dedicated ভক্ত কখনো বঞ্চিত হয় না। বিভীষণ ও সীতার আবাসস্থান ছাড়া
আর সব কিছুই হনুমান পুড়িয়ে দেন। সেই আগুনের আঁচ থেকে যিনি কঠোর ও ভীষণভাবে
discipline, sacrifice ও devotion চর্চা করেন তিনিই নিষ্কৃতি পেতে পারেন।
পরে যেহেতু নিজের মধ্যে অনাহত শব্দ প্রথম শ্রবণ করে সাধক অচৈতন্য হয়ে যায়
তাই প্রতীকায়িত হয়েছে মেঘনাদের অস্ত্রে লক্ষণের সাময়িকভাবে comaএ চলে যাওয়ার মধ্যে।
রাম তার আধ্যাত্মিক যাত্রায় বাধা প্রাপ্ত হয়ে অশান্ত হয়েছেন ও সুষেণ ( সু = good +
সেনা= peace, শান্তি ফিরিয়ে আনেন যিনি) যিনি তারাপিতা তার সাহায্য নিতে হয়েছে রামকে।
আবার জাম্ববানও শক্তিশেলের ক্ষেত্রে হনুমানকে একই নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ এখন ওষধির
জ্ঞান্টি জানা হয়ে গেছে।
সুষেণ হনুমানকে চারটি ওষধি ভোরের আগে হিমালয় থেকে আনতে বলেছিলেন। তারা হল
মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী, সন্ধানী। এই চার ওষধি যে কোন সাধকের পক্ষেই জীবনদায়ী।
তারা চার সাধনার প্রতীক যা ব্যতিরেকে কেউই যোগেশ্বরত্ব লাভ করে ত্রিকুটি জয় করতে পারে
না। ১। সত্য ও unreal এর মধ্যে পৃথগীকরণ করার
ক্ষমতা ( বিবেক = মৃতসঞ্জীবনী ), ২। বহির্জগতের স্টিমুলাসে তাৎক্ষণিক রিঅ্যাকশান দেওয়া
থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার মানসিক উদাসীনতা ( বৈরাগ্য = বিশল্যকরণী ) ৩। মনের নিয়ন্ত্রণ
সম , দেহের নিয়ন্ত্রণ দম, সহনশীলতা, ধৈর্য্য ( তিতিক্ষা ), শ্রদ্ধা, steadfastness
প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ষড় সম্পত্তি ( সুবর্ণকরণী ) ও ৪। মুমুক্ষতা ।
একেবারে শেষে একটা কথা বলে এ লেখা শেষ করবো এবং তা হল অ্যানথ্রোপলজিক্যাল
ভিউপয়েণ্ট। আমরা ভল্লুক গোলাঙ্গুল সহ নৃতত্ত্বের দিক থেকে হয়তো অখন্ড ভারতে যত ধরনের
প্রজাতির মানুষ সম্ভব তার একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাচ্ছি যুদ্ধকান্ডের ২৬তম সর্গে।
গোটা ভারতের ভৌগোলিক বর্ণনাও পেয়ে যাই এই অংশে। যেমন জাম্ববান নর্মদার অংশের রাজা ও
তার জল পান করেন। কারও দেহ শুভ্র, কারও নীল, কারও পিঙ্গল, কারো কালো, কারও চোখ হলুদ
দেহবর্ণ অত্যুজ্জ্বল ইত্যাদি বহু নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ভ্যারাইটি ও গোটা ভারতব্যাপী
তাদের বাসের বর্ণনা পাওয়া যায়। হিমাচল, বিন্ধ্য, কৈলাশ, ধবলগিরি, মন্দর, মহেন্দ্র,
উদয় ও অস্তগিরি, পদ্মাচল, অঞ্জনশৈল, মহাশৈল, সুমেরু পার্শব, ধূম্রাচল, তাপসাশ্রম, মহারুণ
শৈল ইত্যাদি স্থানে বানরদের বসতি ছিল। যেমন
বিন্ধ্যপর্বত থেকে আগত বানরদের রং অঙ্গারবর্ণ, মহারণ শৈল থেকে আগতদের স্বর্ণবর্ণ গাত্ররং।
ভাল্লুক ও গোলাঙ্গুলরা অতিরিক্ত রোমশ বলে তাদের ঋক্ষ বলা হয়েছে। যা থেকে সংকালিয়ার
পুর্ববর্ণিত মত খন্ডন করা যায়। এবং বলা যায় যে যেভাবে রেতু নির্মাণের বর্ণনা বাল্মীকি
ও কৃত্তিবাস দিয়েছেন তাতে মনে হয় যে অগভীর সমুদ্রের উপর কাঠ ও পাথর ফেলেই সেতু বানানো
হয়েছে। উপগ্রহ চিত্রে ভারতের রামেশ্বরম থেকে শ্রীলঙ্কার মান্নার দ্বীপের যোগসূত্র হিসাবে
প্রাকৃতিক রাম-সেতুর স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। অত্যন্ত অগভীর সমুদ্রের মাঝে মাঝে যে
পাহাড় তার প্রমাণ তো হনুমানের সাগর লঙ্ঘনের সময়ই পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমে মৈনাক পাহাড়,
তারপর সুরমা রাক্ষসী যাকেও একটি পাহাড় ধরা যায় । আর সিংহিকার দেহ অভ্যন্তরে ঢুকে বেরিয়ে
আসার মাধ্যমে কি এই ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে সেটিও একটি পাহাড় ও তার মধ্যের গুহাপথ দিয়ে
গিয়ে হনুমান সুবেল গিরিতে উপনীত হচ্ছেন!!
যদিও পণ্ডিতরা প্রক্ষিপ্ততার দোষ দেখতে পারেন কিন্তু এত দেখেও হনুমানের
ইউনিকনেস as a anthropological being উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। প্রথমত মনে হয় হনুমান বানরকুলের
হয়েও যে সম্পূর্ণ আলাদা একটি জীব। যার বাম হনু ভগ্ন বা বিরাট হনু যা মূলতঃ কাঁচামাংসভোজী
ইরেকটাসদের দেখা যেত। হনুমান ইচ্ছামতো দেহ ফোলাতে কমাতে পারেন যেমন বেজি ইত্যাদিরা
করে যেমন আরশোলা দেহ খুবই ছোট করতে পারে অর্থাৎ খুবই ফ্লেক্সিবল বডি হনুমানের যা বহু
মনুষ্যেতর কীট বা প্রাণী করতে পারে। হনুমান পাখিদের মতো উড়তে পারে। আর হনুমানের লেজের
ব্যবহার। হনুমান ছাড়া অন্য কোন বানর বা বা-নর অর্থাৎ মানুষের মতো জীবেরা যাদের প্রকৃতপক্ষে
টোটেম বানর(যেমন চৈনিকদের ড্রাগন বা রেড ইন্ডিয়ানদের ঈগল) তারা লেজের সে অর্থে ব্যবহারই
করেনি। কারণ লেজ তারা কাপড় বা অলংকার হিসাবে বানরকে অনুসরণ করে “ধারণ” করতো। কিন্তু
লেজের ব্যবহার লঙ্কায় আগুন দিতে করেছেন হনুমান এবং আরো অন্যান্য জায়গায় লেজ দিয়ে শত্রুকে
প্রহার করেছেন ইত্যাদি। কিন্তু একমাত্র হনুমানই কেন? অন্য কোন বানর নয় কেন? সব মিলিয়ে তাই অন্য
এক ধারণা দানা বাঁধে যা দিয়ে এই লেখা শুরু হয়েছিল অর্থাৎ রামায়ণে একমাত্র ক্ষেত্রজ
দেবতার সন্তান হনুমানই। হনুমান বানর বলে চিহ্নিত হলেও তিনি এক বিশেষ জীব যাকে সাধারণ
বানরের সংজ্ঞায় ধরা যায় না। হয়তো এক বিরল জীব, হয়তো এক্সট্রাটেরেস্টিয়াল
alien, হয়তো আরো আরো অনেক প্রাচীন, রামকথার থেকেও অনেক প্রাচীন যুগের কোন লুপ্তজীবের
স্মৃতি থেকে মিথে পরিণত চরিত্র যাকে কেন্দ্র করে ও যাকে সন্নিবেশিত করে নিয়ে রচিত হয়েছে
রামায়ণ। আর যাই হোক, এক্সট্রাটেরেস্টিয়ালের কথা শুনে যদি হাসি পায় বা উন্মাদ বলে বোধ
হয় লেখককে তবে উত্তরকাণ্ডে রাবণের দিগ্বিজয়ে বেরনোর এক গল্প উল্লেখ করলাম।
রাবণকে যুদ্ধার্থ একান্ত উৎসাহী দেখে নারদ তাকে নারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে
শ্বেতদ্বীপে যেতে বললেন। সেখানে গেলে সেই দেবদুর্লভ দ্বীপের তেজে পুষ্পকও স্তব্ধ হল।
যেন রেডিয়েশন বেরোচ্ছে এরকম দ্বীপের তেজে সমস্ত রাক্ষস নিরস্ত্র হয়ে সরে পড়ল। সেখানে
অতিবিশালাকায় যুবতীরা রাবণের কোমর ধরে অবলীলায়
তাকে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল-দেখ সখী, আমি কীট ধরিয়াছি!! রাবণকে নিয়ে তারা বেশ একটু লোফালুফি
খেলল। এবার ভাবুন তবে সেইসব মেয়ের দেহের আকার ও শক্তি কি মাত্রায় ছিল! সুতরাং শেষ সিদ্ধান্ত
এই যে হনুমান বানররূপী কিন্তু বানরমাত্র নন, তিনি এক চিররহস্য হয়তো ভবিষ্যতে কোন রেফারেন্স
কোন গবেষণায় কপিবীরের এই অতিকপিত্বের রহস্য উদ্ঘাটন হবে।
জয়বজরংবলী
শেষকথা : পাঠকের হয়তো মনে হবে এ লেখায় ভক্তি, আধ্যাত্মবাদ, কুণ্ডলিনী যোগ
বা অষ্টসিদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে view point অতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। হতে পারেন হনুমান
আধ্যাত্মবাদ নিয়ে ব্যাখা তো হতেই পারেন। তা আমার subject নয়, objectiveও নয়। মূলতঃ
রামায়ণ আয়নায় মুখ দেখার মতো, যার যা mental state ও trait সে রামায়ণে তাই দেখে। এটাই
রামায়ণের সবচেয়ে বড় মাহাত্ম্য, সবচেয়ে আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য। আর আমার কাছে রামায়ণ নিজে
বড় নয়, আমার দর্শন দৃষ্টিভঙ্গী রাজনীতি মনস্তত্ত্ব বাস্তবকে প্রকাশ করার অস্ত্র হল
রামায়ণ। আমার দেশের মানুষের যৌথ অবচেতনে নিহিত রামায়ণের মাধ্যমে নিজের বক্তব্য প্রকাশ
করায় হল আমার লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই আমার এই এ হনুমানগাথা যা সাবেক হনুমানচালিশা
কি তলসীদাসের ধার ধারে না কারণ লেখক নিজে তাদের বিষয়ে least interested। কোন কিছুর প্রতিই
দায় নেই লেখকের, নিজের প্রতি সততার অঙ্গীকার ছাড়া। কোন এক্সপেক্টেশানও নেই। just
time pass।
সূত্রঃ A study on the Ramayana- Amal Sarkar
- বাল্মীকি
রামায়ণ- হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুদিত
- India
in the Ramayana Age -S.N. Vyas
- রামায়ণের
উৎস কৃষি- জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- Carl
Jung – Archetypes and collective unconscious সহ ইয়ুঙ সাহিত্য
- রামকথার
প্রাককথন- সুকুমার সেন
- রামায়ণী
কথা- দীনেশচন্দ্র সেন
- বাল্মীকির
রাম ও রামায়ণ- নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি
- মহাভারতের
কথা- বুদ্ধদেব বসু
- Ramayan
: A myth or reality?- Sankalia
- বাল্মীকি
রামায়ণের স্থান-কালক্রম ও সমাজ- পার্শবনাথ রায়চৌধুরী
- Symbolism
in Ramayan and Mahabharat
- অমিতাভ
প্রহরাজের সঙ্গে কথোপকথন