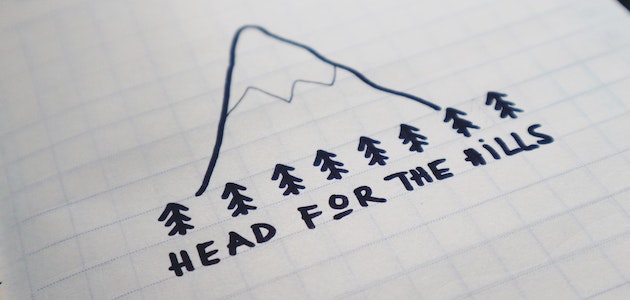ঔপনিবেশিক কলকাতায় শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারে বাংলার বিদ্বৎসমাজের
অবদান
ভূমিকা:
“আজব
শহর কলকাতা।
রাঁড়ি
বাড়ি জুড়ি গাড়ি
মিছে
কথার কি কেতা।
হেতা
ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে
বলিহারী
ঐক্যতা”।
(‘হুতোম
প্যাঁচার নকশা’, কালীপ্রসন্ন সিংহ)
প্রায়
পাঁচশ বর্গমাইল বিস্তৃত ‘আজব শহর কলকাতা’র ইতিহাস তিনশো বছরের।
একদিন যা ছিল অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের
রাজধানী সময়ের প্রবাহমানতায় তা পরিণত হল পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী তথা পূর্বাঞ্চলের
প্রাণকেন্দ্রতে। এই শহরের ধারাবাহিক ইতিহাস, তার পত্তন এবং
তিলোত্তমা নগরীতে রূপান্তরিত হওয়া ইত্যাদি ঘটনাকে নিয়ে; নানা মতভেদ থাকলেও নগর
কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নানা ধরণের সাহিত্যসম্ভার।
কেবলমাত্র বাংলা ভাষা বা গদ্যকেন্দ্রিক সাহিত্যসৃজন নয়, ইংরেজী ও পদ্যকেন্দ্রিক
বিভিন্ন রচনা রয়েছে এই শহরকে নিয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে
পাশ্চাত্য শিক্ষা অনুসৃত তথাকথিত নবজাগরণ ঘটলেও; বাঙালির চিন্তা-চেতনার প্রসারে
তথা কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল তৎকালীন সময়ে গড়ে
ওঠা বিভিন্ন সভা-সমিতিগুলি।
আলোচ্য
ক্ষেত্রে ‘গবেষণা প্রবন্ধ প্রস্তুতি’র জন্য রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুর প্রণীত “কলিকাতার ইতিহাস”
নির্বাচন করা হল। উক্ত গ্রন্থ
অবলম্বনে ঔপনিবেশিক কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে বাংলার বিদ্বৎসমাজের ভূমিকা
সম্বন্ধে আলোচনা করা হল। গবেষণার
সুবিধার্থে সমগ্র বিষয়টিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হল।
প্রথম অধ্যায়ে, ঔপনিবেশিক পরিবেশ এবং নগর কলকাতার
পত্তন কেন্দ্রিক একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।
দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঘটে পাশ্চাত্য
শিক্ষা অনুসৃত বঙ্গীয় নবজাগরণ ও তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
তৃতীয় অধ্যায়ে, নবজাগরণের আলোকপ্রাপ্ত কলকাতার
বিদ্যাচর্চার প্রসার ও প্রচার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।
চতুর্থ অধ্যায়ে, ঔপনিবেশিক সময়ে কলকাতার সাংস্কৃতিক ও
সামাজিক পরিবর্তনে তৎকালীন সময়ে স্থাপিত সভা-সমিতিগুলির অবদান নিয়ে আলোচনা করা
হয়েছে।
গ্রন্থের
সংক্ষিপ্ত পরিচয়
বঙ্গীয়-সাহিত্য
পরিষদের অন্যতম প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুর প্রণীত “The
Early History and Growth of Calcutta (1905)’’ অবলম্বনে; ইংরেজী ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত লেখক, ইংরেজী
ফ্রেজ ইডিয়ম অভিধানের সংকলক, সরল বাংলা অভিধান প্রণেতা ও সাহিত্য সংহিতা পত্রিকার
সম্পাদক শ্রী সুবলচন্দ্র মিত্র কর্তৃক বাংলা ভাষায় ‘কলিকাতার ইতিহাস
(১৯৮৭)’ নামে সংকলিত হয়। উক্ত
গ্রন্থে জায়মান কলকাতা শহরের জনজীবনের ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। নগর কলকাতার পত্তন থেকে শুরু করে
অন্ততঃ সত্তর বছর পূর্বের এক বিস্তৃত পরিচায়ক এই গ্রন্থ। শহরের উৎপত্তি, ইংরেজের আগমন,
ভূ-বৃত্তান্ত, শিক্ষার প্রসার, জনবসতির শুরু, বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠান,
ব্যবসা-বাণিজ্য, শহরের বিচার ও শাসন ব্যবস্থা, ছাপাখানা এবং সংবাদপত্র, ইউরোপীয় ও
হিন্দু সমাজ প্রভৃতি প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।
চাবিশব্দ;
শিক্ষা, সংস্কৃতি, নবজাগরণ, পরিবেশ, কলকাতা,
সাহিত্য, বিদ্যাচর্চা, সভা, সমাজ
প্রথম অধ্যায়
ঔপনিবেশিক পরিবেশ ও নগর কলকাতার পত্তন
কলকাতা
কলকাতাই। গঙ্গার তীরে গড়ে ওঠা অন্যতম জনবহুল এই জনপদের ইতিহাস
তিনশো বছরের। জন্মলগ্নের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজনীতি,
অর্থনীতি, সমাজনীতির টানাপোড়েনে কলকাতার রূপবদল ঘটেছে।ব্রিটিশ
ভারতের রাজধানী হিসেবে সারা দেশে এই শহরের ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। জীবন
ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছিল এখানে। শহর এগিয়ে চলেছিল নতুন সত্যের সন্ধানে।
এমন কোনো মানুষ ছিল না এই শহরে যারা সেদিনের সাংস্কৃতিক ভাঙা-গড়ার পালায় অংশগ্রহণ
করেনি। বহু মানুষের ত্যাগ ও শ্রমের বিনিময়ে জন্ম এই শহরের। “এই শহর-সৃষ্টি ইংরেজের নয়--তারা
প্রভুত্ব করেছিল ঠিকই; কিন্তু শহরের পত্তনে রাজমিস্ত্রীর ভূমিকা ছিল বাঙালীর”।১
১৬০০
খ্রিষ্টাব্দে ভারত ও পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের একদল বণিক ইস্ট
ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে, যা ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে পর্দাপণ করে। ১৬৯০
সালের ২৪ শে অগাস্ট ব্রিটিশ কেরানী জব চার্ণক ভাগীরথীর তীরে তাদের প্রধান
বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে কলকাতার মহানগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন।
১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে মোগল রাজদরবারে প্রাপ্ত ফরমানের মাধ্যমে ভারতে ইংরেজদের
একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারিত হয়। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী
লাভের পর বাংলার শাসনকার্য সাক্ষাৎভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে আসে। অষ্টাদশ
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে
আমূল পরিবর্তন ঘটে। মধ্যযুগীয়
শাসনপ্রথা ও সমাজবিন্যাসের ধারা পরিবর্তিত হয়ে ১৭৫৭ সালে পূর্বভারতের শাসনদণ্ড
নবাবের হাত থেকে স্খলিত হয়ে গ্রেট ব্রিটেনের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে এসে পড়ল।
পলাশীর যুদ্ধের দশ বছরের মধ্যে “বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিলো রাজদণ্ড
রূপে’’। ঔপনিবেশিক ভারতের প্রাণকেন্দ্র রূপে আত্মপ্রকাশ করলো
নগর কলকাতা। বর্তমান সময়ে কলকাতা শহরের স্বরূপ তাকে একটি
ঐশ্বর্যশালিনী মহানগরী হিসেবে প্রতিভাত করলেও, কলকাতা সুদৃঢ় মাটির ওপর গড়ে ওঠে নি। তৎকালীন
সময়ের জনৈক লেখকের লেখনী থেকে জানা যায় যে, ইংরেজ আমলের বহু পূর্বে কলকাতা ছিল
নদীয়া জেলার সামান্য একটি জল-অধ্যুষিত জঙ্গলময় পল্লীগ্রাম।২ সেখানে কেবল
বেশ কয়েক ঘর মৎস্যজীবী ও কৃষিজীবী মানুষ বসবাস করত।
১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উস-শানের কাছ থেকে তিনখানি
গ্রাম কেনার অনুমতি পায়। বিনয়কৃষ্ণ
দেবের মতে, “১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইহা যখন জমিদারীরূপে ক্রীত হয়,
তৎকালে ইহার পরিমাণ ফল ১১/২ বর্গ মাইল মাত্র ছিল। কলিকাতা
সে সময়ে একটি বাণিজ্যিক উপনিবেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।”৩ “সুতানুটি,
গোবিন্দপুর ও কলকাতা—ভাগীরথী নদীর পূর্ব পাড়োস্থিত এই তিনটি গ্রামের আয়তন ছিল
উত্তর-দক্ষিণে প্রায় তিন মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় এক মাইল। বর্তমানের চিৎপুর,
বাগবাজার, শোভাবাজার ও হাটখোলা ছিল সুতানুটি নামে পরিচিত; ধর্মতলা, বউবাজার,
মির্জাপুর, সিমলা অঞ্চল জুড়ে ছিল গোবিন্দপুর গ্রাম”।৪
দ্বিতীয় অধ্যায়
বঙ্গীয় নবজাগরণ ও তার প্রভাব
ঊনবিংশ
শতাব্দী বাঙালির চিত্তজাগরণ তথা আত্মজাগরণ এবং আত্মপ্রত্যয়ের যুগ। মূলত এই সময়কে বলা যায় ইকোরাস আর
প্রমিথিউসের আলোর মিছিলে উজ্জ্বল এক চিত্তপ্রকর্ষের যুগ। এই শতাব্দীর সূচনালগ্নে ঔপনিবেশিক ভারত তথা
কলকাতার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে মৌলিক
পরিবর্তন সূচিত হয়। বাংলায়
পাশ্চাত্য শিক্ষা অনুসৃত এই পরিবর্তনই বঙ্গীয় নবজাগরণ নামে পরিচিত। যার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছিল
সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক নানা ধারার কর্মকান্ডের মধ্যে।
উনিশ
শতক বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে আধুনিকতার আগমনের সূচক-কাল। আধুনিকতা দৈবনির্ভরতা মুক্ত,
অন্ধসংস্কার মুক্ত এক নতুন যুগচিহ্ন প্রতিনিধিত্ব করছিল তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্যে। আধুনিকতার স্তম্ভ হিসেবে মানবতাবাদ,
যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বদেশপ্রেম, নারীপ্রগতি প্রভৃতি বিষয়গুলি
প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
ফলে বাংলায় নবজাগরণের স্বরূপ নিরূপণে তৎকালীন সাহিত্য ও সমাজে তার প্রভাব আলোচনা
বাঞ্ছনীয়।
সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভাব
পূর্বভারতে
শাসনকার্য নির্বাহের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্মচারীদের দেশীয় বাংলা ভাষায়
শিক্ষিত করার জন্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে কলকাতায় ‘কলেজ অফ ফোর্ট উইলিয়াম’
স্থাপিত হয়। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে উক্ত কলেজে বাংলা
বিভাগ খোলা হয়। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা পড়াতে গিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ
উইলিয়াম কেরি বাংলা গদ্য গ্রন্থের অভাব বুঝে, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ
বাচস্পতি প্রমুখ সংস্কৃত পন্ডিতদের পাঠ্যপুস্তক রচনায় উদ্বুদ্ধ করেন। যার ফলস্বরূপ বাংলা ভাষায়
আধুনিকতার সূত্রপাত স্বরূপ পাঠ্যপুস্তকের আবির্ভাব ঘটল।
কিন্তু
ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা গদ্যের সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন রাজা
রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ )। ‘এই প্রচণ্ড
প্রতিভাবান কর্মী মনীষী ছিলেন ভারতবর্ষে আধুনিকতার অগ্রদূত।
ধর্মসংস্কার সমাজসংস্কার শিক্ষাবিস্তার রাজনৈতিক-আন্দোলন—সর্বত্রই রামমোহনের
নেতৃত্বে বাঙ্গালা দেশ তথা ভারতবর্ষকে নবদেশের প্রেরণায় চঞ্চল করিয়াছিল।
...রামমোহনের রচনায় সাহিত্যরস ছিল না, তবে তাঁহার ভাষা ছিল বক্তব্যের উপযোগী এবং
প্রাঞ্জল’। ‘বেদান্ত গ্রন্থ’(১৮১৫), ‘বেদান্ত সার’(১৮১৫) প্রভৃতি তাঁর
উল্লেখ্যযোগ্য রচনা।
সমাজজীবনে প্রভাব
এছাড়া
ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঠ্যপুস্তক এবং ব্যক্তিগত রচনাবৃত্তের বাইরে আধুনিকতার
ফসলস্বরূপ বাংলায় সংবাদপত্রের প্রচলন ঘটে । ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে
শ্রীরামপুর মিশনের মিশনারীবর্গ কর্তৃক ‘দিগ্দর্শন’(মাসিক পত্রিকা, ১৮১৮খ্রিঃ
এপ্রিল মাস) এবং ‘সমাচার-দর্পণ’( সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১৮১৮খ্রিঃ, মে মাস ) পত্রিকা
দুটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে
বাঙালিদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা। তার
মধ্যে রামমোহন রায়ের ‘সম্বাদ কৌমুদী’( ১৮২১ ডিসেম্বর মাস ), ভবানীচরণ
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সমাচার-চন্দ্রিকা’(১৮২২ খ্রিঃ), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
‘তত্ত্ববোধিনী’ ( ১৮৪৩ খ্রিঃ ) ইত্যাদি পত্রিকাগুলি উল্লেখযোগ্য।
বঙ্গীয়
নবজাগরণ যেমন তৎকালীন সমাজে বহু ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছিল, ঠিক তেমনই বাংলার
সমাজ-জীবনে তার কিছু নেতিবাচক প্রভাবও বিস্তৃত হয়েছিল। নবচেতনার উন্মেষের বিপরীতে সমাজে
বাবুসমাজের উৎপত্তি ঘটে। ইংরেজ শাসকদের মোসাহেবী করে এই জনজাতির দিন
অতিবাহিত হলেও, সাজসজ্জা ও স্বল্প ইংরেজীশিক্ষা-বলে বাবুরা বিশৃঙ্খল জীবনযাপন করতো। যার পরিচয় তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের
‘নকশা’ গ্রন্থ রচনায় প্রতিফলিত হয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কলিকাতা
কমলালয়’(১৮২৩), ‘নববাবুবিলাস’(১৮২৫),
‘নববিবিবিলাস’(১৮৩১), প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’(১২৬৪) এবং
কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’(১২৬৬) ইত্যাদি সমাদৃত বাবু-আখ্যান।
তৃতীয় অধ্যায়
নগর কলকাতায় বিদ্যাচর্চার অভ্যুদয়
ইংরেজ সাহেবগোষ্ঠীর মাধ্যমে নগর কলকাতায়
বিদ্যাচর্চার অভ্যুত্থান ঘটলেও তা ছিল ইংরেজ সিভিলিয়ানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত
পাঠ্যপুস্তকগুলির মূল্য অত্যাধিক হওয়ায় দেশীয় বিদ্যার্থীদের বিদ্যাচর্চায় প্রতিকূল
অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই
সমস্যার নিরূপণের উদ্দেশ্যে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে রাধাকান্ত দেব, রামকমল
সেন, তারিণীচরণ মিত্র এবং উইলিয়াম কেরী প্রমুখের উদ্যোগে ‘কলিকাতা স্কুল বুক
সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭
খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারী দেশীয় ছাত্রদের জন্য রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার
প্রমুখের উদ্যোগে কলকাতায় ‘হিন্দু কলেজ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। যার মাধ্যমে ইংরেজী ভাষা সহ বিজ্ঞানের নানান
বিষয়ে জ্ঞানোহরণের পথ প্রশস্ত হয়।
এরপর ডেভিড হেয়ার ‘হেয়ার স্কুল’ (১৮১৮
খ্রিষ্টাব্দ), রামমোহন রায় পটলডাঙায় ‘অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল’(১৮২২ খ্রিস্টাব্দ )
এবং জগৎমোহন বসু ভবানীপুরে ‘ইউনিয়ন স্কুল’ বিদ্যায়তন স্থাপন করেন। এইসব প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী শিক্ষার পাশাপাশি নীতি
ও ধর্মশিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হতো। সময়ের কালপ্রবাহের ধারায় গৌরমোহন আঢ্যের ‘ওরিয়েন্টাল সেমিনারি( ১৮২৯),
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা’(১৮৪০) ও ‘হিন্দুহিতার্থী
বিদ্যালয়’(১৮৪৫) স্থাপিত হয়। হিন্দু কলেজের পরে খ্রিষ্টান মিশনারীদের
উদ্যোগে ‘শ্রীরামপুর কলেজ’ (১৮১৮), ‘বিশপ্স কলেজ’ (১৮২০), সরকার পরিচালিত
‘সংস্কৃত কলেজ’ (১৮২৪) ও ‘কলকাতা মাদ্রাসা’ (১৮২৯) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের পর সরকারী বা বেসরকারী ভাবে
স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায় বিপুল সাড়া পড়ে যায়। যার প্রভাব নগর কলকাতার পাশাপাশি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। সমগ্র বাংলায় বিদ্যাচর্চার প্রসারণ ঘটলেও তা
কেবলমাত্র পুরুষদের মধ্যে সীমায়িত থাকায় পরবর্তী সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র
বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনের কাজ শুরু হলেও জন ওয়াটারড্রিঙ্ক
বেথুনের পৌরহিত্যে তৎকালীন নারীসমাজ শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়। এই বিষয়ে সমকালে বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি
হলেও বিদ্যাসাগর, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার,
তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখের উদ্যোগে
বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের
প্রসার ঘটে।
চতুর্থ অধ্যায়
ঔপনিবেশিক সময়ে কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিবর্তন
ইংরেজ
অধ্যুষিত সময়কালে তথাকথিত নবজাগরণের ফলে নগর কলকাতার পুর্ননবীকরণ ও উন্নয়নের
পাশাপাশি তার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। যার অনিবার্য ফলশ্রুতিরূপে গড়ে ওঠে
নানা সভা-সমিতি।
ভাব-সংগঠনের জন্য ইংরেজদের বণিক-সভা ও সাহিত্য-সভা প্রভৃতি বহু পূর্বেই স্থাপিত
হয়; তৎকালীন সমাজের পদস্থ কিছু ব্যক্তি তার সভ্য হন। ‘রুস্তমজী কাওয়াসজী ও দ্বারকানাথ ঠাকুর ‘বেঙ্গল
চেম্বার অব্ কমার্সে’র সদস্য ছিলেন।’ এশিয়াটিক সোসাইটি ( ১৮২৯ পর্যন্ত ভারতীয়দের
স্থান দেয়নি ), কেরির ‘Agricultural and Horticultural Society’ প্রভৃতি সাংস্কৃতিক সমিতির কথাও অবিস্মরণীয়।
‘আত্মীয় সভা’
রামমোহন
রায় প্রতিষ্ঠিত ‘আত্মীয় সভা’ (১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ) বাঙালির সংগঠিত প্রথম সভা। এখানে আলোচিত বিষয়ের মধ্যে ছিল
মূর্তি পূজার অসারতা, বর্ণপ্রথা, সতীদাহ প্রথা ও বহুবিবাহের কুফল এবং বিধবাবিবাহ
সংক্রান্ত বিষয়সমূহ। এই
সভা পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সভার সঙ্গে যুক্ত হয়ে
ব্রাহ্ম সভা হিসেবে নামাঙ্কিত হয়। ব্রাহ্ম
সভায় মূলত নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা বিষয়ে আলোচনা হলেও সমকালীন সমাজ-সমস্যাগুলিও
এখানে আলোচিত হতো।
‘কলিকাতা স্ত্রী-যুব-সমিতি(The Calcutta Female
Juvenile Society)’
১৮১৯ সালে কলিকাতা স্ত্রী-যুব-সমিতি
স্থাপিত হয়। বাংলায় স্ত্রী-বিদ্যালয়ের সাহায্যের উদ্দেশ্যে এই সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতি প্রথমে ৩২টি ছাত্রী নিয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে। পড়াশুনার
পাশাপাশি সূচিকর্ম, কারুশিল্প বিষয়ে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। ১৮২২ সালে এই সমিতি বঙ্গীয় খ্রিস্টান স্কুল
সোসাইটির সঙ্গে মিলিত হয়। মিসেস
উইলসন কলিকাতা স্ত্রী-যুব-সমিতির অন্যতম সভ্য ছিলেন।
‘গৌড়ীয় সমাজ’
১৮২৩
খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ কলকাতায় দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন
প্রমুখের উদ্যোগে গৌড়ীয় সমাজ স্থাপিত হয়। বিদ্যাচর্চা
ও বিদ্যানুশীলনের মধ্য দিয়ে তৎকালের প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলি আলোচনার মাধ্যমে একটি
নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ—এই সমাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া শাস্ত্রবিষয়ক বিভিন্ন বিষয়
আলোচনা এবং নীতিগত বিরোধের জায়গাগুলি সুচিহ্নিতকরণের দ্বারা সমাধানের ক্ষেত্রে
গৌড়ীয় সমাজের ভূমিকা অনবদ্য। রামকমল সেন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন এই সভার
সম্পাদক।
১৮২৭ সালে এই সভার সভ্য তারাচাঁদ চক্রবর্তীর উদ্যোগে গৌড়ীয় সমাজ থেকে বাংলা-ইংরেজি
অভিধান প্রকাশিত হয়।
‘অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন’
১৮২৮
খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের অন্যতম শিক্ষানবীশ লুই হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিওর
অনুপ্রেরণায় অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীন চিন্তা, যুক্তিবাদ,
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, আনুগত্য ও সংস্কার বর্জন এবং
স্বদেশীকতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা হতো। এই সভা উনিশ শতকে কলকাতার বিদ্যা ও
সংস্কৃতি চর্চার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কৃষ্ণমোহন
বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার,
রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব প্রমুখ এই সভার সদস্য ছিলেন।
‘সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা’
মহর্ষি
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে এবং তাঁর সম্পাদনায় ১৮৩২ সালে সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা
স্থাপিত হয়। বাংলার
নবজাগরণের অগ্রদূত রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায় এই সভার সভাপতি ছিলেন। বাংলাভাষা চর্চা, বিদ্যাচর্চা এবং
বিজ্ঞান বিষয়ক নানা বিষয়ে এখানে আলোচিত হতো; যা সেই সময়ের জ্ঞানপিপাসু মানুষের মনে
সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।
‘সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা’
১৮৩৮
খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর মৃত্যুর পর, তাঁর অনুপ্রেরণায় গঠিত
অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ভেঙে গিয়ে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা গঠিত হয়। ডিরোজিও প্রোথিত ইডিওলজির তাড়নায়
রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী
প্রমুখের উদ্যোগে এই সভা স্থাপিত হয়।
ঔপনিবেশিক
ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার সূচনা হয় এই সভায়। এছাড়া তৎকালীন ভারতবর্ষের শিল্প,
শিক্ষা, সমাজ, বাণিজ্য এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা হতো। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে এই
সভার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সমকালীন
সমাজ-সমস্যা থেকে শুরু করে যুব সমাজের জাগরণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরির
প্রচেষ্ঠায় সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার ভূমিকা অনবদ্য।
‘তত্ত্ববোধিনী সভা’
উনিশ
শতকের নব্য কলকাতায় জ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহযোগিতায় স্বীয় পৈতৃকভবনে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন
করেন ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে।
১৮৪৩
খ্রিষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে সভার মুখপত্র হিসেবে তত্ত্ববোধিনী
পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
যার ফলে জায়মান বাংলা গদ্যের এবং সাহিত্যের ইতিহাসে নবযুগের অরুণোদয় সূচিত হয়। অক্ষয় কুমার দত্ত ছিলেন
‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ ও ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র সম্পাদক।
সূচনালগ্নে
ব্রাহ্মধর্মের অনুকূল সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা ও আত্মতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা হলেও; অক্ষয় কুমার দত্তের প্রচেষ্ঠায়
এই সভা কেবলমাত্র তত্ত্ববিদ্যা আলোচনায় পর্যবসিত না থেকে বিজ্ঞান, দর্শন,
পুরাতত্ত্ব, গণিত ও সাহিত্য প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনার প্রকৃষ্ট বাহন হয়ে
উঠলো।
সভায় আলোচিত প্রতিটি বিষয় সবিস্তারে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত
হতো। অক্ষয়কুমারের
নীতিগর্ভ এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞানোদ্দীপক প্রবন্ধগুলি এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত
হয়।
‘বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ (Vernacular
Translation Society)’
১৮৫১
সালে ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে ‘স্কুল বুক সোসাইটি’র
সহযোগী হিসেবে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের
উদ্যোগে বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ গঠিত হয়।
এই সভার আনুকূল্যে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট পন্ডিত মনস্বী ও বাগ্মী রাজেন্দ্রলাল
মিত্রের ‘বিবিধার্থসংগ্রহ’ প্রকাশিত হয়। তাঁর সাধারণ ব্যবহার্য বস্তুর নির্মাণ বিষয়ক
গ্রন্থ ‘শিল্পিক দর্শন’ ও (১৮৬০) এই সভা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৫২ সালে বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজের
‘আদেশে’ হরচন্দ্র দও কৃত ‘শ্রীযুৎ মেকালি সাহেব কর্তৃক রচিত’ “Life
of Lord Clive” গ্রন্থের অনুবাদ ‘লর্ড ক্লাইভ’ প্রকাশিত হয়।
পরবর্তী
সময়ে বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজের সঙ্গে যুক্ত হন রেভারেন্ট জেমস লঙ, ঈশ্বরচন্দ্র
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র সহ অন্যান্য বিদ্যোসাহী
ব্যক্তিগণ। ১৮৫৩
সালে এই সভার উদ্যোগে “মহাকবি সেক্ষপীর প্রণীত নাটকের মর্ম্মানূরূপ লেম্বস্টলের
কতিপয় আখ্যায়িকা ডাক্তার এড্বার্ড রোয়ার সাহেব কর্তৃক অনুবাদিত হইয়া”৫
প্রকাশিত হয়। এতে-“ঝড়বৃত্তান্ত,
নিদাঘ নিশীত স্বপ্ন বিবরণ, শিশির সমাজ রহস্য(Winter’s Tale), অকারণ গোলোযোগ, তোমাদের যথেচ্ছা, বেনিস নগরীয় বণিক্, লিয়র রাজা, মেক্বেথ
ও হেমলেট”৬—এই নয়টি কাহিনি অনুবাদিত হয়েছিল। জায়মান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঊষালগ্নে
বাংলাভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র হিসেবে বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজের
ভূমিকা অনস্বীকার্য।
‘কলিকাতা বেথুন সোসাইটি’
নবজাগরণের আলোকপ্রাপ্ত কলকাতায় নারীশিক্ষার
প্রচার ও প্রসারে যে কয়েকজন ব্যক্তি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, জন
ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনায় অনুরাগ বৃদ্ধি এবং ইউরোপীয় ও দেশীয়
ব্যক্তিদের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন বিষয়ক সংযোগ স্থাপন, নারীশিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের
উদ্দেশ্যে কলিকাতা বেথুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাস্টিস ফিয়ার, কর্ণেল ম্যালিসন, পাদরি কে এম
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষ এবং বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এই
সভার সদস্য ছিলেন।
প্রায় চল্লিশ বছর টিঁকে থাকা সভায় তৎকালীন
বাংলার কৃষি সংক্রান্ত সমস্যা, ভূমিবণ্টন ব্যবস্থা, স্থাপত্যবিদ্যা, বিদ্যুৎশক্তি,
নারীনিগ্রহের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করা ছাড়াও চিনজাতির
ইতিহাস, ভারতীয় ও ইউরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসের তুল্যমূল্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হতো। ১৮৫৩ সালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
তাঁর ‘সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য’ বিষয় প্রবন্ধটি প্রথম কলিকাতা বেথুন সোসাইটিতে পাঠ
করেন। এরপর ১৮৮১ সালে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘গান ও ভাব’ প্রবন্ধটি এই সভায় পাঠ করেন। তৎকালীন বঙ্গসমাজে নারীনিগ্রহের প্রতি
অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে কলিকাতা বেথুন সোসাইটির কার্যক্রম অনবদ্য। এছাড়া নারীশিক্ষার প্রসার এবং বিভিন্ন
প্রাসঙ্গিক বিষয় আলাপ-আলোচনার কেন্দ্র হিসেবে এই সমিতির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।
‘বামাবোধিনী সভা’
১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে বামাবোধিনি সভা উমেশচন্দ্র
দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বমী,
হেমন্তকুমার ঘোষ প্রমুখের পৃষ্টপোষকতায়
সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে (১২৭০ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে) এই সভার মুখপত্র স্বরূপ
‘বামাবোধিনী’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সভায় মূলত ভ্রমণ বৃত্তান্ত, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, চিত্রকলা, বিজ্ঞান
বিশ্লেষণ, বিদেশী নারীর সাফল্যর কাহিনি, শিক্ষা প্রসঙ্গ, স্বাস্থ্য জ্ঞান,
শিশুপালন পদ্ধতি, ধর্ম বিষয়ক আলোচনা ও গাহর্স্থ্য প্রসঙ্গ আলোচিত হত। যা নিয়মিতভাবে সভার মুখপত্রে প্রকাশিত হত। তবে বামাবোধিনী সভায় আলোচিত প্রধান বিষয় ছিল
তিনটি নারীশিক্ষার প্রচার, প্রসার ও সার্থকতা, শিশুপালন সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং
পরিবারের প্রতি রমণীদের কর্তব্য ও সেখানে তাদের স্থান ইত্যাদি প্রসঙ্গ।
‘বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা (The Bengali
Social Science Association)’
১৮৬৭
খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ট জেমস লঙের অনুরোধে মেরি কারপেন্টারের উদ্যোগে বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।
জাস্টিস ফিয়ার ও বেডার্লি, নবাব আব্দুল
লতিফ খাঁ বাহাদুর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এই সভার সদস্য ছিলেন।
তৎকালীন
সময়ে পাশ্চাত্য রীতি অনুসারী বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞান বিষয়ক নানা প্রসঙ্গ এই সভায়
আলোচিত হতো। সমকালীন
বিদ্যোৎসাহীদের একত্রীভূত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়া আইন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও
বাণিজ্য বিষয়ে বহু হিতকর বক্তৃতা এই সভায় আলোচিত হতো। সমকালীন মানুষের জীবনযাত্রা তথা
সাংস্কৃতিক বোধের উদ্রেক ঘটানোর প্রয়াসে বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভার ভূমিকা অগ্রগণ্য।
‘ভারতীয় বিজ্ঞান সভা (The Indian
Association for the Cultivation of Science)’
১৮৭৬ সালে
বউবাজার স্ট্রীটে সভা ভারতীয় বিজ্ঞান
সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায়। এর স্থাপন কাল অব্দি প্রত্যেক রাজপ্রতিনিধি এর
পেট্রন ছিলেন এবং বঙ্গের শাসন কর্তারা ও অন্যান্য প্রধান-প্রধান রাজপুরুষ সকলেই এই
সভার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও অনুরাগ প্রদর্শন করেছিলেন।
‘শোভাবাজার হিতৈষী সভা(The
Sovabazar Benevolent Society)’
১৮৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব
বাহাদুর এই সভার পেট্রন ও পোষণকর্তা ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র রাজা বিনয় কৃষ্ণ
দেব বাহাদুর ইহার প্রতিষ্ঠাতা। জাতিধর্ম নির্বিশেষে দরিদ্র ছাত্র অসহায় বিধবা ও অনাথ আতুরদের অভাবমোচন
করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।
‘মুসলমান-সাহিত্য সমিতি (The
Mahammedan Litery Socitey)’
১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার
উদ্দেশ্য ছিল সর্বশ্রেণীর জনগনের মধ্যে, বিশেষত মুসলমান সমাজে, সামাজিক ভাব ও
সাহিত্য বিষয়ে অনুরাগ উদ্দীপিত করা। পরলোকগত নবাব আবদুল লতিফ খাঁ এই
সমিতির প্রাণস্বরূপ ছিলেন। বস্তুত
নবাব বাহাদুর ভারতবাসী সকল সম্প্রদায়ের একজন নেতা বলে বিবেচিত হতেন। সকল সমাজে এই সভার প্রতিষ্ঠালাভ কেবল আবদুল
লতিফ বাহাদুরের যত্নের ফল তাতে কোন সন্দেহ নেই।
উপসংহার
নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটি পল্লীগ্রাম থেকে
ব্রিটিশ ভারতের প্রাণকেন্দ্রে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে তিলোত্তমা কলকাতার রদবদল
ঘটছে বারংবার। আনুষাঙ্গিকভাবেই
পরিবর্তিত হয়েছে তার আর্থ-সামাজিক পরিমন্ডল থেকে শুরু করে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক
পরিবেশ। ইংরেজ আগমনের ফলে
ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে পরিণত হলেও, নগর কলকাতার পত্তন এবং বঙ্গীয়
নবজাগরণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ফলত উনিশ শতকের নব জাগরিত নাগরিক সমাজের
পরিশোধনের ক্ষেত্রে দেশীয় ব্যক্তিবর্গ প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেলেও, পরোক্ষভাবে
সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা। উনিশ শতকীয় কলকাতায় স্থাপিত
সভা-সমিতিগুলি এরই স্বপক্ষ ধারণ করে। মধ্যযুগীয় সময় পর্যন্ত বাংলায় যে
চরম অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল, এই সময়ের সভা-সমিতি সেই অরাজকতা সেই নৈরাজ্যের
বিরুদ্ধে মানুষের চেতনার জগতকে জারিত করেছিল। সর্বোপরি দেশীয় মানুষ স্বাদেশীকতা বোধে উদ্বুদ্ধ
করা থেকে শুরু করে নারী শিক্ষার প্রচার-প্রসার এবং বিদ্যাচর্চা ইত্যাদি ক্ষেত্রে
গণজাগরণকারী মাধ্যম হিসেবে সর্বজনীনতা লাভ করেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর সভা-সমিতিগুলি। তাই নগর কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে আলোচনার
ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলির অবদান অনস্বীকার্য।
তথ্যসূত্র:
বিনয় কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, ‘কলিকাতার ইতিহাস’, দ্র. ‘ভূমিকা’, জে এন চক্রবর্তী এন্ড কোং, কলকাতা,
পৃ ৫
তদেব, দ্র. ‘কলিকাতার প্রাচীন বিবরণ’, পৃ ৪৫
তদেব, পৃ ৪৬
সুকুমার
সেন, ‘বাংলা সাহিত্যে গদ্য’, দ্র. ‘প্রথম পরিচ্ছেদ’,
আনন্দ পাবলির্শাস, কলকাতা, পৃ ৫৯
তদেব,
পৃ ৬০
গ্রন্থপঞ্জী
সহায়ক
গ্রন্থ:
গোপাল
হালদার, ‘বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা’ (২য় খন্ড), বঙ্গাব্দ ১৪০১, প্রথম প্রকাশ, অরূণা
প্রকাশনী, কলকাতা
বিনয়
ঘোষ, ‘বাংলার বিদ্বৎসমাজ’, ডিসেম্বর ২০০৬, প্রকাশ ভবন, কলকাতা
শিবনাথ
শাস্ত্রী, ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’, ২০১৬, চতুর্থ মুদ্রণ, নিউ এজ
পাবলির্শাস, কলকাতা
স্বপন
বসু, ‘বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস’, অগাস্ট ২০১৬, ষষ্ঠ সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা
সহায়ক
ওয়েবসাইট
www.bn.banglapedia.org/index.php?title=কলকাতা
www.bondhu.in/2018/09/blog-post.html?m=1
www.bn.banglapedia.org/index.php?title=বঙ্গীয় রেনেসাঁ