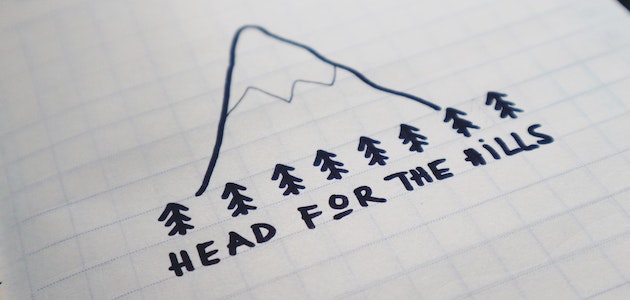বড় পর্দায় হিন্দী ছবি: (১৩শ পর্ব) অতি-প্রাকৃত বিষয় নিয়ে ছবি
১১শ পর্বের ও মাই গড ২-তে অতি-প্রাকৃত ব্যাপার ছিল। মহাদেবের প্রতিভূরূপে হরিদ্বারে
ভক্তের সংকটমোচনে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর এক অনুচর, শিবগণ। এই পর্বে সরাসরি ভৌতিক বিষয়
নিয়ে ছবির কথা থাকবে।
২০২২ সালের ভেড়িয়া (নেকড়ে)

পাশ্চাত্যের werewolf-কে এনে ফেলেছে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের
অরুণাচল প্রদেশে। মুনাফাবাজ এবং প্রকৃতিকে ধ্বংস করে তথাকথিত ‘উন্নয়নে’র প্রবক্তা ববনজিৎ
বাগ্গার (সৌরভ শুক্লা) হুকুমে পাকা রাস্তা তৈরির ঠিকেদার ভাস্কর (বরুণ ধাওয়ান) আর তার
জ্ঞাতিভাই জনার্দন (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) অরুণাচলের জিরোতে উপস্থিত হয় জঙ্গলের মাঝখান
দিয়ে রাস্তা করার প্রস্তাব নিয়ে। স্থানীয় বয়ঃজ্যেষ্ঠরা এর তীব্র প্রতিরোধ করলে ভাস্কর
তরুণ প্রজন্মের সমর্থন আদায় করে, জঙ্গলের জায়গায় নেটফ্লিক্স, শপিং মল আর আকাশের তারার
পরিবর্তে স্টারবাকস-এর লোভ দেখিয়ে। স্থানীয় জোমিন (পালিন কাবাক) ভাস্করের পক্ষে হলেও,
আপাত-বহিরাগত কিন্তু পরিবেশ-সচেতন পাণ্ডা (দীপক দোবরিয়াল) ভাস্কর-জনার্দনকে সাবধান
করে এই বলে যে অরণ্যে আছে ‘বিষাণু’। যে অরণ্যধ্বংসের প্রয়াস করবে, বিষাণুর দংশনে সে
পরিণত হবে ‘যাপুম’ বা মানুষ-নেকড়েয়। সেদিনই রাতে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাবার সময় ঘটে দুর্ঘটনা
আর ভাস্করের নিতম্বে কামড় বসায় এক নেকড়ে। আহত ভাস্করকে জোমিন নিয়ে যায় স্থানীয় পশু-চিকিৎসালয়ে
(নেকড়ে আক্রমণের কথা জানাজানি হলে রাস্তা-প্রকল্প আটকে যাবে) যেখানে অনিকা-নাম্নী পশুদের
ডাক্তার (কৃতি সানন) ভাস্করের ক্ষতস্থানে ইনজেকশন দেয়। পরদিন অপ্রত্যাশিতভাবে ভাস্কর
সেরে ওঠে, তার ক্ষত হয় অদৃশ্য। কিন্তু সে এও বোধ করে যে তার শ্রবণশক্তি অস্বাভাবিকভাবে
বৃদ্ধি পেয়েছে, আর ঘ্রাণশক্তিও; শুধু মৃত পশুর গন্ধ তার কাছে লাগছে ফুলের সুবাসের মতো!
এরপর প্রকাশ পাজা (দোসাম বেয়ং), যার ওপর ভাস্কর
দায়িত্ব দিয়েছিল স্থানীয়দের জমি বেচার দলিলে টিপসই সংগ্রহ করতে, রাতে নেকড়ে-দ্বারা
আক্রান্ত হয়। পরদিন জোমিন আর জনার্দনের সামনে ভাস্কর করে রক্ত-বমি। তার অজান্তে তার
বিষ্ঠা সংগ্রহ করে উক্ত দুজন (স্ক্যাটোলজিকাল কমেডির এক দমফাটা দৃশ্য), আর তা পরীক্ষা
করলে পাওয়া যায় মানুষের দেহাংশ, নখ ইত্যাদি। বিষাণু তার কাজ শুরু করে দিয়েছে!
এরপর আমরা ভাস্করের পূর্ণিমা রাতে মানুষ থেকে নেকড়ে
রূপান্তরিত হওয়া চাক্ষুষ করব।
স্থানীয় ওঝা (মদাং পাই) পাণ্ডে-মারফৎ ভাস্কর-জনার্দন-জোমিনকে
জানায় যে ভাস্কর তখনই শাপমুক্ত হবে যখন নিজের নিতম্বে সে দ্বিতীয়বার যে নেকড়ে তাকে
আক্রমণ করেছিল তার কামড় দ্বিতীয়বার খাবে। সেই নিরাময় হবার মুহূর্তে, যে নেকড়ে ভাস্করকে
কামড়েছিল তার ওপর গুলিবর্ষণ করে আসাম থেকে প্রশাসন-কর্তৃক আনয়ন করা শিকারীর দল। আহত
নেকড়ের পিছু নিয়ে ভাস্কর আবিষ্কার করে যে সেটিও মানুষ-নেকড়েঃ গত একশো বছর ধরে সে অরণ্যের
রক্ষা করে আসছে। তার মনুষ্যরূপঃ অনিকা!
এরপর নেকড়েরূপী অনিকা পুলিশের হাতে বন্দী হলে ভাস্কর
নেকড়েরূপ ধারণ করে তাকে মুক্ত করে, কিন্তু পালিয়ে যাবার পর নেকড়ে-ভাস্করের সামনেই আহত
নেকড়ে-অনিকা পাহাড় থেকে খাদে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।
অনুতপ্ত ভাস্কর এবার সিদ্ধান্ত নেয় যে রাস্তা হবে
জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নয়, জঙ্গলের সীমানা বরাবর, যাতে অরণ্যবিনাশ না হয়। খবরে এও জানা
যায় যে ববনজিৎ বাগ্গা এক রহস্যময় বন্য পশুর উদরস্থ হয়েছেন!
ছবি শেষ হয় জনার্দন ভাস্করকে ঘরে শেকল দিয়ে বেঁধে
রেখে তাকে কাঁচা মাংস খাওয়াবার দৃশ্য দিয়ে।
ছবিতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, অরণ্যবিনাশ রোধ ছাড়াও
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষেরা বাকি দেশে যেভাবে ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং জাতিগত স্টিরিওটাইপিং-এর
সম্মুখীন হন (তাঁদের চীনে মনে করা, ধরে নেওয়া তাঁরা সবাই কুং ফু জানেন), এবং তার সঙ্গে
যে কোন অন্য ধরণের মানুষ, যেমন আপাত-বোকা জনার্দন, যেভাবে আক্রান্ত হয়, তার অত্যন্ত
সংবেদনশীল সমালোচনা রাখা হয়েছে।
সবদিক দিয়ে অত্যন্ত উপভোগ্য ‘কমেডি-হরর’।
ভুল ভুলাইয়াঁ - ৩ (২০২৪)
১৮২৪ সাল। বঙ্গভূমির রাজ্য রক্তঘাট। গভীর রাতে নৃত্যরতা
এক অবগুণ্ঠিতা নারীমূর্তি। হঠাৎ সেখানে সদলবলে আবির্ভাব রাজার। ক্রুদ্ধভাবে তিনি চপেটাঘাত
করলেন ঐ নারীকে। তারপর তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে জীবন্ত দাহ করা হলো। এরপর রাজার শয়নগৃহে
অতর্কিতে দেখা দিল এক প্রেতাত্মা। তার হাতে বধ হলেন রাজা, তাঁর গৃহ গ্রাস করল আগুন
– ঠিক যেমনভাবে তা গ্রাস করেছিল নর্তকীকে।
বর্তমান কাল। কলকাতায় ভূত তাড়াবার নাম করে ব্যবসা
করে রুহান (কার্তিক আরিয়ান) নামে এক যুবক। এই ভণ্ড ওঝাকে কাজে লাগায় রক্তঘাট রাজপরিবারের
মামা (রাজেশ শর্মা) ও তাঁর ভাগ্নী মীরা (তৃপ্তি ডিমরি) । রক্তঘাট রাজপ্রাসাদ থেকে রুহানকে
দিয়ে রাজকন্যা মঞ্জুলিকার ভূতকে তাড়াবার ভান করে ঐ পরিবার প্রাসাদটি চড়া দামে বিক্রী
করবে। বিক্রীর দামের ভাগ রুহান পাবে।
মঞ্জুলিকা ছিল রাজবংশের জ্যেষ্ঠা সন্তান। কিন্তু
পরে দেবেন্দ্রনাথ নামে পুত্র জন্মাতে রাজা পুত্রকেই নিজের উত্তরাধিকারী করেন। অসূয়াতাড়িত
মঞ্জুলিকা ভাইকে হত্যা করলে রাজা নাকি নিজের মেয়েকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার নিদান দেন।
মঞ্জুলিকার প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেতাত্মা রাজার প্রাণ নিলে, রাজপুরোহিত তাকে একটি কক্ষে
বন্দী করে কক্ষের দরজায় মন্ত্রপূত তালা লাগিয়ে দেন। চেহারায় রুহান দেবেন্দ্রনাথের মতো,
অতএব তাকে দেবেন্দ্রনাথের পুনর্জন্ম নেওয়া সত্তা বলে প্রচার করা হয়।
ইতিমধ্যে রুহান আরেকটি রুদ্ধ কক্ষের সন্ধান পায়,
এবং নিজে ভণ্ড ওঝা হওয়ার সুবাদে ভূতে অবিশ্বাসী বলে সেই দরজা খুলে ফেলে, এবং প্রাসাদে
আরেক প্রেতাত্মার আবির্ভাব ঘটায়।
বর্তমান রাজপুরোহিত জানান যে রাজার এক নয়, দুই কন্যা
ছিলঃ অঞ্জুলিকা ও মঞ্জুলিকা। দুজনেরই সিংহাসনের ওপর লোভ ছিল!
মীরা প্রাসাদের সংস্কারের জন্য একটি সংস্থা থেকে
কাউকে পাঠাতে বললে এসে উপস্থিত হয় ‘মল্লিকা’-নাম্নী (বিদ্যা বালন) একজন। যেসব দর্শকেরা
প্রথম ভুল ভুলাইয়াঁ দেখেছেন, তাঁরা তৎক্ষণাৎ
সন্দেহ করবেন যে মল্লিকা আসলে মঞ্জুলিকা (প্রথম ছবিতে মজুলিকার আত্মা বিদ্যা বালন অভিনীত
চরিত্রের ওপরেই ভর করেছিল) । আবার প্রাসাদের ক্রেতারূপে আগত হন মন্দিরা (মাধুরী দীক্ষিত)
নামধারিনী এক ‘রাণী’! দর্শক অনুমান করবেন যে মন্দিরা আসলে দ্বিতীয় কন্যা অঞ্জুলিকার
অতিপ্রাকৃত সত্তা।
নানান বিচিত্র ও চমকপ্রদ ঘটনাসমূহের পর শীর্ষবিন্দুতে
দেখা দেয় দেবেন্দ্রনাথের প্রেতাত্মা। সেইই ছিল দ্বিতীয় কক্ষে আবদ্ধ ভূত! অতীতে তার
দুই ঈর্ষাকাতর দিদি একদিন ভাইকে দেখে মেয়েদের মতো গয়না আর পোশাক পরতে। দেবেন্দ্র তাদের
বলে যে সে আসলে এক রূপান্তরকামী নারী! সেইই রাতে প্রাসাদে নেচে বেড়ায়। তার রাজত্বের
কোন লোভ নেই, সে শুধু নিজের মতো করে বাঁচতে চায়। আর সে তার দুই দিদির কাছ থেকে পূর্ণ
সহমর্মিতার প্রত্যাশী – তারা যে মেয়ে! আর কে তাকে তাদের চেয়ে ভালো বুঝবে?
দুই ক্ষমতালোভী দিদি এবার সহানুভূতির ভান করে। অঞ্জুলিকা
গান ধরে – প্রথম ভুল ভুলাইয়াঁ থেকে আহরিত
‘আমি যে তোমার’ – যার তালে তালে নাচ ধরে দেবেন্দ্র, আর মঞ্জুলিকা বীরদর্পে রাজাকে গিয়ে
বলে, “যে পুরুষ সন্তানের জন্য আমাদের রাজত্ব থেকে বঞ্চিত করেছো, এসে দেখে যাও সে কেমন
পুরুষ!”
অতএব, ছবির শুরুতে আমরা নৃত্যরত দেখেছি দেবেন্দ্রকে।
রাজা তাকেই জীবন্ত দগ্ধে মারার নিদান দিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রের রূপান্তরকামিতা সর্বসমক্ষে
রাষ্ট্র করার অপরাধে দুই বোনের জোটে নির্বাসনের শাস্তি।তবে প্রজাদের জানানো হয় যে রাজত্বের
লোভে দেবেন্দ্রকে হত্যা করেছে মঞ্জুলিকা। আর রাজাকে হত্যা করে পুরোহিতদের দ্বারা দ্বিতীয়
কক্ষে অবরুদ্ধ হয় মঞ্জুলিকা নয়, দেবেন্দ্র। তারই আত্মাকে রুহান মুক্ত করেছে। অতীতের
রাজপুরোহিত আরেকটি কক্ষের দরজায় মিথ্যা মন্ত্রপূত তালা লাগিয়ে সেখানে মঞ্জুলিকার ভূত
আবদ্ধ আছে এমন গল্প ফাঁদেন যাতে দেবেন্দ্রের আত্মার ঘরের দিকে কেউ নজর না দেয়।
দেবেন্দ্র চায় পুরো পরিবারের বিনাশ। কিন্তু দুই
অনুতপ্ত দিদি নিজেদের সহমর্মিতার অভাব স্বীকার করে ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চাওয়াতে দেবেন্দ্র
হিংসার পথ ত্যাগ করে মোক্ষলাভ করে।
লক্ষ্যণীয়, ছবিটির শেষাংশে কিভাবে একাধিক গতানুগতিক
চিন্তাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো হয়েছে। রাজা পুত্রলাভ করা মাত্র পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতায়
কন্যাদের সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করেন। নিরপরাধ ভাইয়ের প্রতি দুই নারীবাদী ভগ্নী চরম বিদ্বেষ
পোষণ করে, এই কথা জানার পরেও যে সেই ভাই রাজত্ব চায় না। তারা তাদের ‘ট্রান্সফোবিক’
বাবার হাতে ভাইয়ের মৃত্যু সুনিশ্চিত করে। নারীবাদীদের রূপান্তর-বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত।
ভাগ্যের পরিহাস এখানেই যে তাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হলেও, তাদের ভাই রূপান্তরকামী, এই কথা
জাহির করার অপরাধে তাদেরও জোটে নির্বাসনের শাস্তি। রক্তঘাট হয়ে পড়ে শাসকহীন!
আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যে ‘প্রিভিলেজ’ বা বিশেষাধিকার
নিয়ে নারীবাদীরা সরব, এই ছবিতে দেখা গেল যে, রূপান্তরকামী হওয়ার ‘অপরাধে’, সবচেয়ে বিশেষাধিকার-বঞ্চিত
কিন্তু কোন জন্মগত নারী নয়, একজন যে জন্মগত হিসেবে পুরুষ কিন্তু নিজের শরীরে নিজেই
বন্দী এক নারী।
রাজপুরোহিতের কথায়, বংশ অভিশাপমুক্ত হলো পুনর্জন্মের
মাধ্যমেই, তবে সে দেবেন্দ্রের রুহান হওয়া দিয়ে নয়, প্রথমত মঞ্জুলিকা মল্লিকারূপে আর
অঞ্জুলিকা মন্দিরারূপে পুনর্জন্ম নেওয়াতে; দ্বিতীয়ত, দেবেন্দ্রের আত্মা মল্লিকা আর
মন্দিরা, দুজনকেই, নিজেদের ‘মঞ্জুলিকা’ বলে জাহির করানোর ফলে। চরম পরিণতি এলো প্রতিহিংসার
মাধ্যমে নয়, ব্যতিক্রমী এক মানুষ, যে জীবিতাবস্থায় ছিল নিজের শরীরে বন্দী আর মৃতাবস্থায়
এক মন্ত্রপূত কক্ষে আবদ্ধ, তাকে সহানুভূতির সঙ্গে বোঝার মাধ্যমে।
মল্লিকা এ জন্মে বিভিন্ন প্রাচীন প্রাসাদ সংস্কারের
সংস্থায় কাজ নিয়েছিল যাতে, বারবার রক্তঘাটের রাজবাড়ীর যে স্বপ্ন সে দেখত, তার খোঁজ
সে পায়। আর মন্দিরা আসলে পুলিশকর্মী এ সি পি রাঠোর, যিনি ভণ্ড ওঝা রুহানকে ধরার ব্যাপারে
সচেষ্ট ছিলেন! এ কথা রাঠোর সর্বসমক্ষে জানানো মাত্র রুহান অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়!
একাধিক পর্বে ভিন্ন যৌনতার আলোচনা করা হয়েছে। ভুল ভুলাইয়াঁ ৩ হলো চণ্ডীগড় করে আশিকী-র সমপর্যায়ের।
সবশেষে পরিচালক শ্রীরাম রাঘবনের উক্তি বাংলায় তর্জমা
করবঃ ‘ভুল ভুলাইয়াঁ ৩-এ কার্তিক আরিয়ানের
রূপান্তরকামী অবতারই ছবির সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা! দুঃখিত মাধুরী, বিদ্যা ও তৃপ্তি!’
স্ত্রী - ২ - সরকাটে কী আতঙ্ক (২০২৫)
সপ্তম পর্বে যা এই ছবি সম্বন্ধে লিখেছিলাম তা অবশ্য
বেশী প্রযোজ্য স্ত্রী নামে ২০১৮ সালের ছবিটির
ক্ষেত্রে। আপনাদের সুবিধের জন্য সে কথাগুলি আবার দিলামঃ
শহরের প্রেতাত্মা বেছে বেছে পুরুষদেরই
অপহরণ করে তাদের ওপর শারীরিক, মানসিক, এবং আধ্যাত্মিক নির্যাতন চালায়, এবং সেটাই এই
‘কমেডি’-র হাস্যরসের মূল উৎস। আবার বলি, লিঙ্গটা পাল্টে দিন; মজা পাবেন তো? হ্যাঁ,
অনেক নারী এবং নারীবাদীরা মজা পাবেন, বলবেন, যুগ যুগ ধরে চলে আসা নারী নির্যাতনের এইই
তো সঠিক উত্তর!
নারীবিদ্বেষের প্রত্যুত্তর যদি পুরুষবিদ্বেষ মনে
করা হয় হয় – misandry as the response to misogyny – তবেই এই ছবিগুলি ভালো লাগতে পারে।
স্ত্রী ২-তে আবির্ভূত হচ্ছে পুরুষ স্কন্ধকাটা
যে হলো শহরের এককালীন সর্দার চন্দ্রভানের (সুনীল কুমার) আত্মা। সেইই স্ত্রী আর তার
প্রেমিককে হত্যা করেছিল আর তার আত্মা ‘প্রগতিশীল’ মেয়েদেরই বেছে বেছে অপহরণ করে। তার
উৎপাতের প্রেক্ষিতে শহরের মহিলাদের বলতে শোনা যায়, “এতদিন স্ত্রীর কল্যাণে পুরুষগুলোকে
বেশ তাঁবে রাখা যাচ্ছিল, এই নতুন ভূতটা এসে সব গোলমাল করে দিচ্ছে!” চন্দ্রভানের বংশধর
চন্দ্রবংশীর ভূমিকায় দেখা গেছে অক্ষয় কুমারকে, আর ভেড়িয়া থেকে ভাস্কররূপী বরুণ ধাওয়ানকেও স্কন্ধকাটার সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখা
যাবে।
ছবির মূল বক্তব্যঃ এককালে হয়ে আসা নারী-নির্যাতনের
প্রতিকার পুরুষ-নির্যাতন এবং তাতে বাধা যে দেবে সেইই ছবির খলনায়ক। অতএব এই ছবি নিয়ে
আর বাক্যব্যয় করতে চাই না।
কোহরা (১৯৬৪)
সবাই বলবেন যে তিনটি আলোচিত ছবিই তো ‘কমেডি-হরর’!
নির্ভেজাল ভয়ের কোন হিন্দী ছবিই কি দেখিনি? উত্তরঃ হ্যাঁ, দেখেছিলাম, সেই আশির দশকের
গোড়ায়, এবং এই ধারাবাহিকের প্রথম পর্বেই সে ছবি আলোচিত হয়েছিল। এককালে অত্যন্ত ভালো
লাগা ছবি যার ভাবমূর্তি বন্ধুপ্রতীম ছাত্র অভিরূপ মাশ্চরকের নির্মম বিশ্লেষণের আঘাতে
অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে! আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য সেই আলোচনাও আবার দিলামঃ
১৯৬৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত আরেকটি ছবি দেখব সুদূর
ভবিষ্যতে, ১৯৮২ থেকে ১৯৮৪-র মধ্যে, যখন আমি যতীন দাস পার্ক লাগোয়া শ্যামাপ্রসাদ কলেজে
অধ্যাপনারতঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত ও সুরারোপিত সাদা-কালো ছবি কোহরা।
এর উৎস-কাহিনী ড্যাফনে ডু মোরিয়ারের ১৯৩৮-এ প্রকাশিত রেবেকা উপন্যাস, এবং তার থেকে ১৯৪০ সালে হওয়া হিচককের বিখ্যাত ছবিটি। ১৯৬২-তে
বীস সাল বাদ হিট করতে, পরের ছবিতে পরিচালক
বীরেন নাগ খানিকটা বাহুল্যবর্জনের পথে হাঁটলেন। কোহরা-র আবহ অনেক বেশী অবিমিশ্রভাবে রোমাঞ্চকর। এখানেও আগের ছবির মতো সেই
নারীকণ্ঠে ভীতিজনক গান, শিল্পী অবশ্যই লতাঃ ‘ঝুম ঝুম ঢলতি রাত’। ছবির শুরুর দিকে গানটি
গাইছে নায়কের প্রথমা স্ত্রী পুণম (থেলমা দেবী), যার মুখ আমরা সারা ছবিতে একবারও দেখতে
পাবো না, শুধু চোখ দুটির ওপর ক্যামেরা মাঝে-মাঝে zoom in করবে! আর পুণম কিন্তু বাকি
ছবিতে বাংলাজিঘাংসা-র মঞ্জুশ্রী (১৯৫১)
বা হিন্দীবীস সাল বাদ-এর রাধার (১৯৬২) মতো
নকল ভূত নয়! পুণমের পূর্বসূরি হলো ১৯৫৮ সালের
মধুমতী ছবির নায়িকা (বৈজয়ন্তীমালা), যে
ছিল আসল প্রেতাত্মা। তবে, মধুমতীর প্রেত ফিরে এসেছিল তার হত্যাকারী উগ্রনারায়ণকে (প্রাণ)
তার অপরাধ স্বীকার করাতে। পুণমের ভূত তাড়া করে ফিরেছে নায়ক অমিত সিং-এর (বিশ্বজিৎ)
দ্বিতীয় স্ত্রী রাজেশ্বরীকে (ওয়াহিদা রেহমান)। মধুমতীর ভূত, প্রাসাদের যে আলসে থেকে
উগ্রনারায়ণের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মধুমতী আত্মহত্যা করেছিল (জিঘাংসা মনে পড়ে?), সেখান থেকেই প্রেমিক আনন্দকে
(দিলীপকুমার) লাফিয়ে পড়তে বলে। ভূত পুণমও মানুষ সতীন রাজেশ্বরীকে দ্বিতীয় বার ‘ঝুম
ঝুম ঢলতি রাত’ গেয়ে অমিতের প্রাসাদের ছাদে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে লাফিয়ে পড়তে বলে। শেষ
মুহূর্তে অমিত রাজেশ্বরীকে বাঁচায়। বলতে দ্বিধা নেই, এই দ্বিতীয়বার গাওয়া গানটির রেকর্ড
বাড়ীতে শুনে সেই ৭/৮ বছর বয়সে বেশ ভয় পেতাম! তুলনায় এর আগের (আপাত-)ভৌতিক গানগুলি
(মহল, মধুমতী, বীস সাল বাদ) অতটা
ভীতির উদ্রেক করে না।
কোহরা-র সম্পদ রাজেশ্বরীর
ভূমিকায় ওয়াহিদা রেহমানের আর দাই-মা’র ভূমিকায় ললিতা পাওয়ারের অভিনয়, আর সবার ওপরে
হেমন্তর সুরে একের পর এক গান। হেমন্তর প্রথম প্রযোজনা নীল আকাশের নীচে-র (১৯৫৯) গান ‘ও নদীরে’ এখানে প্রায় অপরিবর্তিতভাবে লতাকণ্ঠে
শোনা গেছে ‘ও বেকারার দিল’ গানে। তবে, উৎস বাংলা গানটিতে তো নদীর প্রতি এক ধরণের উদাস
ভালোবাসার অভিব্যক্তিই ছিল। কোহরা-য় নায়িকার
মনে জমে থাকা দুঃখ, হতাশা হঠাৎ প্রেমের ছোঁয়ায় যেভাবে অভিমান-ভরা উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়েছে,
হেমন্তর সুর আর লতার গায়কীতে তা মনকে মুগ্ধ করে দেয়। এক টুকরো আগুন (১৯৬৩) ছবিতে হেমন্তর সুরে উৎপলা সেন গেয়েছিলেন ‘হে বিরহী,
সরে থেকো না’। গানটির আস্থায়ীর সুরটুকু নিয়ে বিশ্বজিতের মুখে হেমন্ত গাইলেন ‘রাহ বনি
খুদ মঞ্জিল’। আর, বোধহয় সবার ওপরে ১৯৫৯ সালেরদীপ
জ্বেলে যাই ছবির সেই সম্মোহক ‘এই রাত তোমার আমার’-এর আস্থায়ী ব্যবহার করে, যা ছিল
একাকী প্রেমিকের প্রেমিকাকে অনুভবে-পাওয়ার গান, তাকে হেমন্ত ও কবি-গীতিকার কইফি আজমি
বদলে দিয়েছেন মুগ্ধ স্বামীর সামনে-উপস্থিত স্ত্রীর প্রতি সেই সম্মোহক ভালবাসার বহিপ্রকাশে।
গানের চিত্রায়নও প্রশংসনীয়। বাংলা গানটির ভিডিও ক্ষতবিক্ষত! তাই শুধু হেমন্তর কণ্ঠে
‘এই রাত তোমার আমার’ এবং তার পরেই ‘ইয়ে নয়ন ডরে-ডরে’-র পূর্ণ দৃশ্য-সম্বলিত ভিডিওটিই
সম্বল ইউটিউবে।
কোহরা বাণিজ্যিক সাফল্য
পায় নি। হয়তো বীস সাল বাদ-এ ব্যবহৃত ‘ফরমুলা’-র
পুনরাবৃত্তি – সেই এক প্রাসাদ, তাকে ঘিরে বা তার মধ্যে – বীস সাল বাদ-এ আপাত, এখানে আসল, মহিলা প্রেতাত্মার কণ্ঠে গান, এবং চিত্রায়নে
১৯৬২-র ছবিটির বহির্দৃশ্য গ্রহণের জায়গাগুলি অবধি অনেকটা এক থাকা, এবং সেই এক নায়ক-নায়িকা
জুটি – দর্শকদের একঘেয়ে লেগে থাকতে পারে। অবশ্য ওই ১৯৬৪-তেই মুক্তি পেয়ে, আবার স্ত্রীকণ্ঠে
(আপাত) ভৌতিক গান ব্যবহার করে বীস সাল বাদ-এর
সঙ্গে যুক্ত ধ্রুব চ্যাটার্জী রাজ খোসলার ও
কৌন থী ছবিতে দারুণ বাণিজ্যিক সাফল্য পান। দুটি ছবির কোনটি আগে মুক্তি পায়, অন্তর্জালে
তা নিয়ে পরস্পর-বিরোধী তথ্য রয়েছে।
এছাড়া, চিত্রনাট্যে যে ত্রুটি ছিল তা হেমন্ত আঁচ করলেও সঠিক
দোষটি ধরতে পারেননিঃ
… সিনেমা লাইনের লোকের কাছে ফুলমার্ক
পেল ‘কোহরা’। কিন্তু আমার মনে তবু সংশয়। ছবিটার
সব ভালো কিন্তু তবু একটা বিরাট ত্রুটি রয়ে গেছে গল্প বলার কায়দায়। একটা ধোঁয়াটে ভাব
রেখে দিয়েছেন পরিচালক … তাই আমি বীরেনবাবুকে বললাম, ‘সবই ঠিক আছে, কিন্তু প্রেতাত্মার
ব্যাপারটাকে দর্শকের কাছে অস্পষ্ট রাখছেন কেন। স্পষ্ট বলে দিন না ওটা প্রেতাত্মা। তাহলেই
সব পরিষ্কার হয়ে যায় …’
কিন্তু বীরেনবাবু আমার কথা মানলেন না। রাজি হলেন
না এতটুকু বদলাতে। (আনন্দধারা, ৮১)
ছবিটি দেখার পর বলতে বাধ্য হচ্ছি যে প্রেতাত্মার
ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা নেই। সমস্যা একমাত্র পুণমের ভূতের আচরণ!
রাজেশ্বরী অমিত সিং-এর দ্বিতীয় পক্ষ হয়ে আসতেই দাই-মা
তার প্রতি বিরূপতা প্রদর্শন করতে থাকে, কারণ রাজেশ্বরী পুণমের মতো অভিজাত নয়। পুণম
প্রাসাদের যে মহলে বাস করতো, রাজেশ্বরী সেখানে গেলে মৃতা পুণমের উপস্থিতি অনুভব করে,
তার হাসি শুনতে পায়, এমনকি আয়নার সামনে তার ছায়ামূর্তিকে বসে থাকতেও দেখে। ঘটনা চরমে
ওঠে পুণমের প্রেত যখন গান গাইতে-গাইতে রাজেশ্বরীকে তাড়া করে নিয়ে যায় ছাদের আলসেতে
এবং ফিসফিস করে তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলে। আতঙ্কিত, সম্মোহিত রাজেশ্বরী তাই করতে যাচ্ছিল,
এমন সময় অমিত তাকে ধরে ফেলে বাঁচায়। আমরা দেখেছি যে পুণমের জীবতাবস্থায় তার একাধিক
পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। তা, এরকম স্বৈরিণী নারী যে মৃত্যুর পর কোপনস্বভাব হয়ে নিরপরাধ
সতীনের ওপর চড়াও হবে, এমন ভূতের গল্প, মনে হয়, অনেক আছে।
কিন্তু এবার স্পয়লার-সতর্কতা
দিয়ে বলিঃ
আমরা প্রথমে জানছি যে প্রথম স্ত্রীর ব্যাভিচারে
ধৈর্য হারিয়ে অমিতই পুণমের মদ-খেয়ে-সংজ্ঞাহীন শরীরের ওপর গুলি চালিয়ে দেয়। তারপর গাড়ীসহ
পুণমের দেহ জলায় ডুবিয়ে দেয় । এই পরের দৃশ্যটি হিচককের সাইকো (১৯৬০) থেকে অনুপ্রাণিত । স্ত্রীহত্যার দায়ে অমিত গ্রেপ্তার হয়,
থানায় যাবার আগে বিহ্বল রাজেশ্বরী অমিতের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। এই দৃশ্য দেখে দাই-মা ছুটে
এসে আদালতে কবুল করে যে অমিত পুণমের মৃতদেহের ওপর গুলি চালিয়েছিল। দেবতুল্য স্বামীর
প্রতি পুণমের অবজ্ঞা দেখে দাই-মা স্বয়ং পুণমের মদে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করে!
গুলি চালালো স্বামী; বিষ দিল দাই-মা। পুণমের ভূত
এই দু’জনকে একবারের জন্যও কিছু করল না, তার যত রাগ নিষ্পাপ রাজেশ্বরীর ওপর! আর, রাজেশ্বরীকে
মারতে বিফল হয়ে পুণমের ভূত একেবারে হাওয়া হয়ে গেলো, অমিত-রাজেশ্বরী প্রাসাদে ফিরে সুখে
সংসার করা শুরু করল!
কোহরা বড় পর্দায় দেখেছি,
আশির দশকে, দু’বার। প্রথমবার ভবানীপুরের বিজলী সিনেমায় দুপুরের শো-তে। হলে পৌঁছে দেখি
ছবি শুরু হয়ে গেছে, গান চলছে ‘ঝুম ঝুম ঢলতি রাত’। অতএব দ্বিতীয়বার গেলাম মধ্য কলকাতায়,
কলকাতা কর্পোরেশনের লাগোয়া মিনার্ভায় (যার নাম পরে বদলে হয় ‘চ্যাপলিন’; কোহরা দেখার সময় এই পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল কিনা
মনে নেই) । সেখানে ছবিটির রোজ তিনটি প্রদর্শনী ছিল। তৃপ্তি করে গোড়া থেকে ছবিটি দেখেছিলাম।
হাতে গোনা যে ক’টি হিন্দী ছবি একাধিকবার দেখেছি, সেগুলির মধ্যে কোহরা তৃতীয়।
লক্ষ্যণীয়, সাম্প্রতিক সময় অবধি বিজলী প্রধানত বাংলা
ছবিই আনত। আর মিনার্ভা/চ্যাপলিন মাঝে-মধ্যে হিন্দী ছবির আগ্রাসনের কাছে মাথা নত করলেও
ষাটের দশকের শেষে পুনর্যাত্রা শুরু করেছিল ইংরেজী – মূলত কলম্বিয়া কোম্পানীর – ছবির
মুক্তিস্থান হিসেবে!