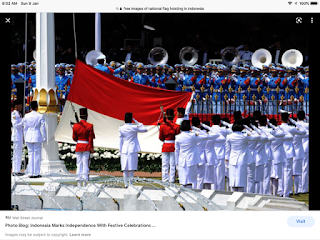সিনেমার পৃথিবী – ১৬
ব্রিটেনের পর এবার আমাদের গন্তব্য জার্মানি।
ইতালি আর ফ্রান্সের সিনেমা দেখে আপনি যদি জার্মানির ছবি দেখতে বসেন, কখনোই মনে হবে
না আপনি অপূর্ব বা সুন্দর সিনেমা দেখছেন। কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন যে নিখুঁত ফিনিশিং
কী জিনিষ! কেন জার্মান পার্ফেকশন নিয়ে গোটা পৃথিবীতে এত কথা ছড়িয়ে আছে। মনে করে দেখুন, গোটা পৃথিবীর ১২টা ক্লাসিক নিয়ে যেদিন
আলোচনা করেছিলাম, জার্মানির ‘মেট্রোপোলিস’ নিয়ে লিখেছিলাম। সেই সিনেমার সেট কীভাবে
বানানো হত আর প্রতি শট্ নিখুঁত করার জন্য তার মানুষজনের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করা হত – সেটা মনে পড়ছে? টি এস এলিয়টের
এক ছোট্ট কবিতা মনে পড়ে গেল, ‘মর্নিং অ্যাট
দ্য উইন্ডো’ – ‘They are rattling breakfast
plates in basement kitchens/ And along the trampled edges of the street/ I am
aware of the damp souls of housemaids/ Sprouting despondently at area gates.’ সকালের
একদম নিখুঁত ছবি, তাই না? আজ আমরা জার্মান সিনেমার এই পার্ফেকশন নিয়ে এগোব।
আরেকটা কথা। আমরা এর আগেও বারবার একটা
টার্ম ব্যবহার করেছি – জার্মান এক্সপ্রেসনিজম। আজ আলোচনা শুরুর আগে সিনেমার প্রেক্ষিতে
সেটার ইতিহাস একটু ঘেঁটে নেব। এক্সপ্রেসনিস্ট শিল্প আন্দোলন (যা বাস্তবের থেকে প্রাধান্য
দিত মানসিক জগৎকে) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই আস্তে আস্তে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল।
১৯১৪ থেকে ১৯১৮ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, যখন জার্মানি, ইতালি আর অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি
একদিকে হয়ে গেল (সঙ্গে তুর্কীও এসে জুটল) আর উল্টোদিকে বাকি ইউরোপ ও আমেরিকা, তখন গোটা
বিশ্বের সঙ্গে জার্মানির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই সময় জার্মানিতে বিদেশি সিনেমা
দেখানো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এক্সপ্রেসনিস্ট আন্দোলন নিজস্ব সিনেমার মধ্যে দিয়ে
জার্মানিতে গন্ডীবদ্ধ হয়ে পড়ে। এইসব সিনেমার চিত্রায়ন হত বেয়াড়া কিছু থিম নিয়ে যা সাধারণ
নয়, ক্যামেরার কাজ অন্যরকম ও অ্যাঙ্গল জ্যামিতির হিসেবে অদ্ভুত, এবং এইসব ছবিতে অবাস্তব ভয়, সাসপেন্স
বা থ্রিলার দেখানো হত যা পরবর্তীকালে যোগাযোগ
স্বাভাবিক হবার পর হলিউড লুফে নিয়েছিল। এটা ঘটনা যে জার্মান নির্বাক সিনেমা সমসাময়িক
হলিউড সিনেমার চেয়ে টেকনিকের দিকে খানিকটা এগিয়ে ছিল। কিন্তু এক্সপ্রেসনিজমের শুরুর
দিকের সিনেমায় কিছু খামতি ছিল যা পরবর্তীকালে মুর্নাউ বা ফ্রিজ ল্যাং বা কার্ল ফ্রয়েড
বদলে নেন। এবং সেই স্টাইল হিচকক্ থেকে শুরু
করে অরসন ওয়েলেস, অনেকেই ব্যবহার করেন।
এবার তাহলে কিছু জার্মান ছবি বাছা যাক।
প্রথমে ১৫টা ছবি বেছে নিই যা দেখলে আপনি জার্মানির ইতিহাস বা বর্তমান সিনেমা সম্বন্ধে
খানিকটা আঁচ পাবেন। এই বাছাইয়ের প্রথম চারটে ছবিই কিন্তু জার্মান এক্সপ্রেসনিস্ট সিনেমা।
রবার্ট ভিনের ‘দ্য ক্যাবিনেট অব ডঃ ক্যালিগারি’ (১৯২০), মুর্নাউ-এর ‘নসফেরাতু’ (১৯২২),
ফ্রিজ ল্যাং-এর ‘মেট্রোপোলিস’(১৯২৭) ও ‘এম’ (১৯৩১), উইকির ‘দ্য ব্রিজ’ (১৯৫৯), হার্জগের ‘আগুয়ার,
র্যাথ অব গড’ (১৯৭২), ফাসবিন্ডারের ‘আলিঃ ফিয়ার ইটস
দ্য সোল’ (১৯৭৪), স্লোনডর্ফের ‘দ্য টিন ড্রাম’ (১৯৭৯), পিটারসেনের ‘দ্য বোট’ (১৯৮১),
ভেন্ডাসের ‘উইংস অব ডিজায়ার’ (১৯৮৭), ক্যারোলিন লিঙ্কের ‘নোহ্যয়ার ইন আফ্রিকা’ (২০০১),
ফন দোনার্সমার্কের ‘দ্য লাইভস অব আদার্স’ (২০০৬), রুজোউইদস্কির ‘দ্য কাউন্টারফেটার্স’
(২০০৭), মাইকেল হানেকার ‘দ্য হোয়াইট রিবন’ (২০০৯) এবং পেজোল্ডের ‘বারবারা’ (২০১২)।
এগুলোর ভেতর আজ আমরা এই ছ’টা ছবি নিয়ে বিশদ আলোচনা করবঃ ‘নসফেরাতু’ (১৯২২), ‘এম’ (১৯৩১),
‘দ্য টিন ড্রাম’ (১৯৭৯), ‘দ্য বোট’ (১৯৮১), ‘লাইভস অব আদার্স’ (২০০৬) ও ‘দ্য হোয়াইট
রিবন’ (২০০৯)।

‘নসফেরাতুঃ দ্য সিম্ফনি অব হরর’ আমি
প্রথম দেখি ২০০৪ সালে। নির্বাক ছবি। সেই সময়
থেকে, এই বই দেখার পর, ইচ্ছে হত এই সিনেমা নিয়ে কিছু লিখি। কারণ ডারউইনের ‘সারভাইভাল
অব দ্য ফিটেস্ট’ থিয়োরি যদি কোন সিনেমার ক্ষেত্রে
প্রযোজ্য হয়, সেটা এই সিনেমা। ঠিক একশ বছর আগের এই ছবি ব্রিটিশ লেখক ব্রাম স্টোকারের
বিখ্যাত উপন্যাস ‘ড্রাকুলা’ (১৮৯৭) অবলম্বনে তৈরি। অবশ্য ড্রাকুলা নিয়ে এটা প্রথম সিনেমা
নয়, প্রথম সিনেমা ছিল হাঙ্গেরির ‘ড্রাকুলা জ ডেথ’ (১৯২১)। কিন্তু সেই সিনেমা জনপ্রিয়
হয়নি, এবং আশ্চর্যভাবে তার একটাও কপি আজ আর নেই। পরের বছর ফ্রেডেরিক উইলহেল্ম মুর্নাউ
‘নসফেরাতু’ তৈরি করেন। মুশকিল হল, তিনি ড্রাকুলা উপন্যাসের স্বত্ব কিনতে পারেন নি। তাই খুব কম বাজেটে জার্মানির প্রেক্ষাপটে
কাউন্ট ড্রাকুলা নাম বদলে কাউন্ট অর্লফ করে এবং বেশ কিছু সিন বদলে দিয়ে এই সিনেমা তৈরি
করেন। তদ্দিনে স্টোকার আর বেঁচে নেই। কিন্তু তার বিধবা বৌ কোর্টে এই সিনেমার বিরুদ্ধে
নালিশ ঠোকেন। এবং কোর্ট নির্দেশ দেয় এই সিনেমার সমস্ত কপি পুড়িয়ে ফেলা হোক। সেটাই হয়।
কিন্তু রিলিজের পর কোন এক সিনেমা প্রেমিকের উৎসাহে একটা কপি তার সংগ্রহে রয়ে গেছিল।
সেটাই উদ্ধারের পর ১৯৩৭ সালে আবার এই সিনেমা আমেরিকায় দেখান হয়। এবং প্রথম দর্শনেই
বাজিমাৎ। তুমুল হিট। এরপর মুর্নাউ-এর নাম বাদ দিয়ে এই সিনেমার এক রিমেক ১৯৭৯ সালে রিলিজ
হয়। তারপর একে একে অন্যান্য রিমেক। জনপ্রিয় ভয়ের এই ছবি সারা পৃথিবীর প্রথম ১০০ ছবির
ভেতর জায়গা করে নেয়।
থিম বলব না, কারণ ড্রাকুলা ছবির থিম
বাচ্চারাও জানে। কিন্তু নসফেরাতু প্রথম দিকের
এক্সপ্রেসনিস্ট সিনেমার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। এর সেট ডিজাইন থেকে শুরু করে ক্যামেরার অ্যাঙ্গল, আউটডোর বা ইন্ডোর শট,
কফিন নিয়ে মিছিল, পারিপার্শ্বিক তৈরি করা, ক্যামেরার হঠাৎ স্টপ-শট এবং প্রকৃতির ছবি
– এই সমস্ত কিছু অদ্ভুত ও অনবদ্য। হ্যাঁ,
এখন এই সিনেমা দেখলে হয়ত আর ভয় লাগবে না, কিন্তু চিত্রায়ন ও কলাকারিত্ব এখনো চমক জাগায়।
এবং জার্মানির ইহুদিবিদ্বেষ আমরা মোটামুটি সবাই জানি। এই সিনেমাতেও কিন্তু সেটা প্রচ্ছন্নভাবে
ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কাউন্ট অর্লকের ছূঁচলো নাক, বড় বড় নখ, লম্বা সরু চেহারা আর টাক,
এগুলো ইহুদিদের লক্ষণ। অনেকটা ইঁদুরের মত, যা ইহুদিদের চটানোর জন্য বলা হত।
এই ছবির পরেই আমি বাছলাম ফ্রিজ ল্যাং-এর
‘এম’ যা এক্সপ্রেসনিস্ট আন্দোলনের আরেক উদাহরণ। আরেক ক্লাসিক জার্মান ছবি। ল্যাং-এর
প্রথম সবাক চলচ্চিত্র। এই সিনেমা এক মনস্তাত্বিক
সাসপেন্স থ্রিলার। বার্লিনের রাস্তায় এক সিরিয়াল কিলার, যে বাচ্চাদের খুন করছে, তাকে
নিয়ে ছবি। এবং সে ধরা পড়ার পর তার বিচার। নসফেরাতু বা মেট্রোপোলিসের তুলনায় এর থিম
অন্য রকম।

‘এম’ পৃথিবীর প্রথম সিরিয়াল কিলারের
ওপরে বানানো ছায়াছবি। মুখ্য চরিত্রে পিটার
ল বোধহয় জীবনের সেরা অভিনয় এখানে উপহার দিয়ে গেছেন। এবং এই সিনেমা অদ্ভুত রকমভাবে ওপেন
এন্ডেড। একজন মনস্তাত্বিক রুগি, সে একের পর এক বাচ্চাদের মেরে ফেলেছে, তাকে কি আদৌ
মৃত্যুদন্ড দেওয়া উচিৎ এবং দিলেও কি সেইসব বাচ্চারা আর ফিরে আসবে? এই প্রশ্ন নিয়ে সিনেমা
শেষ। বিচার শেষ হবার আগেই। ক্যামেরার কাজ অনবদ্য। ট্র্যাকিং শটের মাধ্যমে লং শট, প্রায়
নব্বই বছর আগে, ভাবা যায়! এছাড়াও ল-এর মুখে শিস হিসেবে মাঝে মাঝেই এক লেইটমোটিফের ব্যবহার,
যা সঙ্গীতের ছোট্ট এক অংশবিশেষ, আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ১ ঘন্টা ৫০ মিনিটের এই সিনেমা
দেখলে আক্ষরিক অর্থেই মনে হবে সিরিয়াল কিলিং ব্যাপারটা মাইক্রোস্কোপের নিচে ফেলে কাটাছেঁড়া
করা হয়েছে। অবশ্য এটাও বলতে চাই, যদিও সেটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত, ল্যাং-এর ‘মেট্রোপোলিস’
আর ‘এম’ দেখে মনে হয় ভদ্রলোক নাৎসিদের মনে প্রাণে ঘেন্না করতেন।
ভোলকার স্লোনডর্ফের ‘দ্য টিন ড্রাম’
বাছলাম অন্য বেশ কয়েকটা কারণের বাইরেও আরেক কারণে। এই উপন্যাসের লেখক গুন্টার গ্রাস
আমার অন্যতম প্রিয় এক লেখক বলে। আসলে গোটা
পৃথিবীতে হাতে গোনা যে কজনের ম্যাজিক-রিয়েলিজম নিয়ে লেখা পছন্দ করি, গ্রাস তার ভেতর
একজন। এবং ১৯৫৯-এর সেই বই, যা থেকে পরবর্তীকালে ১৯৭৯-র এই সিনেমা, সেই জাদু বাস্তবতার
এক জ্বলন্ত উদাহরণ। ১৯৯৯ সালে গ্রাস যখন সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, তখন তার স্তুতি করতে গিয়ে সুইডিশ
নোবেল কমিটি লিখেছিল, গুন্টার হচ্ছেন সেই লেখক ‘whose frolicsome black fables
portray the forgotten face of history’। যাইহোক, এই সিনেমায় ফিরি। নাৎসি জার্মানির
আবহে এই ছবি সম্পর্কের এক জটিল ক্যানভাস। অস্কার এক তিন বছরের বাচ্চা ছেলে। তার দাদুর
সময় থেকেই তাদের বংশের জন্মপঞ্জী নিয়ে বেশ গন্ডগোল ছিল। যেমন অস্কারের বাবা কে, সেটা
তার মা অ্যাগনেস-ও সঠিক জানে না। আলফ্রেড বা জান, এদের ভেতর কোন একজন। সমাজের এই রকম
অনেক জটিল ধাঁধাঁ আর নোংরামো দেখে অস্কার তার তিন বছর বয়সে সিদ্ধান্ত নেয় সে আর বড়
হবে না। এবং তার মায়ের উপহার দেওয়া এক টিনের ড্রাম নিয়ে সারাদিন পড়ে থাকে। তার বৃদ্ধি
সত্যিই থেমে যায়। এবং সে এক অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী হয়। কেউ তার ড্রাম কেড়ে নিতে চাইলে
সে এত জোর চেঁচাতে পারত যে আশেপাশের সব কাচ ভেঙে যেত। এখান থেকে সিনেমা নিজের মত গড়িয়ে
চলে। অস্কারের বয়স বাড়ে কিন্তু তার বৃদ্ধি হয় না। সে একে একে ভালবাসার সম্পর্কে জড়ায়
এবং তারা মারা যায়। অস্কারের মা-ও মারা যায়। একসময় অস্কার আবার সিদ্ধান্ত নেয় যে সে
আবার বড় হবে। এরপর কোন একজন ঘোষণা করে যে অস্কার সত্যিই আবার বড় হচ্ছে। এবং তারপরেই
অস্কার অনুভব করে, তার চেঁচানোর সেই ক্ষমতা আর নেই। অসাধারণ ম্যাজিক রিয়েলিজম।
এক পুরনো ফাটা টিনের ড্রামকে বিরক্তি
প্রকাশের মোটিফ হিসেবে রেখে সম্পর্কের জটিল মোড়কে ভেঙে পড়া সামাজিক কাঠামোর একের পর
এক স্পষ্ট দৃশ্যায়ন। সেই থিমের নিরিখে প্রায় ২ ঘন্টা ৪০ মিনিটের এই ছবিকে অল টাইম ফেভারিট
জার্মান ছবির লিস্টে বেছে নিতে কোন দ্বিমত থাকা উচিৎ নয়।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মনস্তাত্বিক
দোটানা সত্বেও কীভাবে কিছু মানুষ দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছিলেন, সেই নিয়ে ওলফ্গ্যাং
পিটারসেনের ছবি ‘দ্য বো’ (জার্মান ভাষায়
Das Boot)। একই নামের ১৯৭৩ সালের জার্মান উপন্যাস অবলম্বনে এই ছবি। আড়াই ঘন্টার সিনেমা।

১৯৪১ সাল। জার্মান সাবমেরিন U-96 বন্দর
ছেড়ে আটলান্টিকের উদ্দেশ্যে ভেসে যায়। সেই সাবমেরিনের সদস্যদের ভেতর যারা প্রবীন, তারা
যুদ্ধের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ কিন্তু যারা বয়সে নবীন, তারা যুদ্ধের বিষয়ে উৎসাহী। আটলান্টিকে
তাদের সঙ্গে একবার ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান আর একবার ব্রিটিশ নৌবাহিনীর যুদ্ধ হয়। সাবমেরিনের
ক্ষতি হয়। কাজ শেষ করে তারা যখন ক্রিসমাস পালন করতে বন্দরের দিকে আবার ফিরে আসছে, তখন
আদেশ আসে দেশে ফেরা চলবে না, তাদের সোজা যেতে হবে ইতালি। যাত্রাপথে তারা স্পেনের এক
বন্দরে রাত কাটায়, জ্বালানী-টর্পেডো-অন্যান্য জিনিষপত্র ভরে নিয়ে ইতালির উদ্দেশ্যে
যেতে শুরু করে। কিন্তু জিব্রাল্টারের কাছে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান তাদের ওপর হামলা করে
সাবমেরিনের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। সেখান থেকে কোনমতে ভাঙা সাবমেরিন নিয়ে তারা রাতের
অন্ধকারে আবার জার্মানির বন্দরে ফিরে আসে। ঠিক তখনি মিত্রশক্তির বিমানবাহিনী বোম মেরে
গোটা বন্দর উড়িয়ে দেয়। সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন ও বেশিরভাগ কর্মী মারা যায়। সাবমেরিন আস্তে
আস্তে জলে ডুবে যায়।
এই সিনেমাকে আমি যুদ্ধের ছবি হিসেবে
দশে দশ দেব। এমন এক যুদ্ধের সিনেমা যেখানে টানটান উত্তেজনা আর ঘরে ফিরতে না পারা যোদ্ধাদের
মানসিক দোটানা পাশাপাশি ফুটে উঠেছে। ক্যামেরার কাজও বেশ ভাল। কিন্তু ইতিহাসের দলিল
হিসেবে এই সিনেমাকে রাখা যাবে না কারণ ১৯৪১-এর শেষভাগে ব্রিটিশ বিমান বাহিনী জার্মানির
কোন বন্দর বোম মেরে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল – এই তথ্য পুরো মনগড়া।

বার্লিনের পাঁচিল ভাঙার আগে পূর্ব জার্মানির
পুলিস গোপনে কীভাবে পূর্ব জার্মানির বাছাই করা কিছু লোকজনের গতিবিধির ওপর নজর রাখত,
সেই নিয়ে ফ্লোরিয়ান ফন দোনার্সমার্কের ‘দ্য লাইভস অব আদার্স’। সিনেমা শুরু হচ্ছে ১৯৮৪ সালের পূর্ব জার্মানিতে। এক স্তাসি পুলিস, এক
বিখ্যাত নাট্যকারের গতিবিধির ওপর গোপনে নজর রাখার ভার পায়। সে নাট্যকারের ফ্ল্যাটে
গিয়ে গোপন মাইক্রোফোন বসিয়ে আসে। এবং কিছুদিন পর বুঝতে পারে, নাট্যকারের গতিবিধির ওপর
নজর রাখা হচ্ছে, যেহেতু তার প্রেমিকার ওপর এক মন্ত্রীর কুনজর রয়েছে। সে একদিন নিজের
পরিচয় গোপন রেখে নাট্যকারের প্রেমিকাকে পরামর্শ দিয়ে আসে মন্ত্রীর থেকে দূরে থাকতে।
এরপর পূর্ব জার্মানির বৈষম্য নিয়ে সেই নাট্যকার পশ্চিম জার্মানির এক পত্রিকায় এক প্রবন্ধ
লেখে। সেই প্রবন্ধ মন্ত্রীর চোখে পড়ে। সে পুলিস দিয়ে সেই ফ্ল্যাট সার্চ করায়, যে টাইপরাইটারে লেখা হয়েছিল, সেই টাইপরাইটার খুঁজে বের
করার জন্য। পুলিসের ভয়ে নাট্যকারের প্রেমিকা টাইপরাইটার কোথায় আছে সেটা বলে দেয় এবং
এক ট্রাকের নিচে পড়ে আত্মহত্যা করে। এদিকে পুলিস এসে সেই টাইপরাইটার কোথাও খুঁজে পায়
না। যদিও তারা নাট্যকারকে জেলে পুরে দেয়। ১৯৮৯ সালে বার্লিনের পাঁচিল ভেঙে ফেলার পর
সেই স্তাসি পুলিস আর তার সহকর্মীরা কাজ ছেড়ে চলে যায়। সেই নাট্যকারও জেল থেকে ছাড়া
পেয়ে যায়। কয়েক বছর পর সেই নাট্যকার এক অনুষ্ঠানে সেই মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে যে তার
ওপর নজর রাখা হয়নি কেন? উত্তরে মন্ত্রী জানায় যে স্তাসি পুলিস প্রথম থেকেই তার ওপর
নজর রেখেছিল। নাট্যকার নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এসে গোপন মাইক্রোফোন খুঁজে পায় এবং বুঝতে
পারে যে সেই স্তাসি পুলিস-ই তার ফ্ল্যাট থেকে টাইপরাইটার সরিয়ে তার উপকার করেছিল। অবশ্য
তদ্দিনে সেই স্তাসি পুলিশ অন্য এক শহরে পোস্টম্যানের চাকরি নিয়ে চলে গেছে। নাট্যকার
তার পরবর্ত্তী বই সেই স্তাসি পুলিসকে উৎসর্গ করে।
তথাকথিত স্পাই বা গুপ্তচর সিনেমার বাইরে
এসে এই ছবি এমন কিছু দর্শন রেখেছে, যা মানুষের মনের কাছাকাছি। প্রথমত, এর প্লট একদম
উলের মত যত্ন করে বোনা, যেখানে মানুষের চাপা চিন্তাভাবনা আর কামনা হঠাৎ হঠাৎ সারফেসে
ভেসে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, যে সমাজ নিপীড়ন করতে ভালবাসে, সেখানে নিজের ইচ্ছেগুলোও যে বোঝা
হয়ে ওঠে, সেটা স্পষ্ট দেখান হয়েছে। এছাড়াও, মানসিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন কোন এক চরিত্রকে
কোথায় নিয়ে দাঁড় করাতে পারে, সেটাও এই সিনেমা দেখিয়েছে। এবং পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের
চেতনাকে কীভাবে বাজি রাখতে হয়, সেই কথাও তুলে ধরেছে ১৩৭ মিনিটের এই ছবি।
হ্যাঁ, যে কথাটা না বললে এই ছবির আলোচনা
পুরো হবে না, তা হল – এই ছবির মুখ্য চরিত্র উলরিখ মুহে বাস্তব জীবনে বিয়ের ছ’বছর পর
জানতে পারেন যে তার স্ত্রী এদ্দিন এক গোপন স্তাসি এজেন্ট হিসেবে কাজ করছিল।

মাইকেল হানেকার ‘দ্য হোয়াইট রিবন’ এক
বিতর্কিত মাস্টারপিস। বিতর্কিত, কারণ হানেকা শক্ত থিম নিয়ে কাজ করতেই ভালবাসেন এবং
তাঁর সিনেমা ঠিক কী বার্তা দিতে চায়, সেই নিয়ে দর্শকও মাঝে মাঝে ধাঁধাঁয় পড়ে যান। এবং
হানেকার ছবিতে নিষিদ্ধ কিছু ব্যাপার থাকবেই।
যেমন এই ছবিতে - নিষিদ্ধ যৌনতা, পেডোফিলিয়া, হিংসা, খুন, অনেক কিছু আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ
শুরু হবার ঠিক আগে জার্মানির কোন এক গ্রাম দেখান হয়েছে। সেই গ্রামে রাজত্ব করেন এক
ভূস্বামী, এক ডাক্তার আর এক চার্চ আধিকারিক। তিনজনেই অর্থ ও ক্ষমতাবশে আর অন্যদের কঠিন
শাস্তি দেবার সুবাদে গ্রামের মাথা। হঠাৎ সেই গ্রামে একে একে ক্ষতিকারক কিছু ঘটনা ঘটতে
শুরু করে। দুটো গাছের মাঝে বাঁধা এক দড়িতে আটকে ডাক্তারের দুর্ঘটনা ঘটে। ভূস্বামীর
ছেলে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। পরের দিন তাকে যখন এক কাঠচেরাই মিলের মধ্যে পাওয়া
যায়, তার সারা গায়ের বেতের দগদগে ঘা। এরপর কিছু পরিবার গ্রাম থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়।
ছবি শেষ হচ্ছে ১৯১৪-র যুদ্ধ শুরুর আবহে। তখনো গোটা গ্রামে হৈচৈ, কিন্তু সেইসব বিক্ষিপ্ত
হিংসার কোন কূলকিনারা হয়নি।
তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে, ছবির নাম
‘হোয়াইট রিবন’ কেন? সাদা রিবনের বো তৈরি করে
আমরা যে কোন ধরনের হিংসার বিরোধীতা করি। এটা এক ধরনের বিশুদ্ধতা বা নিখাদ অনুভূতির
প্রতীক। ফলে সাদা রিবন আর বাচ্চারা যেন ঝকঝকে নিষ্পাপ সমাজের উপস্থাপক, এভাবেই দেখা
হয়। কিন্তু এই সিনেমায় হানেকা-র কাছে সেটার অস্তিত্ব নেই। আর নেই বলেই দর্শকের কাছে
অক্সিমোরন হিসেবে এই নাম তুলে দেওয়া হয়েছে। ১৪৪ মিনিটের এই সাদা-কালো ছবির আরেক তারিফ
করার মত দিক হল, এর সিনেমাটোগ্রাফি। ছবির বেশিরভাগ শুটিং হয়েছে অন্ধকার ফ্রেমে। সামনে
বড়জোর মোমবাতি, লম্ফ বা টর্চ। এমনকি খামারবাড়ি পুড়ে যাবার লেলিহান আগুনের দৃশ্যেও চারপাশে
জমাট অন্ধকার। সঠিক আলো-আঁধারির খেলা দেখানোর জন্য এখানে ক্যামেরাম্যান নতুন এক টেকনিক
তৈরি করেছিলেন – সিনে রিফ্লেক্ট লাইটিং সিস্টেম। ফলে প্রত্যেক ফ্রেমে হিংসার টোন একটু
করে কমিয়ে উৎকন্ঠা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এবং ছবিতে শেষ অব্ধি যে ধারণাকে গুরুত্ব
দেওয়া হয়েছে, তা হল, ছবি যেন দর্শকের মাথায়
শেষ হয় – পর্দায় নয়।
কোন কোন সমালোচক এই সিনেমাকে নাৎসি হিংসার
শুরুর দিকের দলিল হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। কিন্তু আমার ছোট বুদ্ধিতে আমি সেটার
বিরোধীতা করি। কারণ সেটা সত্যি হলে ধরে নিতে হবে আমাদের সবার মনেই নাৎসি হিংসার বীজ
লুকিয়ে আছে। এই ছবি আসলে এক ভূতের সিনেমা, যেখানে কোন ভূত নেই। কারণ সেই ভূত আমাদের
মত এক বা একাধিক অচেনা মানুষ, আর তাকে ভয় পায়
আমাদেরই মনের শঙ্কা ও উৎকন্ঠা।
শেষ করার আগে এক ছোট্ট পয়েন্ট নিয়ে দু’এক
কথা বলি। আমি এর আগের বিভিন্ন পর্বে যখন ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন বা ব্রিটেনের সিনেমা
নিয়ে লিখেছি, তখন বলেছি যে ৫০ ও ৬০-এর দশকে নব্য-বাস্তবতা ছড়িয়ে পড়ার হাত ধরেই এইসব
দেশের সিনেমায় স্বর্ণযুগ এসেছিল। কিন্তু জার্মানির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। দ্বিতীয়
বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে অন্তত ১৯৭০ সাল অব্ধি গোটা পৃথিবী জার্মানির জন্য দরজা বন্ধ করে
রেখেছিল। ফলে এই সময় জার্মান সিনেমার বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি।
(ক্রমশ)