ধারাবাহিক উপন্যাস
ছেঁড়া শেকড়ের অন্তরাখ্যান
(২)
মানচিত্র মানে এক ধারালো লেড পেনসিল
শ্রীচরণকমলেষু বাবা,
আশাকরি আপনি ও মা সুস্থ আছেন। মেজদি, বড় জামাইবাবু, দাদা, অমু, নিরু কুশলে আছে। দাদার উপর অধিক ভার পড়িতেছে বুঝিতে পারি। আর দুইটি বৎসর মাত্র অপেক্ষা। আমি পাশ করিয়া দাদার পাশে দাঁড়াইয়া সংসারের দায়িত্ব লইতে পারিব। আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইয়াছি। ক্লাস পুরাপুরি আরম্ভ হয় নাই। আপনাদের আশীর্বাদে সসম্মানে এম-এ পাশ করিতে পারিব বলিয়া আশা রাখি। অমু এবং নিরু যেন মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করে। আপনিই আমাদের শিখিয়েছেন একমাত্র লেখাপড়া চক্ষু উন্মীলন করিতে পারে। আর অধিক কী? আমার জন্য চিন্তা করিবেন না। পূজার ছুটিতে আপনাদের সহিত সাক্ষাতে সব বলব। আপনি এবং মা আমার সভক্তি প্রণাম নেবেন। ভাইবোনদের আমার প্রাণভরা ভালোবাসা জানাই।
ইতি বিনীত, মনু।
পোস্টকার্ডখানা পড়ে কথামৃতর মধ্যে রেখে দিলেন ধীরেন্দ্রনাথ বসু। মনোরঞ্জনের শেষ চিঠি। গত ছ’বছরে অন্তত কয়েকশোবার তিনি এটি পড়েছেন। আশা করেছেন মনু ফিরে আসবে। আসেনি। ক-মাস পর তার একখানা টেলিগ্রাম এসেছিল, “গান্ধীজী হিয়ার”। আর খবর পাননি, মনু ফেরেনি। টেলিগ্রামটা তাঁর ট্রাঙ্কে আছে। ট্রাঙ্কের লোহার চাবি কোমরের কারে বাঁধা। ধীরেন্দ্রনাথ নির্জীবের মতো তক্তপোশের ওপর শুয়ে পড়লেন। কাঁঠালকাঠের বেঢপ তক্তপোশে পাতলা তোশক পাতা। তাতে শস্তায় কেনা খসখসে চাদর। শক্ত দু-তিনখানা মাথার বালিশ, গোটাদুই গায়ের চাদর। ভোরবেলা উঠে বিছানা ঝেড়েঝুড়ে, তোশক-সমেত মুড়ে মাথার দিকে গুটিয়ে রেখেছেন। খালি কাঠে শীতলপাটি বিছানো। লোকজন এলে অথবা নিজেদের সারাদিনের শোওয়া-বসা সেখানেই। অনিচ্ছাসত্বে অপটু হাতে কাজটা তাঁকে করতে হচ্ছে। ঘরের একধারে বাঁশের আলনা। পাশে পরপর দু-খানা লোহার ট্রাঙ্ক একটার ওপর আরেকটা রাখা। স্ত্রীর ট্রাঙ্কের চাবির খবর ধীরেন্দ্রনাথ রাখেন না এবং ভেতরে কী থাকে জানেন না। সাত-আট দিন হল তারাসুন্দরী শান্তিপুরে গেছেন মেজোমেয়ে রমলার কাছে। বড়জামাই মুরারী এসে নিয়ে গেছে। রমলা পৌঁছসংবাদ দিয়েছে। সেখানে তারাসুন্দরীও দু-কলম লিখেছেন, ‘আমরা ভাল আছি। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিয়েন।’
স্ত্রীর লেখা অংশটি বারবার দেখেন তিনি। মুখে সামান্য হাসি খেলে
যায়। তারাসুন্দরী নিরক্ষর নন, ইশকুলে চারক্লাস পর্যন্ত পড়েছেন। বছর দুই পর তাঁদের বিবাহের
চারদশক পূর্ণ হবে। দেখতে দেখতে এতগুলো বছর পেরিয়ে এলেন। বিবাহের সময় ধীরেন্দ্রনাথ পঁচিশ
বছরের সুঠাম যুবক, তারাসুন্দরী বারো-তেরো বছরের বালিকা। বিবাহের পাঁচবছর পর এক বৃহস্পতিবার
ভরসন্ধেয় তারাসুন্দরীর কোলে প্রথম সন্তান এল। ধীরেন্দ্রনাথের বাবা নাম রাখলেন কমলা।
লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো সে মেয়েই বা রইল কোথায়?
এ বয়সে একা থাকলে স্মৃতিকাতরতা স্বাভাবিক। সঙ্গে দুঃখ আর অনিশ্চিত ভবিষ্যত-সংক্রান্ত দুশ্চিন্তার পাহাড় ঘাড় সোজা করতে দেয় না। এইভাবে থাকার কথা ছিল তাঁর? তাঁর পরিবারের? ধীরেন্দ্রনাথ নিজের দু-হাত চোখের সামনে ধরলেন। শিরা জেগে-থাকা ফর্সা ধপধপে হাত। চারবছর আগে ষাট পেরিয়ে গেছেন। বার্ধক্য যত না শরীরে নেমেছে তার চেয়ে অনেক বেশী মনে। ভূগোলের ডাকসাইটে মাস্টারমশাই ছিলেন। শুধু পেনসিল দিয়ে অবলীলায় অতি নিখুঁত মানচিত্র আঁকতেন। ছাত্রদের দেখাতেন দেশের মানচিত্র। সহজ ভাষায় প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক মানচিত্রের পার্থক্য বোঝাতেন। গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ইছামতীর গতিপথ চেনাতেন। স্কেলের মাপে দিল্লী, কলকাতা, লাহোর, ঢাকার দূরত্ব শেখাতেন। স্কুলের ছুটি পড়লে পায়ে হেঁটে, নৌকায়, একান্ত প্রয়োজনে ট্রেনে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে একা বেরিয়ে পড়তেন। ঘুরে বেড়াতেন, নিজের বিশাল দেশ চিনতেন। পুরনো দিন মনে পড়লে রক্তচাপ বাড়ে। বুকের মধ্যে টনটন করে যন্ত্রণা হয়। ধীরেন্দ্রনাথ অপলক চোখে নিজের ডানহাতের পাতার দিকে চেয়ে রইলেন। রেখাগুলো মিলেমিশে মানচিত্রের আকার নিয়েছে। সেখানে অজস্র ক্ষত। নদীতে কালচে রক্তের ধারা। পাঁচবছর আগে একটা অর্বাচীন আন্তর্জাতিক লাইন পরিকল্পিতভাবে আশৈশব চেনা মানচিত্রকে তিন টুকরো করে ভেঙে দিয়েছে। তাঁর গ্রাম, তাঁর জেলা আর তাঁর নেই। সে সব এখন বিদেশ, দু-হাজার মাইল দূরের ভূখণ্ডের অংশ। নতুন মানচিত্র তিনি আঁকতে পারেন না। চানও না। পেনসিলের সিস ফুটে ক্ষতবিক্ষত আঙুল। ঘামের বদলে দানাদানা রক্ত ফুটছে বুকে, কপালে। হাত মুঠো করে তিনি নামিয়ে রাখলেন। মুখে শব্দ করলেন, “উঃ উঃ”।
অমলা পাশের ঘরে ছিল। বইপত্র গুটিয়ে রেখে উঠে এল। বাবার শয্যার
পাশে দাঁড়িয়ে কপালে হাত রেখে চিন্তিত গলায় বলল,
“বাবা, বড় ঘাম দিতাছে আপনার! বাতাস দেই?”
“না না বাতাস দেওন লাগত না। তুই ঘরে যা গিয়া। নিরু ইশকুলে গেছেনি?”
“গেছে।”
“বলদাডার যে কবে জ্ঞান অইব! যা তুই—, আমি ঘুমাই।”
আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি, ভ্যাপসা গরম। বৃষ্টি তেমন হচ্ছে না। চোখ বন্ধ অবস্থায় হাতপাখা দোলাতে লাগলেন ধীরেন্দ্রনাথ। কপালে গভীর ভাঁজ। সংসারের দায়িত্ব অমলার ওপরে পড়ছে। প্রায়ই কলেজ কামাই হচ্ছে। এদিকে ঝি পাওয়া যায় না। ঝি রাখার টাকাই বা কোথায়? খাটালের একটি হিন্দুস্থানী বউ এসে একটু বেলায় উনান ধরিয়ে দেয়। সপ্তাহে দু-দিন ঘর-দুয়ার মাটি লেপে দিয়ে যায়। মেয়ের কষ্ট তিনি বোঝেন, কিন্তু কিছু করতে পারেন না। কাজ করার অভ্যাস নেই। চোখ বুজে মেয়ের কথা ভাবতে থাকেন। তার প্রতি আশ্চর্য মায়া, কিন্তু কাছে এলে তিনি কেমন লজ্জা পান। ভারী অস্বস্তি হয়। অমলা আর নিরঞ্জন পিঠোপিঠি, তাঁদের অধিক বয়সের সন্তান। যেন আসার কথা ছিল না, ক্ষণিকের উদ্দামতায় এসে পড়েছে। অমু নিজেও কি একথা ভাবতে শিখেছে? মেয়ে বাবার কাছে বিশেষ ঘেঁষে না। আধাচোখে দেখলেন সে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন,
“কী জিগাইবা মা, জিগাও।”
“মায়ে কবে আইব বাবা?”
“আইব – অই – তুমার রাঙাদিদির— সকল কাজ মিট্যা গ্যালে মুরারী টেলিগ্রাম করব।”
প্রসব শব্দটা মেয়ের সামনে উচ্চারণ করতে সঙ্কোচ হল। অতি দীর্ঘ
নিঃশ্বাস ফেলে ভেঙে ভেঙে বলতে লাগলেন,
“কারে আর কী কই? কপালের নাম গুপাল। কুমুরে দ্যাখতে কইলকাতায় আইছিলাম।
তাইরে বাচাইতে পারলাম না, চাকরিখানও গেল গিয়া! ঘরবাড়ি উজরাইয়া অহনে জলাজঙ্গলের মইধ্যে
মাথাগোজনের জাগা হইছে। হেইডাও আইজ আছে, কাইল থাকব কিনা কেডায় জানে? সহায়সম্বলহীন বাস্তুহারা
মাস্টারের সন্তান তুমরা। ল্যাখাপড়া শিখ্যা স্বাবলম্বী হইয়া দারাইতে অইব—মনে রাখবা!”
অমলা নীরবে শোনে পিতার তীব্র আক্ষেপ, যন্ত্রণার শব্দ। তার ফর্সামুখ
লাল হয়ে ওঠে। আগেও কতবার শুনেছে, এমন করে বুকে বাজেনি। সে অনুভব করল, হঠাৎ সে অনেকটা
বড়ো হয়ে গেছে। অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে।
শ্রাবণমাস ফুরিয়ে এল। বৃষ্টিতে ছেদ পড়েনি। বিকেলবেলা ঘন হয়ে সন্ধের অন্ধকার নামছে। মেঘে-ঢাকা আকাশ নিশ্ছিদ্র কালো। মুষলধার বৃষ্টি হচ্ছে দু-দিন ধরে। সামান্য থামছে, কিছুক্ষণ পর আবার প্রবল বেগে ঝরে পড়ছে। শান্তিপুর থেকে সকালে মুরারীর টেলিগ্রাম এসেছে, “সন বর্ন।”ধীরেন্দ্রনাথ নাতির জন্মবার্তায় খুশি হলেন কিনা বোঝা গেল না। নিঃশব্দে দু-হাত কপালে ঠেকালেন। ছোটো ছেলেকে ডাকলেন,
“শুন নিরু। কই যে, একখান পূজা দেওন লাগে। পারবা? কাইল তাইলে কালীঘাটে
গিয়া শুদ্ধবস্ত্রে পাচসিকার পূজা দিয়া আইবা। মন্দিরের পাণ্ডা ভোলাঠাকুরে আমারে চিনে,
তাইনরে কইও। অমু, সকালে আধপো দুধ আইন্যা দিমু। পায়স রান্ধন পারবানি?”
দাওয়ায় মাদুরে ঝিম হয়ে বসে থাকেন তিনি। লণ্ঠন জ্বেলে দিয়ে গেছে
অমলা। টিমটিমে আলো। দাওয়ার মেঝে ঢালাই-করা। দু-পাশে মুখোমুখি দুটি ঘর। কোণের দিকে আরেকটি,
একটু ছোটো। ওখানে তারাসুন্দরীর গোপালের ছোটো আসন। বেড়ার দেওয়াল, টালির চাল। উঠোনের
একধারে রান্নাঘর, অদূরে চাপাকল। পেছনদিকে আড়াল-দেওয়া চানের ঘর, পাশে খাটা পায়খানা।
বছরদেড়েক আগে চারকাঠা জমিসমেত এই আস্তানা নামমাত্র দামে কিনেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ। অদূরে,
অল্প দূরে ক-ঘর বাসিন্দা। ওরা তাঁর মতো প্রতিদিনের লড়াই করে চলেছে। অপ্রশস্ত কাঁচা
গলিপথ, আগাছা, লতানেগাছের ঝোপঝাড়, ডোবা। বাড়ির চৌহদ্দি জুড়ে ঢেঁড়সের জঙ্গল। জলা জমিতে
প্রচুর ফলে। সামনে একটু জায়গা পরিষ্কার করে ফুলগাছ পুঁতেছেন তারাসুন্দরী। গোলাপী আর
হলদে সন্ধ্যামণি, লঙ্কাজবা, তুলসীচারা। নয়নতারা গাছ আপনিই গজিয়ে উঠেছে। বৃষ্টির বাতাসে
ফুলের মৃদু সৌরভ ছাপিয়ে মল ও আবর্জনার দুর্গন্ধ ওড়ে। পোকা আর মশার ঝাঁক ভনভন করে। গায়ে
বসে। ধীরেন্দ্রনাথের চটাস চটাস করে মশা মারেন। বিশ্রী লাগে, বুকের খাঁচায় রাগের উত্তপ্ত
বাতাস বয়।
রান্নাঘর থেকে অমলা এসে দাঁড়াল। বলল,
“বাবা খাইবেন না? রান্না হইয়া গ্যাছে।”
“কী রানছ?”
“ভাত, ঢেরসের ঝোল। ওই বেলার ডাইল আছে। গরম কইরা রাখছি—।”
ধীরেন্দ্রনাথ মুখ বিকৃত করলেন। তিনি খেতে ভালোবাসেন। ঢেঁড়সের
তরকারি খেয়ে মুখ পচে গেছে। অমলার রান্নাও ভালো না, পানসে। অমলা বুঝি বাবাকে লক্ষ করল।
চোখ নীচু করে করুণসুরে বলল,
“আমি মা-র মতন রান্ধন পারি না বাবা—।”
মেয়ের কথায় সত্যিকারের দুঃখ পেলেন ধীরেন্দ্রনাথ, অপরাধী মনে
হল নিজেকে। মেয়েকে উৎসাহ দিতে বললেন,
“যা করতাছ হেইডাই যথেষ্ট। কাল বাজার থে’মাছ লইয়া আমু। কই যে, যদ্দিন
না বিয়াশাদী হইত, মা’র নিকট থে’ শিখ্যা লইও। ইংরাজিতে একখান প্রভার্ব আছে, বোঝলা? টু
হার্ট থ্রু স্টমাক। আমি এফ-এ এক্সামে ইংরাজিতে
দ্বিতীয় হইছিলাম, জান? তুমার মায়েরে শিখানের কত চ্যাষ্টা করছি। অইল না, মাথা নাই।”
ধীরেন্দ্রনাথ এবার প্রাণ খুলে হাসতে থাকেন। তাঁর হাসি দেখে অমলার
খুশি জাগে। জোর গলায় বলে,
“আমার মা-র মতো রান্না কেও পারে না!”
“সইত্যই। একবার জান, আমগ বাসায় এক অতিথ আইছিল। খাওন লইয়া হের
বড়ই প্যাংছা। হাত চাইট্যা খাইয়া উইঠ্যা কয় কী জানস, অমৃত! অমৃত! খাইলাম শুধু উনার পাকের
তারে—।”
বাতাস হালকা হয়ে বইছে। অমলা বাবার পাশটিতে চুপ করে বসে থাকে।
তার ফর্সা গালে, ন্যাতানো ডোরাকাটা শাড়িতে, ছোট্ট কপালে, কালো, ঘন চুলের আলগা বেণীতে
লণ্ঠনের মৃদু আলো। ধীরেন্দ্রনাথের বুকে মায়া
থইথই করে। অমুর বয়স কত হল ভাবলেন – সতেরো না আঠারো? জন্মসাল ধরে হিসাব করে দেখলেন,
বৈশাখে ঊনিশে পা দিয়েছে। মনে মনে বেশ চমকে উঠলেন। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তাঁর তিন মেয়েই রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। বাবাকে তাকিয়ে
থাকতে দেখে অমলা আবার বলে,
“চলেন বাবা—। নিরু বুঝি শুইয়া পরছে। তারে ডাইক্যা লই।”
ধীরেন্দ্রনাথ মেয়ের সামনে নিজের ডানহাত পেতে দিয়ে কেমন যেন অসহায়
গলায় বললেন,
“আমার এই হাতখান একবার দ্যাখ দেহি মা—।”
সস্নেহে বাবার হাতখানা ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল অমলা। কিছু বুঝল
না। আস্তে আস্তে আঙুল বুলিয়ে দিয়ে বলল,
“কী হইছে বাবা? দুঃখু পাইছেন?”
“যন্ত্রণা মা—! দরদরাইয়া রক্ত বাইরাইতাছে দেখতে পাইতাছ?”
অমলা ভীত, বিস্মিত। কী করবে সে বুঝতে পারছে না। তার সুকুমার
মুখখানা উদ্বিগ্ন দেখাল। ধীরেন্দ্রনাথ আজকাল মাঝেমাঝে সামান্য অসংলগ্ন কথা বলেন। কয়েকমুহূর্ত
পরেই টেনে নিলেন হাত। নিজের চোখের সামনে ধরামাত্র হাতের রেখায় সেই টুকরো টুকরো রক্তাক্ত
মানচিত্র ফুটে উঠল। ধীরেন্দ্রনাথ দু-হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে উঠলেন,
“ভাইঙ্গা-চুইরা এইর-ম ক্যান করলেন আপনেরা? আমরা কী অপরাধ করছিলাম?”
আরও মাসখানেক কাটিয়ে দিনকয়েক আগে ফিরেছেন তারাসুন্দরী। মুরারীমোহন ছুটি পায়নি। তার এক ভাই কৃষ্ণমোহন এসে পৌঁছে দিয়ে গেল। বেশী বয়সে প্রথম সন্তান হল রমলার। শরীর যথেষ্ট খারাপ হয়েছিল। ছেলেটি যদিও সুস্থ সবল হয়েছে। তারাসুন্দরী ফিরে আসাতে সংসারের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেল অমলা। তার মর্নিং কলেজ। ক্লাস কামাই হচ্ছিল। বাসা থেকে মাইলদেড়েক হেঁটে গেলে ট্রামডিপো। ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে যাতায়াত করে অমলা। যাত্রাপথটি ভারী ভালো লাগে। এত ভোরে লোক চলাচল কম থাকে। ভোরের আলো ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়। ঢাকুরিয়া লেকের পাশ দিয়ে ট্রাম চলে। চোখে পড়ে কর্পোরেশনের লোক হোসপাইপ দিয়ে রাস্তা ধোওয়াচ্ছে। অমলা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে, কেমন সুন্দর শহর। ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। অথচ একই শহরে ক-মাইল মাত্র দূরে তাদের থাকার জায়গা, তাদের পাড়া কোন অন্য পৃথিবী! কলেজ যাওয়ার পথটি রোজ আবার নতুন করে উপভোগ করছে অমলা। তারাসুন্দরী বাড়িতে না থাকার জন্য কলেজ যাওয়া অনিয়মিত ছিল। বইখাতা নিয়ে বাড়িতে পড়ার চেষ্টা করেছে। মন বসেনি। সে তেমন মেধাবীও নয়। কোনওরকমে ইন্টারমিডিয়েট উতরেছে।
অমলা কলেজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলে তারাসুন্দরী অভ্যস্ত হাতে
সংসারের কাজে ঢোকেন। উনুন ধরিয়ে কাপড় ছাড়েন। ঠাকুর জাগান। ঠাকুরের জায়গাটি পরিষ্কার
করে নিজের পোঁতা গাছ থেকে ক-টি ফুল তুলে দেন। তারপর চা করেন। ধীরেন্দ্রনাথের চা একবারই
খান। তিনি নিজেই বারবার খান বলে বাটিতে বেশী করে ঢেলে রাখেন। রান্নার ফাঁকে একটু করে
গরম করে নেন। ধীরেন্দ্রনাথ বাজার করে আনেন। বাজার বিশেষ দূরে না হলেও বর্ষাকালে কাদাজল,
নোংরা পেরিয়ে যাওয়া কষ্টকর। বর্ষার পরে জায়গায় জায়গায় পাঁক জমে থাকে। মাছির বাচ্চা
বিনবিন করে। এমনিতেও সারা বছর খোলা ড্রেন আর খাটা পায়খানার বদ গন্ধ হঠাৎ হঠাৎ উড়ে আসে।
দুপুরের পাট সেরে, বাসন তুলে এসে খুব সাবধানে বিছানায় কাত হলেন
তারাসুন্দরী। অমলা অন্য ঘরে হয় বইদপ্তর খুলে বসেছে, অথবা ঘুমোচ্ছে। নিরুর স্কুল থেকে
ফিরতে বিকেল হয়ে যায়। ধীরেন্দ্রনাথের নাক ডাকছিল। তারাসুন্দরীর চাপে খাট সামান্য নড়ে
উঠল। তক্তপোশের প্রত্যেক পায়া দু-খানা করে ইট দিয়ে উঁচু করা। জলা জমিতে ঘর, মেঝেতে
কেমন ভেজাভাব থাকে বিশেষতঃ বর্ষাকালে। ধীরেন্দ্রনাথ স্ত্রীর গায়ের ওপর হাতখানা রাখলেন।
পঞ্চাশ-পেরোনো শরীর ঢিলেঢালা, মেদল। চওড়া কোমর, ভারী বুক। মাথায় প্রচুর চুল। সিঁথিতে
গাঢ় সিঁদুর। ফর্সা কপালের টিপ পরে পরে দাগ হয়ে আছে। তারাসুন্দরী সামান্য বিব্রত, বিরক্ত
হয়ে স্বামীর হাত ঠেলে সরালেন। ধীরেন্দ্রনাথ নিঃশ্বাস ফেলে সোজা সটান হলেন। হাল্কা গলায়
বললেন,
“বুড়া হইয়া গেছি ভাইব্য না!”
“হঃ, আপনের যত আজাইরা কথা। দুফরবেলা—!”
“তয় রমুরে কেমন দেইখ্যা আইলা? সুখে আছে? বংশে পোলা আইছে, বংশধর—। খাতির করতাছে?”
“ভালই আছে। শরীর দুর্বল, সারে নাই অহনেও। ঘরে শাশুড়ি নাই, বাচ্চা
দ্যাহে কেডা? পিস্শাশুড়ি বিধবা, বুড়া হইছে। তাইন আর কী করবেন? বাসায় মাইয়া নাই, মুরারীর
বাবা, ভাইয়েরা—। ননদেরা সংসার ফালাইয়া আইবার পারে? তয় কামের বেডি আছে, পাক
করনের বেডি আছে—।”
“তাইলে মাইয়া সুখেই আছে কও—?”
“অহন বেবাক মাইষের দেওন-থোওন তদারকি, রমুরে সামলাইতে হইব। আমি
আতুড় তুইল্যাই আইয়া পরলাম।”
“নিয়া আইতা! ছয়মাসের পোলা কোলে ফিরত যাইত—।”
“কই রাখতেন মাইয়ারে আইন্যা? জাগা নাই, বাসা নাই, টাহার জোর নাই—। মধু পোস্টকাট দিছিল বুইনের
কাছে। ভাগনা অইছে জাইন্যা খুশী কইল।”
“হুম। তার করছিল বুঝি মুরারী? মধু আমারেও পত্র দিছে। টাহাও পাঠাইছে।
পূজার পর দেয়ালি না কী য্যান কইল, তহন আইব।”
“হেরও বিয়ার বয়স—, অমুডারও—,”
বাক্য অসমাপ্ত রেখে নীরব হয়ে গেলেন তারাসুন্দরী। ধীরেন্দ্রনাথ
অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললেন,
“কার ঘরে কেডা বসত করে—! কুমু-মা কই গেল গিয়া—।”
তারাসুন্দরী জানেন ধীরেন্দ্রনাথের ক্ষত, একই ক্ষত তাঁরও। প্রথম
সন্তান কমলা। তার অকালমৃত্যুর শোক বুকে বয়ে বেড়াতে হবে যতদিন জীবিত আছেন। ধীরেন্দ্রনাথ
মাথা নীচু করে বসে থাকেন। স্মৃতির আবর্তে পড়ে বুকের খাঁচায় শোঁ-শোঁ ঝড়ের ঝাপটা। তারাসুন্দরী
মনের দিকে অনেক শক্ত। পরিষ্কার গলায় বলেন,
“এইগুলা ভুইল্যাও ভাইবেন না। রমুও ত আমগ মাইয়া—। তাই সুখে থাউক, আপনে আশীর্বাদ
করেন নাই? দিদির সংসারে দিদির জাগায় সে—, মনে মইরা থাহে। আমারে কইল, ‘মা, দিদি আমারে অভিশাপ দেয় নাই
কও? আমি ত তাইর ধন কাইরা লই নাই’—।”
ধীরেন্দ্রনাথ নিজের ডানহাত তারাসুন্দরীর সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,
“দ্যাহ, দ্যাশডারে কাইট্যা ভাইঙ্গা কী কইরা ফালাইছে! হেইডা বোঝন
লাগে দ্যাশ জীবন্ত। কাইট্যা ফালাইলে রক্ত ঝরব। হের মাটিতে মানুষ বসবাস করে। জড়পদার্থ
না। হেরা বোঝল না।”
(ক্রমশঃ)


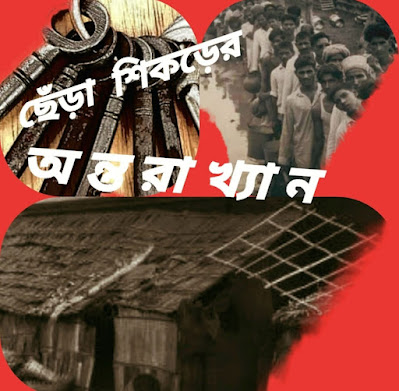
Thanks to all
উত্তরমুছুন